দেবাশিস মিথিয়া
একটি ইংরেজি দৈনিক সম্প্রতি দাবি করেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের মতে, এই বৃদ্ধি কেবল স্থিতিশীলই নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলকও বটে। ২০১৪ সালে মোদীর দেওয়া “সবকা সাথ, সবকা বিকাশ” (সবার সাথে, সবার উন্নয়ন) স্লোগান গত ১১ বছরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারুণ সাফল্য দিয়েছে। চোখে পড়ার মতো অগ্রগতি এবং পরিবর্তন ঘটেছে বলেও পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে।
প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি দেশের উন্নয়ন ঘটেছে? আর যেটুকু যা হয়েছে তার সুফলও কি দেশের প্রতিটি জনগণের কাছে সমানভাবে পৌঁছেছে? এককথায় উত্তর হলো না। ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি, আজও গভীর সঙ্কটে জর্জরিত। কৃষক আত্মহত্যা দিন দিন বাড়ছে, যা এই খাতের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে তুলে ধরে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কোভিড-১৯ এর প্রভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; ভালো সংখক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হয় বন্ধ হয়ে গেছে, নতুবা ধুঁকছে যে কোনও দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে— যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার গুণগত মান এবং স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা মৌলিক পরিষেবাগুলিতে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি করেছে। বেকারত্ব এক ক্রমবর্ধমান সমস্যা। দারিদ্র হ্রাসের দাবি সত্ত্বেও, গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-এ ভারতের স্থান তালিকার নিচের দিকে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের পকেটে চাপ বাড়িয়েছে। দেশের ভালো অংশের মানুষ এখনও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রাম করছেন, যা তথাকথিত ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন’-এর দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়।
কৃষি ও শিল্পে সঙ্কট
ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো কৃষিক্ষেত্র, যা দেশের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশের জীবিকা। অথচ ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (যেমন খরা বা অসম বৃষ্টি) এবং ঋণের বোঝা কৃষকদের জীবনকে প্রতিদিন দুর্বিষহ করে তুলছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো – এর তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০২২ সালেই ভারতে ১১,২৯০ জন কৃষক ও কৃষি শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন, যা গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্বলতা এবং কৃষকদের বঞ্চনার এক করুণ ইঙ্গিত।
বিশেষ করে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিয়ে কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলন সত্ত্বেও, ফসল উৎপাদনে প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে সঠিক এমএসপি নির্ধারণ এবং সেই এমএসপি -তে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি ক্রয় নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ। এর ফলে কৃষকরা প্রায়শই খোলা বাজারে তাদের ফসল নামমাত্র দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন, যা তাদের আয়ের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে।
এছাড়াও, শস্য বিমার আধুনিকীকরণ এবং কৃষকদের সুরক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি বারবার দেওয়া হলেও, কার্যক্ষেত্রে অনেক কৃষকই সঠিক সময়ে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জটিল প্রক্রিয়া, দীর্ঘসূত্রিতা এবং তথ্যের অভাবের কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কাছে বিমার সুফল পৌঁছাচ্ছে না। যদি শিল্প ও পরিষেবা খাতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি না হয়, তাহলে কর্মপ্রার্থীরা কৃষিক্ষেত্রে ফিরে যেতে বাধ্য হন, যা কৃষির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং কৃষি আয়ের স্থবিরতার কারণ হয়। কৃষিক্ষেত্রের এই দুর্দশা ‘সবকা বিকাশ’ স্লোগানের সঙ্গে বড়ই বেমানান।
দেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান অপরিসীম। বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটি গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি। কোভিড-১৯ মহামারী এবং তার কারণে লকডাউন, এই শিল্পগুলিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ‘জন সহাস’-এর ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, কোভিডকালে দেশের প্রায় ৪২% ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হয় বন্ধ হয়ে গেছে অথবা ধুঁকছে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন এবং বহু ছোট ব্যবসা ঋণের ভারে জর্জরিত। যদিও এমএসএমই গুলিকে সাহায্য করার জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি ঘোষণা করেছে, তবে সেগুলির সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র মতো উদ্যোগগুলিও এই খাতের প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটাতে পারেনি, যার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি ব্যাহত হয়েছে। মূলধনের অভাব, প্রযুক্তির অভাব এবং বাজারের সীমিত প্রবেশাধিকার এই খাতের উন্নতির প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ভয়াবহতা
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার যেকোনও জাতির উন্নয়নের ভিত্তি হলেও, শুধু প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়, শিক্ষার গুণগত মানও জরুরি। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা, পরিকাঠামোর অভাব এবং আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অভাবে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। যদিও সাক্ষরতার হার বেড়েছে, কিন্তু পঠন-লিখনের দক্ষতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার অভাব এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ; ২০২২ সালের ‘অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট’— এর তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ ভারতে তৃতীয় শ্রেণির মাত্র ২০.৫% শিক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় অনলাইন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হলেও, ডিজিটাল বিভাজন প্রকট হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার প্রায় ৫২.৪% হলেও, শহর ও গ্রামের মধ্যে ডিজিটাল সুবিধার অসমতা দারুণভাবে চোখে পড়েছে। ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের অভাবে বহু দরিদ্র ও গ্রামীণ শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র ধারণার এক অন্ধকার দিক।
“সবকা বিকাশ” তখনই অর্থবহ হয় যখন দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়, কিন্তু এই খাতে ভারতের চিত্রটি বেশ হতাশাজনক। দেশের জিডিপি’র তুলনায় স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ এখনো অনেক কম; ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি’র মাত্র ১.৯% এই খাতে ব্যয় হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে, যা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির (২০১৭) ২.৫% এর যে লক্ষ্য তার চেয়েও কম এবং উন্নত দেশগুলির তুলনায় তা নগণ্য। এর ফলে সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিষেবার মান, পর্যাপ্ত চিকিৎসক-নার্স এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব প্রকট। এছাড়াও, বেশিরভাগ মানুষ চিকিৎসার জন্য এখনও ব্যক্তিগত খরচের উপর নির্ভরশীল, যেখানে প্রায় ৪৭% চিকিৎসা খরচ মানুষ নিজেদের পকেট থেকে দেয়। গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে এই বিশাল ব্যয় অনেক পরিবারকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেয়, যা তথাকথিত দারিদ্র হ্রাসের পরিসংখ্যানের সঙ্গে যায় না।
কর্মসংস্থানবিহীন বৃদ্ধি, দারিদ্র ও ক্ষুধা
উন্নয়নের দাবি সত্ত্বেও, বেকারত্ব ভারতের এক বড় সমস্যা। ‘সেন্টারে ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি’ - র তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বেকারত্বের হার প্রায়শই উদ্বেগজনকভাবে বেশি থাকে। ২০২৪ সালের মে মাসে এই হার ছিল ৮.১%, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে পর্যাপ্ত চাকরির অভাব হতাশা বাড়াচ্ছে। অর্থনীতির বৃদ্ধি হলেও যদি পর্যাপ্ত নতুন চাকরি তৈরি না হয়, তাহলে তাকে ‘কর্মসংস্থানবিহীন বৃদ্ধি’ বা ‘জবলেস গ্রোথ’ বলা হয়, যা ভারতের বর্তমান অর্থনীতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।
যদিও সরকারি পরিসংখ্যানে দারিদ্র হ্রাসের দারুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। দারিদ্র শুধু আয়ের ভিত্তিতে পরিমাপ করা যায় না, এর রয়েছে বহুমাত্রিক দিক (মাল্টিডায়মেনশনাল পভার্টি)। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পানীয় জল, স্যানিটেশন, বাসস্থানের অভাব – এই সব ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা দেখা জরুরি।
সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো ক্ষুধা ও অপুষ্টি। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-এ ভারতের অবস্থান প্রায়শই পিছিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালে ভারত ১২৭ টি দেশের মধ্যে ১০৫ তম স্থানে ছিল, যা দেশের ক্ষুধা ও অপুষ্টির গুরুতর পরিস্থিতি তুলে ধরে। এটি ‘সবকা বিকাশ’ ধারণার সাথে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ কোটি কোটি মানুষ যখন পুষ্টির অভাবে ভুগছে, তখন সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দাবি কতটা বাস্তবসম্মত?
সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের দাবি করলেও, সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ছে প্রতিনিয়ত। খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রায়শই খুব বেশি থাকে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের উপর। শাকসবজি, ডাল, তেল– নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাগামছাড়া। উপভোক্তা মূল্য সূচক অনুযায়ী, ২০২৪ সালের মে মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৬৯%, যা সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির (৪.৭৫%) থেকে অনেক বেশি। যদি আয় এই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে না বাড়ে, তাহলে প্রকৃত আয় কমে যায়, যা ভোগ এবং জীবনযাত্রার মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোভিড-১৯ অতিমারীর পর এই চাপ আরও বেড়েছে। শুধু তাই নয়, পেট্রোল-ডিজেলের উচ্চ মূল্য পরিবহণ খরচ বাড়িয়ে সব পণ্যের দামকে প্রভাবিত করছে, যা পরোক্ষভাবে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয়।
আন্তর্জাতিক সূচক ও ভারতের বাস্তবতা
উন্নয়নের দাবি সত্ত্বেও, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সূচকে ভারতের পারফরম্যান্স তেমন উজ্জ্বল নয়:
ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স-এর তালিকায় ভারতের অবস্থান নিজের দিকে। ২০২৫ সালে ১৪৭টি দেশের মধ্যে ভারত ১১৮ তম স্থানে রয়েছে, যা জনগণের মানসিক সুস্থতা, জীবনযাত্রার সন্তুষ্টি এবং সামাজিক সহায়তার অভাবকে প্রতিফলিত করে।
ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স অনুযায়ী, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ভারতের অবস্থান উদ্বেগজনক। ২০২৫ সালে ভারত ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৫১ নম্বরে। যদিও এ বছর গত বছরের ১৫৯ নম্বর থেকে ৮ ধাপ উন্নতি ঘটেছে, তবে বিগত বছরগুলিতে এর অবস্থান ক্রমশ নিম্নগামী ছিল। এই ছবি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের চিত্র তুলে ধরে।।
২০২৫ সালে প্রকাশিত শিক্ষা স্বাধীনতা সূচক (এডুকেশন ফ্রিডম ইনডেক্স)-এ বিশ্বের ১৭৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ১৫৬ নম্বরে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই নিম্ন অবস্থানের মূল কারণ হলো দেশে একাডেমিক স্বাধীনতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশের অনুকূল পরিবেশের অভাব।
ভারতের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার চিত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। ফ্রিডম হাউসের মতো স্বনামধন্য সংস্থাগুলি ভারতের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে ‘আংশিকভাবে স্বাধীন’ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক মানের অবনতিকেই নির্দেশ করে। তাদের রিপোর্টে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, একাডেমিক স্বাধীনতা এবং ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতার মতো মৌলিক অধিকারগুলির উপর ক্রমবর্ধমান চাপের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলির উপর সরকারের নজরদারি ও চাপ, এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার ঘটনাগুলিও গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের জন্য এই মৌলিক স্বাধীনতাগুলি অপরিহার্য, যা ‘সবকা বিকাশ’ ধারণার সঙ্গে সরাসরি জড়িত এবং দেশের সার্বিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য হয়েছে। কাশী বিশ্বনাথ করিডোর বা উড়ান প্রকল্পের মতো উদ্যোগগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। কিন্তু একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই প্রতিফলিত হয় যখন তা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, বিশেষ করে দুর্বল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের জীবনে।
মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য, কৃষক আত্মহত্যা, ক্ষুধা ও অপুষ্টির মতো সমস্যাগুলি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে ভারতের দুর্বল পারফরম্যান্স ইঙ্গিত দেয় যে “সবকা সাথ, সবকা বিকাশ” স্লোগানটি এখনও সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। দেশের একটি বড় অংশের মানুষ এখনও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রাম করছেন। এই গভীর এবং বহুমাত্রিক সমস্যাগুলির সমাধান না করে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব নয়, কারণ কেবলমাত্র কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য সমগ্র চিত্রকে পরিবর্তন করতে পারে না।


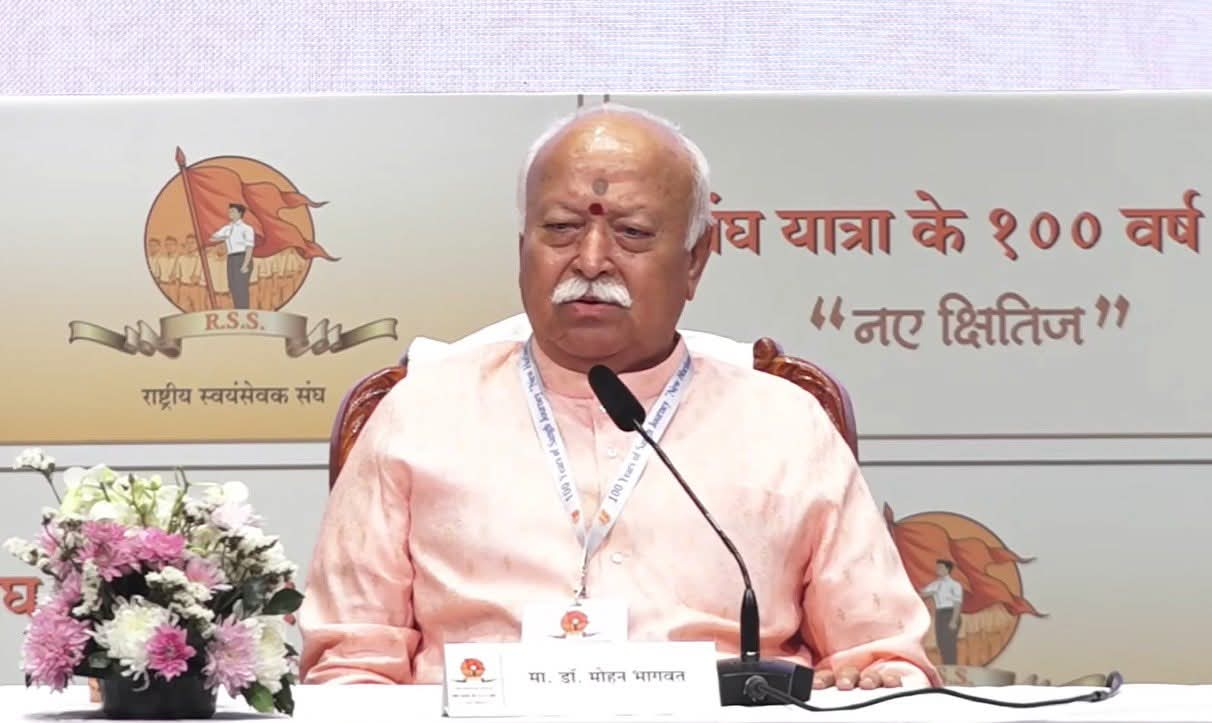


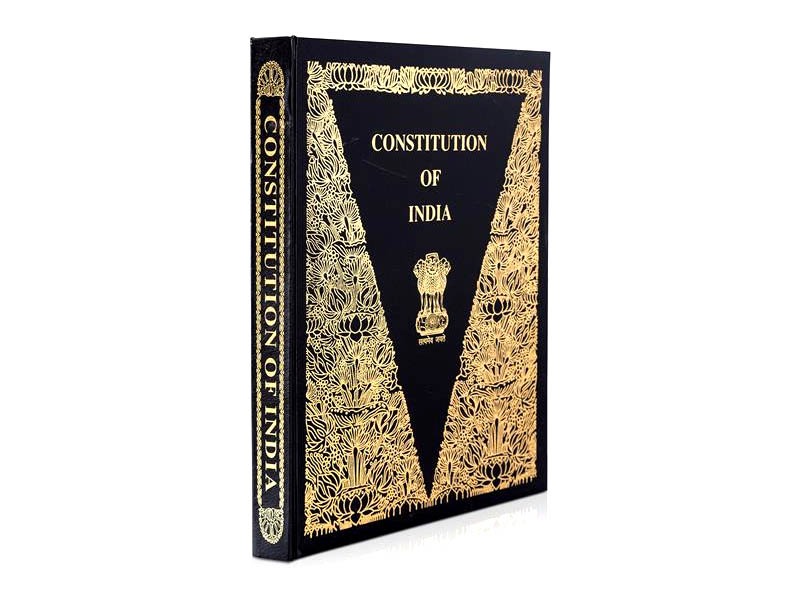


Comments :0