অরণ্য চৌধুরি
‘‘৯/১১-র ঠিক পরপর আমি একদিন পেন্টাগনে যাই। আমার জুনিয়র এক জেনারেলের সঙ্গে দেখা হয়। তার কাছে শুনি, কারা নাকি ঠিক করেছে আমাদের ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হবে! যথারীতি আমি অবাক হই। কোনও ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছু করা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করি। দেখলাম ওরাও ঠিক করে কিছু বলতে পারল না। আমতা আমতা করে বলল, এ বিষয়ে আগেই নাকি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আমাদের সেনবাহিনীর অসীম ক্ষমতা। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও দেশের সরকার ফেলে দিতে পারে। তা বুঝেই নেতাদের একটু হাত পা ছড়ানোর ইচ্ছে হয়েছে আর কি এর কয়েক সপ্তাহ পর আবার সেই জেনারেলের কাছে একদিন গেলাম। তখনও কিন্তু ইরাকের দিকে আমরা এগোইনি। ও আমায় একখানা কাগজ ধরিয়ে বলল, উপরতলার নির্দেশ এসেছে যে, আগামী পাঁচ বছরে আমরা নাকি সাতটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধে যাবো। প্রথমে ইরাক, তারপর সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং সব শেষে ইরান!’’ ২০০৯-র এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন মার্কিন সেনা কর্তা জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্কের বলা এই কথাগুলো দুনিয়াজুড়ে সাড়া ফেলে দেয়। এককালে ক্লার্ক হোয়াইট হাউসের বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৯৮-র ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯৯-র জুন পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশে পূর্ব ইউরোপের কসোভোয় মার্কিন বায়ুসেনার ‘অপারেশনে’ ১০ হাজার মানুষ নিহত হন। অবসর নিয়ে আবার হঠাৎ বিবেকের গুঁতোয় তিনি হয়ে উঠলেন পশ্চিমা বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের এক প্রধান প্রবক্তা।
তবে ২০০১ পরবর্তী ঘটনাক্রমে পেন্টাগনে ক্লার্কের পাওয়া সেই ‘উপরতলার নির্দেশের‘ সঙ্গে প্রায় অনেকটাই মিলে যায়। কোথাও সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, কোথাও বা ইজরায়েলের মতো ‘পোষ্য রাষ্ট্র’-কে ব্যবহার করে, কোথাও আবার সশস্ত্র গোষ্ঠীদের অস্ত্র ও ডলারের মদত দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে একের পর এক দেশ ‘দখল’-র অভিযান চালিয়েছে আমেরিকা। লিবিয়ার মতো কিছু জায়গায় আবার ইউএস-এইড’র টাকায় তৈরি এনজিও ও মানবাধিকার সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেক ধরা ‘রঙিন বিপ্লব’ (কালার রেভোলিউশান) অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। তাতে দেশের সরকার পড়েছে। প্রবল রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। তার পর গৃহযুদ্ধ এবং মার্কিন ‘শান্তি বাহিনীর’ হস্তক্ষেপের সুযোগ! স্বার্থটা খুব স্পষ্ট। এই সব কটা দেশই জ্বালানি তেল কিংবা অন্যান্য বিরল ধাতুর ভাণ্ডারে ঠাসা। অথবা, বিশ্ব বাণিজ্যের লজিস্টিক চেইনে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমস্ত দেশ জবরদখল করে বেলাগাম মুনাফার পথ প্রশস্ত করতে চায় বিভিন্ন ইঙ্গ-মার্কিন জ্বালানি তেলের কোম্পানি।
তবে পরিকল্পনা মাফিক আমেরিকার পক্ষে পাঁচ বছরে সাতটা দেশ দখল করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ২০০১-র পর আড়াই দশক কেট গেছে। এর মধ্যে অন্তত দুটো দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়েছে আমেরিকা। পাঁচ বছর নয়। সেগুলো চলেছে অন্তত ২০ বছর ধরে। বলা বাহুল্য এই দুটোর কোনোটাতেই আমেরিকা জেতেনি। শুধু এই দুই যুদ্ধ কেন, ১৯৪৯-এ ন্যাটো’র পত্তনের সময় থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কোনও যুদ্ধেই কিন্তু আমেরিকা জেতেনি। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইরাক কিংবা আফগানিস্তান, সবক্ষেত্রেই বহু বছর ধরে লড়াই করার পর সেনা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছে। এর কারণ কী? আধুনিক যুগে যে কোনও যুদ্ধের পিছনে দুই ধরনের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। এক, রাজনৈতিক স্বার্থ; দুই, বাণিজ্যিক স্বার্থ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক স্বার্থই রাজনৈতিক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে রাজনৈতিক স্বার্থের অস্তিত্বই স্পষ্ট ভাবে না থাকে, তবে যুদ্ধের কোনও সমাধান হয় না।
অস্ত্র ব্যবসায়ীরা যদিও তাই চায়। যুদ্ধ যদি চট করে শুরু হয়ে ফট করে শেষই হয়ে যায়, তারা ব্যবসা করবে কোত্থেকে? ফলত গোটা বিশ্বে সর্বক্ষণ এক শেষ না হওয়া যুদ্ধ চলতে দেওয়াই তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থ। এই বাণিজ্যিক স্বার্থ যাতে রাজনৈতিক স্বার্থে সঠিক রূপে প্রতিধ্বনিত হয়, তার জন্য তৈরি হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল আর্মস লবি। ১৯৪৫-র পর থেকে মার্কিন তথা পশ্চিমা বিশ্বের আপামর রাজনীতি তারাই প্রভাবিত করে চলেছে। একাধিক মার্কিন রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত হোয়াইট হাউস ছাড়ার ঠিক আগে, প্রকাশ্যেই তাদের তাঁবেদারি করার কথা স্বীকার করে গেছেন। তারাই আমেরিকা এবং তার শরিকদের গত ৮০ বছর ধরে একটানা যুদ্ধে রত থাকতে বাধ্য করেছে।
যথারীতি এই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের সরাসরি আঘাত এসে পড়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর। বিশ্বের যাবতীয় প্রাকৃতিক কিংবা সামাজিক সম্পদ এখানেই রয়েছে। প্রথম বিশ্বের উন্নয়ন, বৃদ্ধি এবং আধিপত্যের তা জিয়নকাঠি বলা চলে। একই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই রয়েছে মস্ত বড় পণ্য ও শ্রমের বাজার। ঔপনিবেশিক আমলে এই বাজারে রমরমিয়ে হুকুমদারি চালিয়েছে আর্মস লবির পূর্বসূরিরা। তবে এখন আর সেদিন নেই। সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কল্যাণে কলোনি থেকে এসব দেশ এখন স্বাধীন, স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্র।
তবে সোভিয়েত পতনের পর নতুন উদ্যমে পুরানো ফর্মুলায়, পূর্বসূরিদের হারানো ‘সম্পত্তি’ পুনর্দখলের অভিযানে নামে আর্মস লবির কেষ্টবিষ্টুরা। হয় ‘গ্যাট’ চুক্তির মতো কূটনৈতিক চাপ দিয়ে বাজার দখল। তাতে কাজ না হলে কিউবার মতো অর্থনৈতিক অবরোধ। ফাঁকফোকর পেলে এনজিও ঢুকিয়ে ‘কালার রেভোলিউশান’। রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি করা, গৃহযুদ্ধে অর্থ আর অস্ত্র ঢালা। আর মুসলিম প্রধান দেশ হলে তো কথাই নেই! ‘সন্ত্রাসবাদ দমনের’ নামে সে দেশে সরাসরি ন্যাটো’র বহর পাঠিয়ে দেওয়া। ৩৫ বছরের একতরফা মার্কিন আধিপত্যে এই ক্রিয়াক্রম খুবই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।
পাঁচটা কোম্পানি রমররমিয়ে, সগর্বে মার্কিন এবং পশ্চিমা বিশ্বের আপামর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারে যেই আসুক, স্টিয়ারিং তাদেরই হাতে থাকে। সংবাদমাধ্যমে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বিগ ফাইভ’। এই বিগ ফাইভের আবার অসংখ্য ডালপালা, শাখা প্রশাখা রয়েছে। কিছু পৃষ্ঠপোষকও রয়েছে। সব মিলিয়ে তা এক জটিল এবং মারাত্মক নেটওয়ার্ক। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, বর্তমান বিশ্বে অশান্তির যতরকম সূত্রপাত রয়েছে, তার সবকিছুতেই তাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মুনাফা স্বার্থ জড়িয়ে। গণহত্যা, যুদ্ধ, সংঘাত এসব তাদের জন্য হয় ‘টেস্টিং গ্রাউন্ড’ কিংবা উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্র।
…
দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় অস্ত্র নির্মাণে আমেরিকার উৎপাদনশীলতা এক ভয়াবহ জায়গায় চলে যায়। ১৯৪৫-র গোড়ার দিকে আমেরিকায় প্রতিদিন অন্তত ২০৩ যুদ্ধবিমান, ৫৯ ট্যাঙ্ক, ৫১ যুদ্ধজাহাজ, ১৩৮ কামানের শেল এবং প্রায় ৩ কোটি রাউন্ড বুলেট উৎপাদন করা হতো। ঠিক সেই কারণেই ওই বছরের ১৫ আগস্ট যখন সব ফ্রন্টে যুদ্ধ থেমে গেল, মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা পড়ল মহা ফাঁপড়ে। এত সংখ্যক অস্ত্র যে তৈরি হয়েও ব্যবহার হলো না, তা যাবে কোথায়? কিছু নষ্ট করা হলো। কিছু গলিয়ে অন্য ব্যবহারযোগ্য পণ্য তৈরি করা হলো। তবে বেশির ভাগটাই গুদামে পড়ে থাকল। অনেকে বলেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের ঠিক পড়েই পশ্চিমা বিশ্বের নতুন শত্রু হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেছে নেওয়ার পিছনে ছিল এই গুদামে পড়ে থাকা অস্ত্রশস্ত্র বিশ্ব বাজারে বিক্রি করার বৃহত্তর অভিসন্ধি। শুরু হলো ঠান্ডা যুদ্ধ।
ঠান্ডা যুদ্ধের সময় সামরিক পণ্যের উৎপাদনশীলতায় সোভিয়েতদের টেক্কা দিতে, বেসরকারি বিনিয়োগ আর রাষ্ট্রীয় তদারকিকে একত্রিত করে আমেরিকায় তৈরি করা হয় বেশ কয়েকটি ‘মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স’ (এমআইসি)। অচিরেই এই সমস্ত এমআইসি এবং তার মালিকরা মার্কিন রাজনৈতিক কাঠামোয় নিবিড় নিয়ন্ত্রণ জমিয়ে ফেলল।
সেই প্রভাব খাটিয়ে, মার্কিন বলয়ের দেশগুলির অস্ত্র-পণ্য-শ্রম বাজার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে একেচেটিয়া অধিকার কায়েম করে বসলো বিভিন্ন এমআইসি। তার বিরুদ্ধে ঠান্ডা যুদ্ধের সময়, বিশ্বের বহু প্রান্তে জনগণ প্রতিরোধের ডাকও দিলো। মার্কিন অস্ত্রে পুষ্ট একের পর এক জুন্টা বাহিনী এই সমস্ত প্রতিরোধকে পিষেও মারলো। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা ন্যাটো, সিয়েটো এবং সেন্টো নামের কমিউনিস্ট বিরোধী যে সমস্ত সামরিক জোট তৈরি করে, তার শরিক দেশগুলিকে বাধ্যতামূলক ভাবে মার্কিন অস্ত্র কিনতে হলো। একই সঙ্গে খাদ্য শস্য থেকে কলকারাখানার যন্ত্রাংশ, সব কিছুতেই তাদের আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য করা হলো।
তবে এ গুড়েও বালি! যে বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের অপেক্ষায় মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ওৎ পেতে বসেছিল, তা আর হলোই না। বিনা যুদ্ধেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের উপর জয় ঘোষণা করে দিল হোয়াইট হাউস। অতএব, আবারও সেই ১৯৪৫-র মতো সঙ্কটের মুখোমুখি হলো এমআইসি’র কর্তাব্যক্তিরা। ‘কমিউনিজমের ভূত’ না থাকায় মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট কমাতে হলো। বহু অস্ত্র কোম্পানি শেয়ার বাজারে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। সমাধান স্বরূপ, নয়ের দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন সরকারের প্রত্যক্ষ তদারকিতে ৫১টা অস্ত্র কোম্পানিকে মার্জ করা হলো। পড়ে রইল পাঁচটা মূল ডিফেন্স ইনকর্পোরেশন: নর্থরোপ গ্রুম্যান, রেথিয়ন টেকনোজিস, বোয়িং ডিফেন্স, জেনারেল ডাইন্যামিক্স, লকহিড মার্টিন। এরাই সেই ‘বিগ ফাইভ’।
নয়ের দশকে দুনিয়া জুড়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীতার সুযোগ নিয়ে ন্যাটো’কে সম্প্রসারিত করার নীতি নেওয়া হলো। তারই সঙ্গে মার্কিন বলয়ে নবাগতদের জন্য তৈরি করা হলো ‘অ্যানুয়াল এইড প্যাকেজ‘। এই প্যাকেজে তাদের জন্য বছর বছর কোটি কোটি ডলার অর্থসাহায্যের ঘোষণা করল আমেরিকা। তবে তার কিছু শর্তও রয়েছে। ‘এইডে’ পাওয়া ডলারের একটা নির্ধারিত অংশ এসব দেশকে মার্কিন অস্ত্র কেনায় খরচ করতে হবে! ফলত ‘বিগ ফাইভের’ জন্য নতুন বাজারের বন্দোবস্ত করা হলো।
এই শর্ত থাকায় সামাজিক পরিষেবা, পরিকাঠামো সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের ‘এইড’ বরাদ্দ কমে। সামাজিক খাতে পর্যাপ্ত ব্যয় করতে না পারায় এই দেশগুলি মার্কিন ‘এইডের’ উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে হয়। জিডিপি’র অন্তত ৩ থেকে ৫ শতাংশ অংশ বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাজেটের ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ। ‘এইড’-র ফাঁদকে কাজে লাগিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ‘বিগ ফাইভ’। বর্তমানে ন্যাটো শরিকদের দুই-তৃতীয়াংশ অস্ত্র তৈরি করে এই পাঁচ সংস্থা। ন্যাটো’র বাইরেও ইজরায়েল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, মিশরের মতো মার্কিন বলয়ের বিভিন্ন দেশ আপামর প্রতিরক্ষা খাতে আমদানির জন্য বিগ ফাইভ এবং আমেরিকার সরকারের উপরেই নির্ভর করে থাকে।
বিগ ফাইভের ভরণপোষণের জন্য চাই দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত। ঠিক সেই কারণেই আমেরিকার পাঁচ বছরে সাত দেশ দখল করা হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধ যত বেশি দিন ধরে চলবে, অস্ত্রের চাহিদা তত স্থায়ী আকার নেবে। একুশ শতকের যে কোনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এটাই সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক স্বার্থ। সীমিত তীব্রতায় দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত এই স্বার্থের জন্য একেবারে উপযুক্ত। এই ধরনের সংঘাতের উদ্দেশ্য মূলত দুটো। এক, নিত্যনতুন অস্ত্রের ‘ব্যাটেল-টেস্টিং’ (যুদ্ধ পরীক্ষা); দুই, দেশে দেশে অস্ত্রের চাহিদা বাড়ানো। এই ধরনের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সমস্যার সমাধান নয়, বরং কোনও না কোনোভাবে সংঘাতকে জিইয়ে রাখা। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে গাজা গণহত্যা দুইই এই ব্লুপ্রিন্ট মেনেই চলছে।
রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। গত ২০২২-এ এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মার্কিন অস্ত্র কোম্পানিগুলোর বার্ষিক আয় প্রায় ২৯ শতাংশ হারে বেড়েছে। সাড়ে তিন বছরের এই যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩২ হাজার কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করেছে ‘বিগ ফাইভ’। নিত্য নতুন অস্ত্রের ‘ব্যাটেল টেস্টিং’ এখানেই হয়েছে। গাজা গণহত্যা আরও মারাত্মক। বিভিন্ন অস্ত্র নির্মাতা থেকে শুরু করে নামজাদা আইটি কোম্পানি এতে যা মুনাফা করেছে, তার কাছে রাশিয়া ইউক্রেন নিতান্তই শিশু বলা চলে। মূলত ইজরায়েলের দুটি সংস্থা: এলবিট সিস্টেমস এবং ইজরায়েল এয়ারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ গণহত্যাকে কার্যত লাভজনক শিল্পে পরিণত করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য এই দুই সংস্থার অন্যতম পৃষ্টপোষক সেই ‘বিগ-ফাইভ’, এবং বিশ্বস্ত পার্টনার আদানি গ্রুপ।
গাজা গণহত্যা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিজরবিহীনভাবে সামরিক ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র দেদার প্রয়োগ হয়েছে। ফলত ‘বিগ-ফাইভের’ সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষ মারার ব্যবসায় মুনাফা বাড়িয়েছে ‘অ্যালফাবেট‘, ‘আমাজনের’ মতো তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা। সম্প্রতি এই নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এক বিস্তারিত রিপোর্টও প্রকাশ করেছে। ২০২৩-র অক্টোবরে ইজরায়েলী সেনা গাজায় অভিযান শুরু করা মাত্রই এই সমস্ত সংস্থার শেয়ার মূল্য প্রায় ১০০ থেকে ২০০ শতাংশ হাতে বেড়েছে। মাসখানেকের মধ্যেই ‘বিগ ফাইভের’ মুনাফা বেড়েছে অন্তত ২০ শতাংশ। আয় বেড়েছে প্রায় ১৪ হাজার কোটি ডলার।
গাজা কিংবা রাশিয়া ইউক্রেন ‘বিগ ফাইভ’ এবং তার পার্টনারদের জন্য কেবলই টেস্টিং গ্রাউন্ড। সেখানে মানুষের প্রাণ হলো তাদের কাছে ‘পয়েন্ট স্কোর‘। একেকটি নতুন তৈরি অস্ত্রের যত বেশি মানুষ মারার ক্ষমতা তাদের ‘ব্যাটেল স্কোর’ তত বেশি, বাজারে চাহিদা তত বেশি। দেশে দেশে অস্ত্রের এই বিপুল চাহিদা ধরে রাখতে, অনবরত ব্যাটেল টেস্টিং প্রয়োজন। ফলে বিশ্বের কোনও না কোনও জায়গায় সব সময়ই যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাত চালিয়ে যেতে হবে।


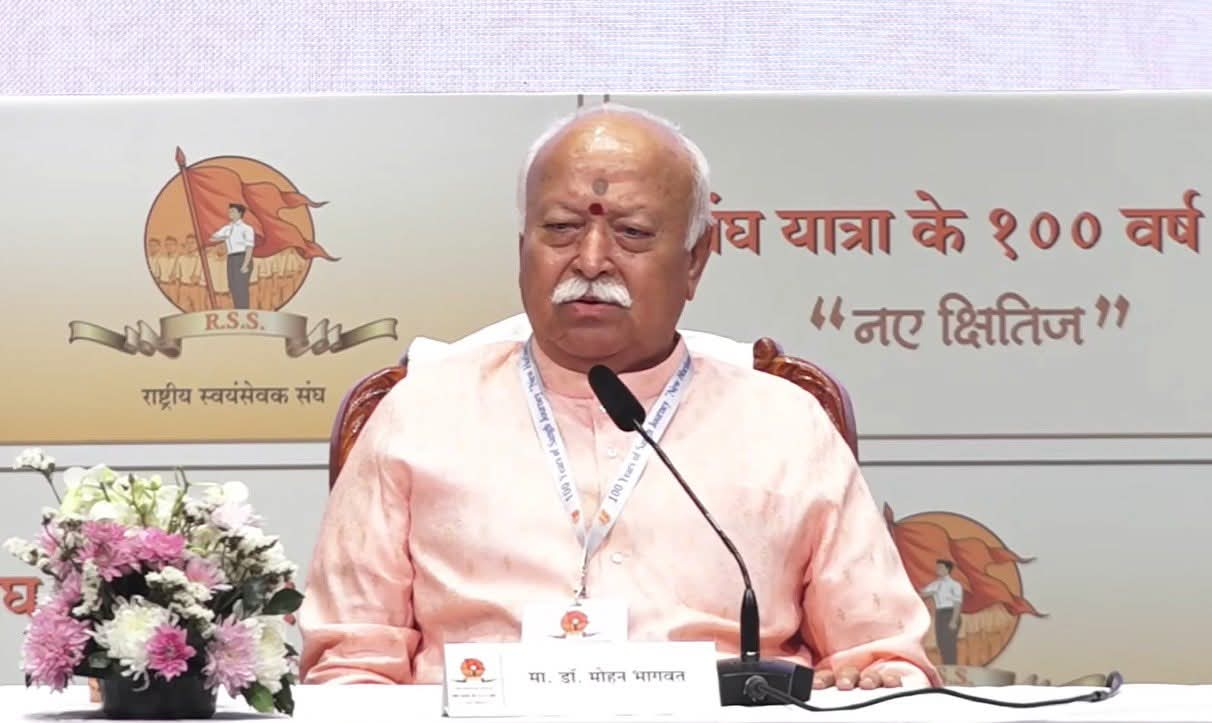


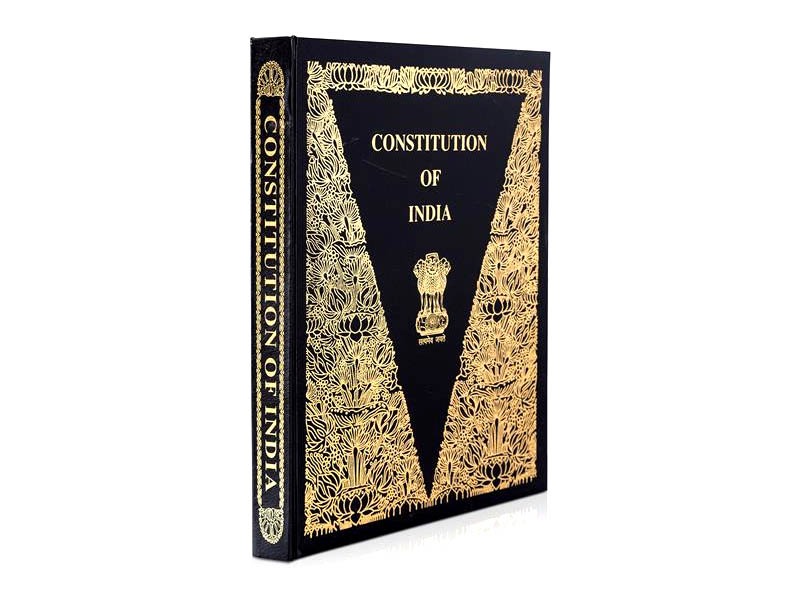


Comments :0