অঞ্জন বেরা
বিজেপি’র নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি দলীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেই জ্যোতি বসু’র প্রসঙ্গ পেড়েছেন। তাঁর দাবি,স্বাধীনতার আগে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা ভাগের প্রশ্নে বেঙ্গল লেজিসলেটি অ্যাসেমব্লিতে বসু সহ কমিউনিস্ট সদস্যরা নাকি হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। সেই বঙ্গভঙ্গের সূত্রেই ২০ জুন বিজেপি ও তার শাখা সংগঠনগুলি ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ হিসাবে উদ্যাপন করে। বলাবাহুল্য, প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।
মাউন্টব্যাটন রোয়েদাদ
বাংলায় লেজিসলেটি অ্যাসেমব্লির ২০ জুন অধিবেশনের পশ্চাদপটে ছিল ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটন ঘোষিত রোয়েদাদ। মাউন্টব্যাটন রোয়েদাদেই প্রথম ক্ষমতার হস্তান্তরের আগে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়। অধিবেশনে বসার পিছনে কারণ এমনকি ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাও বাংলাভাগের বিষয়টি উহ্য রাখে। মাউন্টব্যাটন রোয়েদাদ অনুযায়ীই বাংলাভাগ এবং গণপরিষদে বাংলার যোগদানের প্রশ্নকে অ্যাসেমব্লির অধিবেশনে বৈধতা দেওয়া হয়। ২০ জুন ছিল অবিভক্ত বাংলায় লেজিসলেটি অ্যাসেমব্লির সর্বশেষ অধিবেশন।
মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ কংগ্রেস, লিগ এবং শিখ সম্প্রদায় সকলেই মেনে নেয়। অথবা মেনে নিতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশভাগ তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও দেশভাগ তাদের কাম্য ছিল না। ১৫ জুন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি দিল্লিতে বৈঠকে বসে এবং ১৫৭-২৯ ভোটে ভাইসরয়ের পরিকল্পনায় সম্মতি দেয়। আসলে দেশ ভাগ তথা বাংলা ভাগ ১৯৪৭ সালের ৩ জুনই হয়ে যায়। ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় বাংলা ভাগের ঘোষিত সিদ্ধান্তে পরিষদীয় সিলমোহর পড়ে।
বাংলাভাগের হুঙ্কার
ক্ষমতার হস্তান্তর ভারত ভাগের মধ্যেই হবে এমন দাবি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোনো পক্ষই করেনি। স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনও দেশভাগের দাবি করেনি। দেশভাগ চায়নি। দেশ ভাগ চেয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তি।
সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ ভেঙেই মুসলিম লিগ পাকিস্তান গঠন করতে চায়। মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক এই দাবির পিছনে ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব। হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতি; তারা একত্রে বাস করতে পারে না— এই ছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির কুযুক্তি। দ্বিজাতি তত্ত্ব ছিল হিন্দুত্ববাদীদেরও। সংখ্যালঘু বিদ্বেষের পক্ষে একইভাবে কুযুক্তি সাজাতো।
বাংলায় হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক বিদ্বেষের পরিবেশ তিক্ততর হয় ১৯৪৬ সালের আগস্টের ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’-র পর। হিন্দু মহাসভা ‘হিন্দু’ বাঙালিদের জন্য পৃথক প্রদেশের দাবি তুলতে থাকে। ১৯৪৬-এর শেষ দিকেই কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবী তৈরি করেন ‘বেঙ্গল পার্টিশন লিগ’। বঙ্গভঙ্গের দাবিতে নেমে পড়ে কলকাতার কিছু কিছু বণিকসভাও। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৯৪৭ সালের ১১ মে সর্দার প্যাটেলকে লেখা চিঠিতে দাবি তোলেন, ‘‘পাকিস্তান হোক বা না হোক,বাংলা প্রদেশ ভেঙে দু’টি প্রদেশ করতে হবে।’’( দুর্গা দাস সম্পাদিত, সর্দার প্যাটেলস করসপন্ডেন্স, ভলিউম– চার) এভাবেই ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইনসভায় হিন্দু মহাসভার একমাত্র নির্বাচিত সদস্য হয়েও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাঙালি ‘হিন্দু’-র ‘রক্ষাকর্তা’ হয়ে উঠেন। পশ্চিমবঙ্গের ‘জনক’ হয়ে উঠেন।
তবে দেশ ভাগ ও বাংলা ভাগ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠার পর্বেও ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মে মাসে কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়, শরৎ বসু, বাংলা প্রদেশ মুসলিম লিগের সম্পাদক আবুল হাশেম, মুসলিম লিগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি ছিলেন সংযুক্ত সার্বভৌম বঙ্গ প্রদেশ গঠন প্রস্তাবের উৎসাহী সমর্থক। যদিও জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভ্য় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই প্রস্তাবে সমর্থন দেননি। অনেকগুলি বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা প্রস্তাবকদের কাছে ছিল না।
কী হয়েছিল ২০ জুন?
মাউন্টব্যাটন রোয়েদাদ অনুযায়ী আহূত বেঙ্গল লেজিসলেটি অ্যাসেমব্লির ২০ জুনের অধিবেশনে মুখ্যত বাংলাভাগ এবং বাংলার গণপরিষদে যোগদানের প্রশ্নে ভোটাভুটি হয়। ওই দিন সভায় কেউ ভাষণ দেননি। শুধুই ভোটাভুটি হয় কয়েকটি প্রস্তাবের উপর।
প্রসঙ্গত, তখনকার ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটি অ্যাসেমব্লিতে ১৯৪৬ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী, প্রধান শক্তিশালী দল ছিল— ১১৩ আসনে জয়ী মুসলিম লিগ এবং ৮৬ আসনে জয়ী জাতীয় কংগ্রেস। সিপিআই’র ছিল ৩টি আসন- জ্যোতি বসু ( রেল ট্রেড ইউনিয়ন), রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিঙ) এবং রূপনারায়ণ রায় (দিনাজপুর)। হিন্দু মহাসভার একজন। সেইসঙ্গে ছিলেন ইউরোপীয় সদস্য ২৫ জন, এবং নির্দলীয় মুসলিম ও নির্দলীয় হিন্দু সদস্য। অবশ্য মনে রাখতে হবে সেই আইনসভা গঠিত হয় সীমাবব্ধ ভোটাধিকারের (মাত্র ১৪ শতাংশ) ভিত্তিতে।
হিন্দু মহাসভার একমাত্র এমএলএ ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। নির্বাচনে তাঁর দলের বিশেষ জনসমর্থন বিশেষ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময় থেকে তিনি হিন্দু মহাসভায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ‘হিন্দু’ পরিচিতি সত্তার পক্ষে সোচ্চার হয়ে প্রাদেশিক রাজনীতিতে তিনি প্রভাব বাড়াতেও সক্ষম হন। অবশ্য, সেসময় সম্ভবত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চাপে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশও তাঁর প্রতি কিছুদিন একটু বেশি উদার ছিলেন। কংগ্রেসের সাহায্যেই মুখার্জি ১৯৪৭ গণপরিষদে নির্বাচিত হন। তারপর স্বাধীন দেশ প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সদস্য।
বিশেষত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রেক্ষাপটে তখন সিপিআই’র সাংগঠনিক সামর্থ্যও ছিল সীমিত। প্রাদেশিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে মূল ভূমিকা ছিল কংগ্রেস ও লিগের। প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম সংরক্ষিত আসনে মুসলিম জনতার প্রায় সর্বাত্মক সমর্থন পাচ্ছে লিগ।
১৯৪৬-র নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রী হন সোহরাওয়ার্দি। মুসলিম লিগের প্রাদেশিক সম্পাদক ছিলেন আবুল হাশেম। এ কে ফজলুল হক তখন অনেকটাই অস্তগামী। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন যুক্ত বাংলার অ্যাসেমব্লির সর্বশেষ অধিবেশন যখন শুরু হতে যাচ্ছে তখন দেশভাগ তথা বাংলা ভাগ কার্যত নিশ্চিত।
দু’ভাগে অধিবেশন
২০ জুন অ্যাসেমব্লির সদস্যরা দু’ভাগে অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি থেকে (মুখ্যত পূর্ব বঙ্গীয়) নির্বাচিত সদস্যরা এবং অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি (মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গীয়) থেকে নির্বাচিত সদস্যরা। সভার ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্য সেদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন।
হিসাব অনুযায়ী, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি থেকে ১৪০ জন এবং অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি থেকে ৭৯জন নির্বাচিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মোট ২১৯ জন। মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি এবং মুসলিম লিগের প্রাদেশিক সম্পাদক আবুল হাশিম ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয় অংশে। কংগ্রেস পরিষদীয় দল নেতা কিরণ শঙ্কর রায় ছিলেন পূর্ববঙ্গীয় অংশে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয় অংশে। কমিউনিস্ট পার্টি তিন জন সদস্যের মধ্যে জ্যোতি বসু এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিঙ) ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয় অংশে। আর পূর্ব বঙ্গের ভাগে ছিলেন রূপনারায়ণ রায়।
২০ জুন সকাল ১১টায় বেঙ্গল লেজিসলেটি অ্যাসেমব্লিতে পৃথকভাবে অধিবেশনে বসেন দুই অংশের নির্বাচিত বিধায়করা। পূর্ববঙ্গীয় অংশের অধিবেশন পরিচালনা করেন স্পিকার নুরুল আমিন। পশ্চিমবঙ্গীয় অংশে বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব।
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের অধিবেশনে কংগ্রেস পরিষদীয় দল নেতা কিরণ শঙ্কর রায় (ইস্টবেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আসন থেকে নির্বাচিত) প্রস্তাব দেন যৌথ অধিবেশনের। প্রস্তাব গৃহীত হয়। সকলেই জানতেন এই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত কী হবে। ফলে তার বাড়তি তাৎপর্য কিছু ছিল না।
সম্মিলিত অধিবেশন
বিকাল তিনটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত যৌথ অধিবেশনে স্পিকার নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে ২১৯ জন সদস্য অংশ নেন। সেখানে ভোট গ্রহণ হয় বর্তমান কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে (১৯৪৬ সালের নভেম্বরে গঠিত ভারতীয় গণপরিষদ) অখণ্ড বাংলা প্রদেশ যোগ দেবে কিনা সেই প্রশ্নে। এই প্রস্তাব ১২৬-৯০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। ফলাফল অপ্রত্যাশিত ছিল না। তিন কমিউনিস্ট সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নেননি।
‘দৈনিক স্বাধীনতা’ পত্রিকায় ২০ জুন প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত সিদ্ধান্ত, কোনও প্রদেশ বা প্রদেশের অংশ ভারত না পাকিস্তান কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে তা গণভোটে নির্ধারিত হওয়া উচিত। সীমাবব্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভায় নয়। কমিউনিস্ট পার্টির অভিযোগ ছিল, মাউন্টব্যাটন রোয়েদাদে গণভোটের স্বীকৃতি নেই। কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র বাংলা প্রদেশের পাকিস্তান-ভুক্তিরও বিরোধিতা করে।
২১ জুন ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় আইনসভার ভোটাভুটির বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়, বিশেষত কমিউনিস্ট এমএলএ-দের ভূমিকা সম্পর্কে।
পৃথক অধিবেশন
অ্যাসেমব্লিতে যৌথ অধিবেশনের পর দুই অংশের বিধায়করা পৃথক অধিবেশনে মিলিত হন। মৌলানা সামসুল হুদা (ময়মনসিংহ দক্ষিণ থেকে নির্বাচিত এবং এ কে ফজলুল হকের সমর্থক), মৌলবী ফজলুল হক এবং খুরম খাঁ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন।
পশ্চিমবঙ্গীয় অংশের (অর্থাৎ, অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ) নির্বাচিত বিধায়কদের অধিবেশনে বাংলা ভাগের সমর্থনে আনা প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে গৃহীত হয়।
বলাবাহুল্য, মুসলিম লিগ সদস্যরা বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস এবং দু’জন কমিউনিস্ট সদস্য (জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ) প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। হিন্দু মহাসভা সদস্যও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। তৎকালীন সংবাদপত্রের পাতা উলটালে যে কেউ দেখবেন, আইনসভায় হিন্দু মহাসভার ভূমিকা নিয়ে বিশেষ উল্লেখ নেই বললেই চলে।
পূর্ব বঙ্গীয় (অর্থাৎ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ) অংশের বিধায়কদের অধিবেশনে বাংলা ভাগের সমর্থনে আনা প্রস্তাব ১০৬-৩৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। বলাবাহুল্য, মুসলিম লিগ সদস্যরা ভোট দেন বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে। আর কংগ্রেসের ৩৪ জন সদস্য এবং কমিউনিস্ট সদস্য ( রূপনারায়ণ রায় ) প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।
গণপরিষদ প্রশ্নে
পৃথক অধিবেশনে ভোটগ্রহণ হয় বর্তমান কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে (গণপরিষদে) যোগ দানের প্রশ্নেও। পশ্চিমবঙ্গীয় অংশ থেকে নির্বাচিত বিধায়কদের অধিবেশনে ভারতীয় গণপরিষদে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে গৃহীত হয়। ৭৯ জন সদস্যের সকলেই ভোট দেন। দুই কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।
পূর্ব বঙ্গীয় অংশের নির্বাচিত বিধায়কদের অধিবেশনে বর্তমান ভারতীয় গণপরিষদে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব ১০৭-৩৪ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। কংগ্রেসের ৩৪ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। ৫৫ জন তফসিলি সদস্য এবং কমিউনিস্ট সদস্য রূপনারায়ণ রায় প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। বঙ্গ প্রদেশ যদি পূর্ব বঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গে বিভক্তই হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ যে পাকিস্তানে থাকবে তা তো সব পক্ষ ৩ জুনের পরই মেনে নিয়েছিল।
পূর্ব বঙ্গীয় অংশের (অর্থাৎ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ) বিধায়কদের অধিবেশনে সিলেট বা শ্রীহট্টকে প্রস্তাবিত পূর্ব বঙ্গ প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ১০৫-৩৪ ভোটে গৃহীত হয় (‘স্বাধীনতা’র খবর অনুযায়ী, ১০৬-৩৪ ভোটে)। এই ভোটে কমিউনিস্ট সদস্য রূপনারায়ণ রায় নিরপেক্ষ থাকেন। (‘স্বাধীনতা’, ২১ জুন ১৯৪৭)
কমিউনিস্টদের নীতি
২০ জুনের অধিবেশনে কমিউনিস্টদের মূল অবস্থান কী ছিল? অধিবেশনের ভোটাভুটি সম্পর্কে সেদিন কমিউনিস্ট এমএলএ’দের বিবৃতি সংক্রান্ত সংবাদের দৈনিক ‘স্বাধীনতা’ (২০ জুন) শিরোনাম দিয়েছিল–‘আইন সভার ভোটাভুটি যেন বাংলার গৃহযুদ্ধে ইন্ধন না যোগায়’ এবং ‘দুই বাংলার মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাই বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ’।
অখণ্ড বনাম বিভক্ত বাংলা
লক্ষণীয় যারা পাকিস্তান চাইলো সেই মুসলিম লিগ ভোট দিল ঐক্যবদ্ধ বাংলা প্রদেশের পক্ষে। আর যারা দেশভাগের বিরোধিতা করে গেল লাগাতার সেই কমিউনিস্টরা ভোট দিলেন বাংলা ভাগের পক্ষে। লিগ কোনও গণতান্ত্রিক চেতনা দিয়ে বাংলার অখণ্ডতা চায়নি। তা ছিল দ্বিজাতি তত্ত্বেরই ভিন্নতর চাল। সমগ্র বাংলাকে প্রস্তাবিত মুসলিম পাকিস্তানে আত্মসাতেরই কৌশল।
অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের পক্ষে মত দেয় দ্বিজাতি তত্ত্বের তাড়নায়। সেই সিদ্ধান্তেরও কোনও গণতান্ত্রিক মর্মবস্তু ছিল না।
কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান আপাতভাবে অভিন্ন দেখালেও মর্মবস্তুর দিক থেকে ছিল গুণগতভাবে ভিন্ন। কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধী অবস্থান থেকে।
হিন্দুত্ববাদীরা চেয়েছিল খণ্ডিত বাংলায় নিরঙ্কুশ অখণ্ড ‘হিন্দুত্ব’ সাম্প্রদায়িকতা। লিগ চেয়েছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার আওতায় অখণ্ড বাংলার আত্মসাৎ।
সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আগ্রাসন থেকে বাংলা প্রদেশকে যতটা সম্ভব সুরক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বাংলা ভাগে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। বাংলাভাগ ছিল আরও অনেকের মতো কমিউনিস্টদের কাছেও বেদনাদায়ক।
দেশবিভাগ প্রশ্নে স্বয়ং জ্যোতি বসু তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে লিখে গেছেন-" পার্টি দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিল— কিন্তু এর প্রতিরোধ করার মতো শক্তি ও প্রভাব পার্টির ছিল না।" (তথ্যসূত্র: 'যত দূর মনে পড়ে' লেখক জ্যোতি বসু; পৃষ্ঠা ৪৫; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৮)
২০ জুন উদ্যাপন কেন?
বাংলাভাগে উল্লসিত হয় শুধুমাত্র মুসলিম লিগ আর হিন্দু মহাসভা। মুসলিম লিগ উল্লাস করেছিল ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠন করে। হিন্দু মহাসভা উল্লাস করে বাংলা ভাগের ‘সাফল্য’ দাবি করে।
হিন্দুত্ববাদীরা শত চেষ্টা করেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্ব রূপায়ণ করতে পারেনি। ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি তখন অধরা থেকে যায়।
২০ জুন ’পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ উদ্যাপনের মাধ্যমে বিজেপি এখন তার রাজনৈতিক পূর্বসূরিদের অধরা ‘হিন্দুত্ববাদী’ স্বপ্ন যতটা সম্ভব সাকার করতে চায়।
২০ জুনের ভুল বিকৃত ইতিহাস প্রচার করে তারা এখন বিভাজনের রাজনীতির পালে বাতাস লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টায় মগ্ন।
পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে বিভাজনের রাজনীতিই বিজেপি’র মূল ভরসা। বিজেপি নেতারা ‘উত্তরবঙ্গ’-এ পৃথক রাজ্যের হুঙ্কার দিচ্ছেন। ‘গ্রেটার কোচবিহার’ ঘোষণার দাবি তুলছে বিজেপি সাংসদ। দার্জিলিঙকে আলাদা করার দাবিও অপেক্ষমাণ আস্তিনের আড়ালে।
বিপাকে পড়ে আক্রোশ বাড়ছে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে। বিজেপি’র বালাই কি কম!




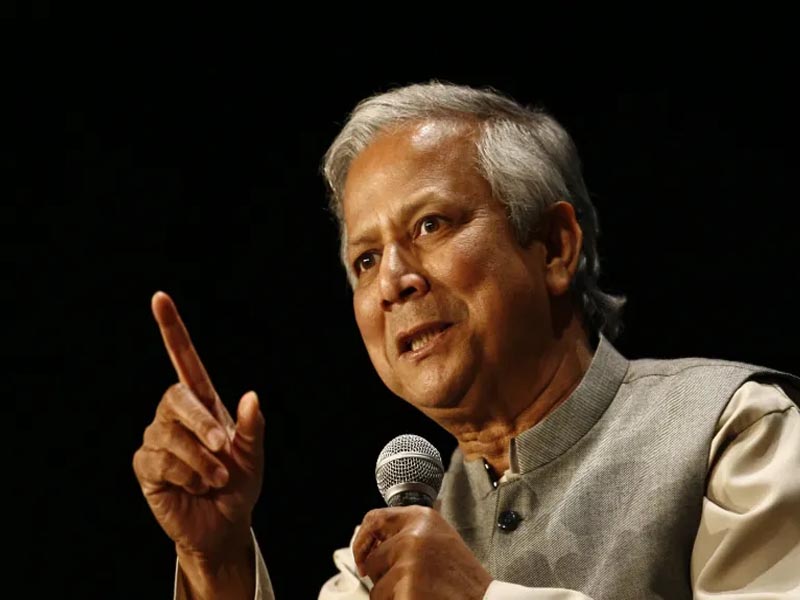



Comments :0