সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য
শরৎ বড় কঠিন এক সময়। নিত্যকার গ্লানি, ফিরে ফিরে আসা বিষাদ, ক্লেদ ঝেড়ে ফেলে এই শরৎই কয়েকটা দিনের জন্য সব ‘ভুলে’ থাকার অবকাশ দেয়। মফস্বল থেকে ট্রেনে গুঁতোগুঁতি করে আসা জনগণও হঠাৎ মাঠে কাশফুল দেখলে ভারি আনন্দ পায়। সেও শরৎকে অনুভব করে মনে মনে। দুঃখ বেচে লুটেপুটে নেওয়ার সময় তো আর এই উৎসবকাল নয়। তার জন্য ঢের সময় আছে, তাই না! মণ্ডপে ঘোরা, বাইরে খাওয়াদাওয়া, নতুন পোশাক – শরৎ মানে তো শুধুই এইসব। তাই শরৎ মানে তামান্না থেকে তিলোত্তমা কেউ না। একদম সিম্পলি ‘নেগেশন’। উৎসব থেকে সামগ্রিকভাবে এই নামগুলোকে ‘অ্যালিয়েনেট’ কর। বিচ্ছিন্ন করে দাও সমগ্র থেকে। ব্যস, উৎসব শুরু।
কিন্তু সেই ‘কেউ না’-রা যখন উৎসবের দিনে সামনে থেকেই যায় তখন বোঝা যায় তো শহরের ঝকঝকে আলোকসজ্জার ঔজ্জ্বল্য একটু কমে গেছে।
এই মাত্র কয়েক মাস আগে যে বাচ্চাটা আপন মনে খেলে বেরাত, হয়তো খেত ঘটি গরম, হয়তো নতুন জামার জন্য বায়না করত, তার নামটা পুজোর দিনে আড়ালে থাকতে পারে নাকি! তা কি হয়! হ্যাঁ, তামান্নার কথা বলছি। ঘটনার পোস্টমর্টেম করতে বসিনি, শুধু বলছি আপন মনে খেলার সময় একটা বাচ্চা যখন লাশ হয়ে যায় তখন তার প্রতি উৎসবের অঙ্গীকার কী হবে, সে প্রশ্ন তো উঠতে পারে। কী, পারে না! বছর খানেক আগে আমাদের সহনাগরিক তিলোত্তমার কথাও তো স্মরণ করা যায়। তামান্নার মাকে চিনি না, সামনে পেলে বলতাম, তামান্নাও এখন আমাদের দুগ্গা। অকালে সর্বজয়া দুগ্গাকে হারিয়েছিলেন। সেও ছিল দুর্গা পুজোর আগে। কোন এক শরতের কাছাকাছি সময়ে। তামান্নার মায়ের কোলও অকালেই শূন্য হলো। তাই তো বলছি শরৎ বোধহয় খুব নিষ্ঠুর। কখন যে দু’হাত ভরে দেয় আর কখন কেড়ে নেয়, কেউ জানে না। তবে তামান্না-তিলোত্তমা-দুগ্গা, একটা জায়গায় এসে এক হয়ে যায় কখনও। তারা আজকের, এই সময়ের দুগ্গা।
হলফ করে বলতে পারি ওদের সকলকেই কমবেশি আমরা চিনি। আরও একটু ঘুরিয়ে বলি, তারাও আমাদের চেনে, কমবেশি। দেখে, কমবেশি। তবে আমরা, একটা টানটান চিৎকার করা সময় পেরিয়ে গেলে, তাদের প্রায়ই ভুলে যাই। আমাদের ‘দুগ্গা’ বছর বছর আসে যায় ঘটা করে। আসা-যাওয়ার পথের ধারে প্রতিদিন কত দুগ্গা খেলে বেরায়, নতুন জামার জন্য বায়না করে আব্বুর কাছে, ঠাকুমার কাছে আচার চায়। পাঁচ বাড়ি বাসন মেজে পুজোর সময় পাতলা প্লাস্টিকের ঝোলায় বাবু-বৌদিদের বাড়ি থেকে সস্তার জামাকাপড় নিয়ে আসে যারা, দুগ্গারা তো আছে তাদের ঘরেও। লেখাপড়ার পাট চুকেছে কবে। রাস্তার ধারে একটা আবাসন উঠছে। ওখানেই একদল বাচ্চা মেয়ে ধুলোর মধ্যে হইচই করে সারাদিন খেলা করে। ওদের মায়েরা কনস্ট্রাকশন সাইটে জোগাড়ের কাজ করে। আর একটু বড় হলে মেয়েগুলোকেও কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের সকলকে, এই দুগ্গার দল, তাদের পরিবার- সকলকে আমরা চিনি আর যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি। ‘দেখছি-দেখব’ এসব পেটেন্ট করা শব্দ উচ্চারণ করি যখনি তারা কোন সমস্যার কথা বলে।
‘আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি।’ লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ, পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ কবিতায়। আপনি কি পড়েন ওইসব একই নামকরণের বাচ্চাগুলোকে! আপনি! আমি! পড়ি কি? দু’দশক আগেও তো ওরা সক্কলের কাছে পরিচিত ছিল বেশ। আলি, ছোট বাবু, আমিনা, লক্ষ্মী, বুড়ি, কালু, ঝন্টু – মনে পড়ছে না এসব নাম! সেই ছোট্ট আনোয়ারা বাটি ভরা সেওই এনে দিত ইদের দিনে। কালু আর নওসাদ একদিন তুমুল মারপিট করেছিল ফুটবলের দখল নিয়ে। সেদিন আপনিই তো ছাড়িয়েছিলেন, মনে পড়ছে না! তবে আমাদের ব্যস্ততা তাদের বিস্মৃতির আড়ালে সরিয়ে দিয়েছে। তামান্নাকেও কি এভাবেই বিস্মৃত হব! জানা তো নেই, শুধু আর কোন তামান্নার নামটি শুনে আমরা যেন বিপন্ন বোধ না করি। আর কোন তামান্না, ঘরের মেয়ে যেন এভাবে মরে না যায়।
দুগ্গাদের মায়েরাই বা বাদ যাবে কেন! কনস্ট্রাকশন সাইটে হাড়ভাঙা খাটনি। বাবুর বাড়িতে রান্না-বাসন মাজা-কাপড় কাচার কাজ করে যে মা, পুজোয় একদিনও ছুটি নেই সেই প্রমীলার। ওই যে কাশি মিত্র ঘাট শ্মশানের ধারে বাবার স্টেশনারি দোকান সামলায় প্রমীলার মেয়ে বাবলি, ও কিন্তু পুজোয় দোকানটাই সামলাবে। বাবা তো সন্ধে হলেই বাংলা খেয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকে। ফাঁক বুঝে একবার কুমোরটুলির ঠাকুরটা দেখে আসবে বাবলি। নতুন জামা হয়নি। বাবা বলেছে, বিক্রি ঠিকঠাক হলে জামা পাবে। অমন একটা খাপছাড়া পরিবেশে মেয়েকে সামলাতে দোকানেও যায় প্রমীলা। রাত বাড়ে। প্রমীলা ভয় পায়। শ্মশানের থেকে একটু দূরে গঙ্গার পারে সেজেগুজে দাঁড়াবে মেয়ের দল। কেউ ‘খদ্দের’ পাবে, কেউ পাবে না। যেমনটা হয় আর কি। হাড্ডি বের করা চেহারা, চড়া সস্তার মেকাপ। দিন চলে।
রণজিৎ দাশ ‘খাটাল’ কবিতায় লিখলেন ‘অনর্গল ফেনা-ভরতি দুধে ভরে ওঠে শহরের বালতি।’ এই কবিই অন্য এক কবিতায় লিখছেন, ‘এ শহরে মাটি বিক্রি হয়।’ দমবন্ধ করে দেওয়ার মতো কবিতা। ‘মাটি’- মাটি তো গ্রামের মেয়েদের গেরস্থালি। ঘরের কাজ সামলে, উঠোনে গোবর লেপা দিয়ে, দুপুরের রান্না করে গ্রামের প্রমীলারা মাঠে যায় পুরুষের কাজে হাত ‘লাগাতে’। কখনও আগাছা তোলে, কখনও বীজতলা তৈরি করে আবার কখনও ধানের চারাও পোঁতে। ঘরে বড় একটি মেয়ে আছে, অনুপমা অথবা সাবিনা অথবা মিনু। সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে। এদিকে পাড়ার ছেলেগুলি সুবিধার নয়। তাই বিকেল হলেই বাড়ি ফিরতে মন চায় প্রমীলার। তামান্নার মাও তো নিত্যদিনের কাজ করে। কিন্তু রক্তাক্ত মেয়েটার শরীর যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন...
কী, তাহলে গ্রাম-শহরের প্রমীলারা কোথাও এক হয়ে গেল না! আর এভাবেই তামান্নাও শহর কলকাতায় ঘুরে বেরায়। এ শহরেই যে কত অচেনা ‘তামান্না’ আছে তারই কি খবর রাখি!
চা বাগান থেকে বিড়ি শ্রমিক মহল্লা, খেতমজুর, শহুরে এলাকার বস্তিবাসী মহিলা যারা গৃহ সহায়িকার কাজ করে, যে মেয়ে প্লাসটিকের কারখানায় কাজ করে, তারা পুজোয়, পরবে কী করছে, জানতে ইচ্ছে করে না! তারা সকলেই একথাটুকু বেশ জানে, মণ্ডপে এই দুর্গার অর্চনা হয়। জগতের মানুষ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির জন্য দুর্গার কাছে আবেদন জানান। অশুভ শক্তি থেকে রক্ষার জন্য দশভূজার অস্ত্রসজ্জিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর।’ দিনের শেষে তোমাদের বাড়িতে যখন মহাভোজ রান্না করে অঞ্জলি মাসি, একহাতে পোলাও সামলাচ্ছে। আবার ডালে ফোড়ন দিচ্ছে। তারই মধ্যে বেসন ফেটিয়ে বেগুনি ভাজার জন্য তৈরি হচ্ছে আর অন্যদিকে প্লাস্টিক চাটনির জিনিস গোছাচ্ছে। এসব কম হলো বুঝি! অঞ্জলি মাসি তোমার ঘরের দশভূজা। যে কোন পার্বণে তেমার আপ্যায়িতদের দুই হাতে সামলায় সে। ভেবেছ কখনও, অতি নির্জনে বা উৎসবের কলরোলে ওই মাসি না থাকলে কী হত? কখনও মুখেও কি একবার বলেছ ‘অঞ্জলী মাসি তোমার ভাল হোক।’ এসব ভাবার সময় তোমার হয়না, জানি।
তাই তামান্না থেকে অভয়া, উৎসবে অনুপস্থিত থেকে যায়।
দুগ্গারা আজও বলে ‘এই দ্যাখো বেঁচে আছি/ ধানক্ষেতে, শীষের ভিতরে’। নবনীতা দেবসেন কত অনায়াসে তাই লিখতে পারেন ধানের শিষে বেঁচে থাকার কথা। পরবর্তী অংশ, ধান কাটা, ঝারাই, পালুইতে রাখা, এসবে বাড়ির মেয়েরা অনায়াস দক্ষতায় হাত লাগান। উলটে কখনও মজুরি চান না। দশ হাতে দশ কাজ করব, এ আর বড় কথা কী-এই অনুভূতি কবে যে মেয়েদের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেছে, কে জানে। কিন্তু দশভূজা প্রতিমার মতোই যে মেয়ের দল ঘাটে-মাঠে-চা বাগানে-বন্দরে-নির্মাণ স্থলে-গৃহ সহায়িকার ভূমিকায় কাজ করে যান নিরন্তর তাঁরা যদি চিৎকার করে বলেন,‘আমরা তামান্নাকে ফিরে চাই, অভয়াকে সুস্থ শরীরে কাছে চাই, আরও আরও অনেক নাম জানা-অজানাদের আমাদের মাঝে চাই’, তাহলে মুচকি হেসে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া বাবু-বিবির দল, আপনাদের কোন কাজ আছে কি! এড়িয়ে না গেলেই কিন্তু একটা প্রতিবাদ অঙ্কুরিত হতে পারে। জন্ম নিতে পারে প্রতিরোধ। এখনও যারা নিশ্চিন্তে ইউটিউব দেখে ডিজাইনার হোম ডেকর কিনে ঘর সাজাতে ব্যস্ত, শুনুন, কবিতার দুখানি লাইনও একদিন দশভূজা হয়ে অশুভের বিনাশ ঘটাতে উদ্যত হয়। কবিতা জীবন সংগ্রহ করে পথ চলে। পথ চলে কুড়িয়ে নেয় আরও জীবন, আরও...
তারপর? তারপর সে দাঁড়ায়। খোঁজে। নিরন্তর খুঁজে চলে। দেখতে পায় কানাইয়ের চায়ের দোকানে কাপ, ডিশ, চায়ের গ্লাস ধুয়ে চলেছে মলিন ফ্রক পড়া এক ছোট্ট মেয়ে। মাঝে মাঝে ওপর দিকে চায়, যেন কোন মন্ত্রবলে বিদ্যুতের তার বেয়ে নেমে আসবে হাড্ডিসার একখানা হাত। তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে অন্য, ভালোতর কোন জীবনে। হাইওয়ের ধাবার পেছনে একটা খুপড়ি ঘর আছে। ধাবা থেকে বেরিয়ে ওই ঘরে মদ খেতে ঢোকে লোকগুলো। ধাবার মালিক তখন কালিন্দী, লক্ষ্মী সোরেনদের বলে, যা মদগুলো দিয়ে আয়। ভয়ে কাঁটা হয়ে কালিন্দী, লক্ষ্মী সোরেনরা ঝুপড়িতে ঢোকে। মদের বোতল আর গ্লাস আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ছোলা সেদ্ধর একটা চাকনা এগিয়ে দেয় টেবিলে টেবিলে। লোকগুলে খুব হাসাহাসি করে। কখনও তাদের বুকে হাত দেয়, কখনও শরীরের অন্যত্র, কখনও টেনে ধরে রাখে হাত। ওদের যন্ত্রণা হয়। লক্ষ্মীরা জানে, রোজই এসব হবে।
এরাও তো তামান্না, শুধু ‘মরে বেঁচে’ আছে।
মনে পড়ছে,…‘আনন্দেরও শেষ আছে, একদিন প্রতীক্ষা ফুরাবে।’ আসলে আনন্দই তো হারিয়েছে ওদের জীবন থেকে। তবু ওরা চলমান। তবুও পথ হাঁটে। আর ‘প্রতীক্ষা’ ? প্রতীক্ষা তো সকলের, আমাদের, আপনাদের, তাদের, তোমাদের, তোদের- তাই না ? এমন পিষে দেওয়া জীবন নয়। মাথার ওপর ছাদ চাই, রোদ-জল-ঝড়ে কুড়িয়ে পাওয়া জীবন নয়। স্কুলে যাওয়া, শুধু অন্যদের যেতে দেখা নয়। পেটে ডাল-ভাত-তরকারি, মাছও, কারো দয়া করে ছুঁড়ে দেওয়া খাবার নয়। খেটে খাওয়ার মর্যাদা, কারখানায় হোক বা মাঠে বা শুধুই বাড়িতে, ‘এসব তো তুমি করবে, স্বাভাবিক’, এসব নয়। বাড়ির কাজ করলেও প্রাপ্য সম্মান যেন মেলে। এইটুকুই।
শরতে মায়েরা কান্নাকাটি করেন। মেয়েরা ভাল নেই। কয়েকটা দিনের জন্য সে বাড়িতে আসুক, ভালোমন্দ খাক, পরুক। তাই গান বাঁধা, ‘যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা বড় দুখে রয়েছে।’ আসলে আজ উমার মায়েরা আরও দুঃখে রয়েছেন। কত মায়ের কোল খালি হলো। কাকে আনতে পাঠাবেন সেই মা? কার সংবাদ আনবেন? তাঁরা কি আজও মেয়েটা খুব ‘ভালবাসে’ বলে কুমড়ো ফুলের বড়া ভাজেন? মেয়েটার জন্য আর তো বোধহয় কিনতে হয়না গরমে পড়ার মতো হালকা কোন সুতির শাড়ি! মেয়েটাকে কি ফোন করেন, হঠাৎ ভুলে গিয়ে? করতে গিয়ে দেখেন, আহা ওর নম্বরটাই তো মনে পড়ছে না!
এই রুক্ষ কঠোর শরতে তাই একটা কথাই বলার, ‘…এসো,/সুসংবাদ এসো-আর কোনো ইচ্ছে নেই’….(ভাস্কর চক্রবর্তী)।







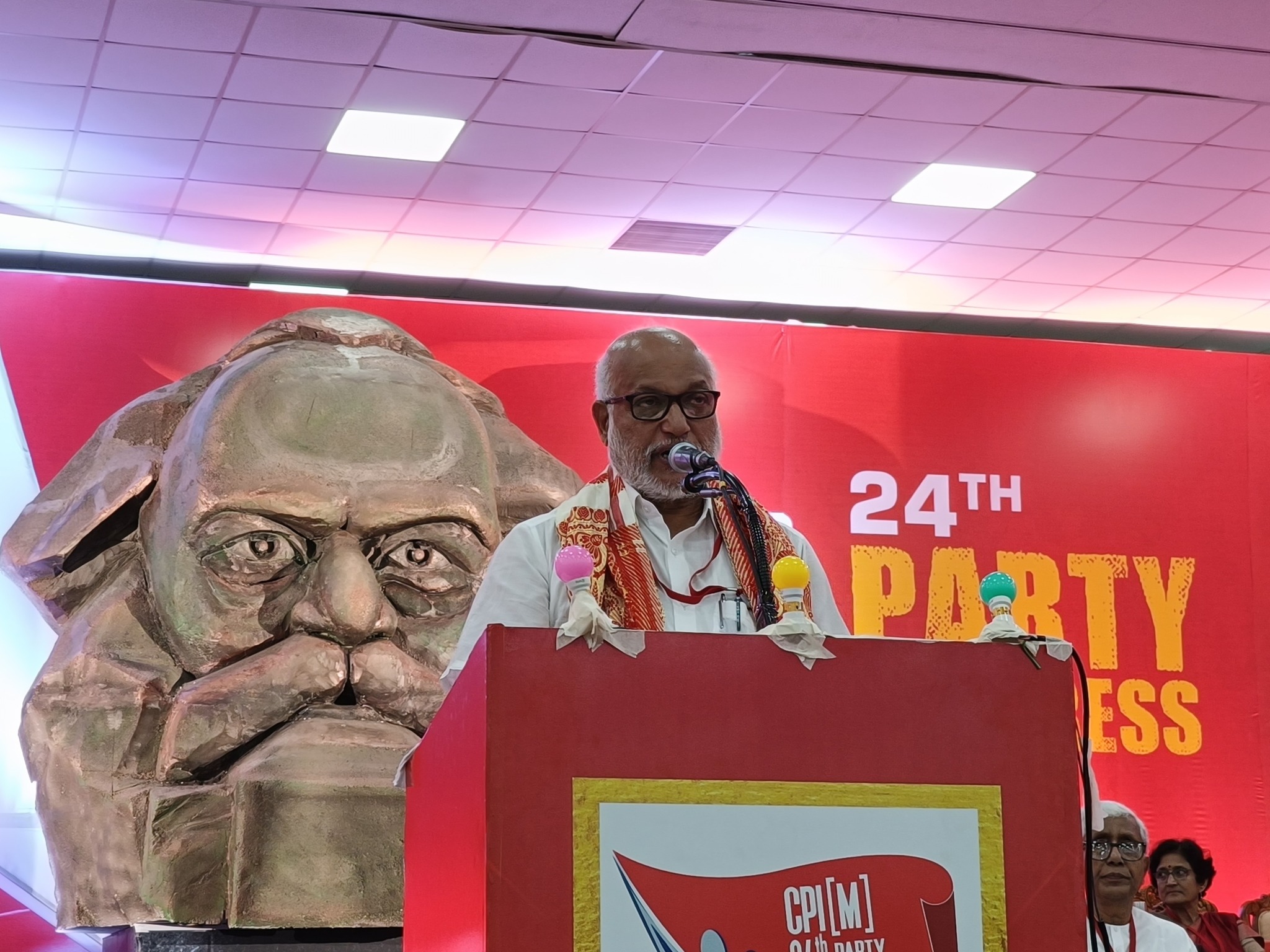
Comments :0