অরণ্য চৌধুরি
‘আইয়ারি’ সিনেমায় কর্নেল অভয় সিংয়ের সেই কথাটা মনে পড়ে? কাশ্মীরে এক মিশন শেষে বাড়ি ফেরার পথে মেজর জয় বক্সী ( সিদ্ধার্থ মালহোত্র) তাঁর রিপোর্টিং অফিসার অভয় সিং (মনোজ বাজপেয়ী)-কে জিজ্ঞেস করেন,‘‘স্যার চারিদিকে এত শিক্ষিত, পণ্ডিত লোকেরা আছেন। তারা সবাই একসঙ্গে মিলে কাশ্মীরের এই সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারছেন না?’’ উত্তরে কর্নেল অভয় বলেন, ‘‘একটা সমস্যা থাকায় অনেকের যখন লাভ হচ্ছে, তখন তা মেটানো হবে কেন? বরং তা জিইয়ে রাখতে হয়। কাশ্মীর কেবল এক জায়গার নাম নয়। কাশ্মীর এক বিরাট বড় বাজার। অনেকের দোকান এখানে চলছে।’’
আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যের মধ্যে আমরা রয়েছি। পুঁজি নাকি এখন যুদ্ধ চায় না। তাহলে যে দেশে দেশে এত নতুন অস্ত্র তৈরি হচ্ছে তার কেনা বেচা চলবে কী করে? যে কোনও নতুন অস্ত্র বাস্তবের মাটিতে কতটা কার্যকর, তা খদ্দেররা যাচাই করতে চায়। কোনও নতুন ধাঁচের অস্ত্র যদি ‘ব্যাটেল টেস্টেড’ (যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিত) হয়, তবে বাজারে তার চাহিদা অনেকখানি বেড়ে যায়। মুশকিল এই যে তার জন্য পুরোদস্তুর যুদ্ধ (টোটাল ওয়ার) প্রয়োজন। বাজারকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে, তাতে আবার পুঁজির মালিকরা জড়াতে চায় না। তাই বিশ শতকের শেষ দিক থেকে একুশ শতকের শুরুর দিকে এক নতুন ধরনের যুদ্ধের বেশি রমারমা। সামরিক পরিভাষায় একে বলা হয় ‘লিমিটেড ওয়ার’ বা সীমিত যুদ্ধ। এই ধরনের যুদ্ধ বা সংঘাতে কোনও পক্ষেরই বড় রকমের দখল অভিযান চালানোর উদ্দেশ্য থাকে না।
এটাও এক ধরনের যুদ্ধ, যেখানে আপামর সামরিক ক্ষমতা কোনও পক্ষই পুরোপুরি ব্যবহার করে না। তাই কেউই এমন কিছু করে বসে না যাতে অপর পক্ষের সেনা বা প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য অপর পক্ষকে পরাজিত করা নয়, বরং কোনও বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তাদের মনোবল দুর্বল করা। পুঁজি মালিকদের কাছে এই ধরনের সংঘাত বাধানোর মূল উদ্দেশ্য নতুন অস্ত্রের ‘ব্যাটেল টেস্টিং’। তার মারফত বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের বাজার, উৎপাদন ও উদ্ভাবনকে জিইয়ে রাখা।
সাধারণত ছোট, ক্ষমতাহীন দেশেই ‘লিমিটেড ওয়ার’ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি তথাকথিত ‘সুপার পাওয়ার’-দের হাতে থাকে। যে কোনও সময় বকুনি দিয়ে মিটিয়ে দেওয়া যায়। বিশ্ব বাজারেও বড় রকমের কোনও ধাক্কা লাগে না।
পহেলগামের ঘটনা এবং তারপর ভারত পাকিস্তানের দিন তিনেকের সংঘাত তারই এক উদাহরণ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এই যুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্যের থেকে বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনেক গুণ বেশি। নানা নতুন ধরনের অস্ত্রের ‘ব্যাটেল টেস্টিং’ সম্ভব হয়েছে। ফলে বাজার তাদের চাহিদা বেশ খানিকটা বেড়েছে। বিশ্বের প্রথম সারির অস্ত্র কোম্পানিগুলির শেয়ার মূল্যে বেশ প্রভাব পড়েছে। মুনাফার ক্ষীর খেয়েছে দেশি বিদেশি অস্ত্র ব্যবসায়ীরা।
প্রথম থেকেই অস্ত্র সেলসম্যানরা এই সংঘাতকে বড় মাপের এক বিজ্ঞাপনী মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেছে। পহেলগাম ঘটনার পর ভারত পাকিস্তানের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হওয়ার দিনকয়েকের মধ্যেই যুদ্ধের ফেরিওয়ালারা নানারকম বিশ্লেষণ শুরু করে দেন। বোঝাই যাচ্ছিল, দু’দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে এমন অনেক অস্ত্র ব্যবহার হবে যা আগে ‘ব্যাটেল টেস্টেড’ নয়। রণনৈতিক বিশ্লেষণের নামে শুরু হলো অস্ত্রের বিজ্ঞাপন। এতে চাপানউতোর আরও বাড়লো। আগুনে ঘি দিল কর্পোরেট মিডিয়া।
অপারেশন সিঁদুরের পরেই, হঠাৎ ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদ সংস্থা রয়টার্স খবর করল, পাক হানায় ভারতের রাফায়েল যুদ্ধ বিমান নাকি ধ্বংস হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রাফায়েলের উৎপাদক ‘ডাসল্ট এভিয়েশান’-র শেয়ার মূল্য হুড়মুড়িয়ে ৩ শতাংশ কমে গেল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল রাফায়েল আর জে-১০সি’র সংঘাতের ভিডিও। মেটা, এক্স’র অ্যালগোরিদমের খেলায় এসব ভিডিওর রিচ কয়েক মিনিটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভিউ পেলো। যত বেশি ‘ভিউ’ তত বেশি ‘রেভিনিউ’। তার আশায় ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে যুদ্ধের এই সমস্ত ‘এক্সক্লিউসিভ ফুটেজ’ শেয়ার করলেন হাজার হাজার দেশি বিদেশি ‘ইনফ্লুয়েনসার’। ভেঙে পড়া রাফায়েলের বেশ কিছু ছবিও ভাইরাল হলো। শেয়ার বাজারের তুর্কি নাচন অব্যাহত থাকলো।
পরে অবশ্য ‘অল্ট নিউজ’-র সৌজন্যে ধরা পড়ল এসব যাবতীয় ছবি, ভিডিও ফুটেজ ভুয়ো। আরও ঘাঁটাঘাঁটি করে জানা গেল ‘আর্মা থ্রি’, ‘মেটালস্টর্ম’, ইত্যাদি ভিডিও গেম থেকে এসব ফুটেজ নেওয়া। রাফায়েল আর জে-১০সি’র মধ্যে কোনও সংঘাত বাঁধেনি। যে ছবি ভাইরাল হয়েছে তাও অন্য এক ঘটনার। ভারতীয় বায়ুসেনার কোনও রাফায়েল আদৌ ধ্বংস হয়েছে কিনা তারও কোনও প্রমাণ মেলেনি।
তবে কি নেহাতই ‘স্টক প্রাইস ম্যানিপুলেশান’-র ধান্দায় ‘অস্ত্র সেলসম্যানরা’ এমন খবর রটিয়েছিলেন? পশ্চিমা বিশ্বে ফরাসী সংস্থা ডাসল্টের মোক্ষম প্রতিযোগী মার্কিন সংস্থা ‘লকহিড মার্টিন’। ডাসল্টের নামে অপপ্রচার করতেই ‘লকহিড মার্টিন’ ঘনিষ্ঠ কেউ এই ভুয়ো প্রচার করিয়েছে? প্রত্যাঘাতে অপর পক্ষকেও কিছু না কিছু করতেই হতো। তাই হঠাৎ ছড়িয়ে দেওয়া হলো ভারতের হামলায় এফ-১৬ ধ্বংস হওয়ার খবর। পাক বায়ু সেনার এই বিমান ‘লকহিড মার্টিন’-র তৈরি। শুর হলো পালটা জল্পনা। একই কায়দায় হাজার হাজার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ছড়ালো ‘এক্সক্লিউসিভ ফুটেজ’। উৎস আবারও আর্মা-থ্রি। গোদি মিডিয়া এই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করল। সঙ্গে দাবি করা হলো, রাশিয়ার তৈরি এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়েই নাকি এফ-১৬’কে ধ্বংস করা হয়েছে। কিছুক্ষণ এই খবর বাজারে খুব চলল। লকহিড মার্টিনের শেয়ার মূল্য ওঠানামা করল। এস-৪০০’র দক্ষতা নিয়ে বাজারে আলোড়ন পড়ে গেল।
তবে অচিরেই এই মিথ্যা ধরা পড়ল। ভারতের বায়ুসেনা কোন এফ-১৬ বিমান ধ্বংস করার কথা এখনও দাবি করেনি। জানা গেল, এই সময়কালে এস-৪০০ ব্যবহারই করা হয়নি। সামরিক বিশেষজ্ঞদের এও অনুমান, পাক বায়ু সেনা কোনও এফ-১৬ নামায়নি। তার কারণ, ভারতের বিরুদ্ধে এফ-১৬ বিমান ব্যবহারের অনুমতি পাকিস্তানের নেই। আরেকটি কারণ, এফ-১৬’র মতো বিমানের বিরুদ্ধে সাধারণত এস-৪০০’র মতো সিস্টেম ব্যবহার করতে হয়। ভারতের সেনা আধিকারিকরা যেখানে স্পষ্ট জানিয়েছেন এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যবহার হয়নি, তখন এটাই ধরে নিতে হয় যে তা ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজনই পড়েনি। অর্থাৎ ভারতের আকাশপথে কোন এফ-১৬ বিমান ঢোকেনি। তবে ভুয়ো প্রচারে বাজারে এস-৪০০’র চাহিদা অনেক গুণ বেড়েছে।
অস্ত্র সেল্সম্যানদের কাছে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে দু’দেশের ড্রোন ব্যবহার। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে ইজরায়েল প্যালেস্তাইন যুদ্ধ সর্বত্রই ড্রোন প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ‘সোয়ার্ম অ্যাটাক’ কৌশল অবলম্বন করে, সহকারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একসঙ্গে হাজার হাজার আত্মঘাতী ড্রোন নিয়ে হামলা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই শত্রুপক্ষ ধ্বংস করতে পারে ঠিকই, তবে তাতে তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কার্যকারিতা এবং দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসে যায়। ‘লিমিটেড ওয়ার’-র জন্য এই ড্রোন ব্যবহার একেবারে আদর্শ। শত্রুপক্ষের বড় রকমের ক্ষতি করবে না তবে নাজেহাল করে রেখে দেব। ‘সোয়ার্ম অ্যাটাক’-র তেমন খরচও নেই। হাজার হাজার ড্রোন ধবংস হলেও মোটে কয়েক হাজার ডলার জলে যায়। বরং এই ড্রোন হামলা আটকাতে গিয়ে শত্রুপক্ষের কয়েক লক্ষ ডলারের বহু ‘সারফেস টু এয়ার’ মিসাইল খরচ হয়ে যায়।
ভারতে ‘সোয়ার্ম অ্যাটাক’-র জন্য পাকিস্তান ব্যবহার করেছে তুরস্কের ‘আসিসগার্দ’ ড্রোন। অপারেশন সিঁদুর সহ নানা প্রত্যাঘাতী হামলায় ভারত ব্যবহার করেছে ইজরায়েলের তৈরি ‘হারোপ’ ড্রোন। মধ্যপ্রাচ্যের অস্ত্র বাজারে দুই প্রতিযোগী দেশের তৈরি অস্ত্রের মুখোমুখি লড়াই দেখার সুযোগ এর আগে তেমনভাবে মেলেনি। এই সমস্ত ড্রোন হামলায় দু’পক্ষেরই যে গুরুতর কোনও ক্ষতি হয়েছে এমনটা নয়। তবে দু’দেশের সেনার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকেই বেশ নাজেহাল করা গেছে। একই সঙ্গে দু’দেশের ব্যবহৃত ‘অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম’-র বাজার দরও বেশ খানিকটা বেড়েছে। ভারতের ব্যবহৃত ইজরায়েলী ‘এমআর-এসএম’, ‘বারাক‘ মিসাইল ইত্যাদির বাজার দর তর তর করে বেড়েছে। একই কায়দায় সোশাল মিডিয়া প্রচার হয়েছে ভুয়ো বিজ্ঞাপনি ভিডিও।
এদিকে ভারতের বায়ুসেনার যে পাঁচটি যু্দ্ধ বিমান ধ্বংস হওয়ার খবর রটেছে, সেই সুযোগে নয়াদিল্লির কাছে আবার এফ-৩৫ বিমান কেনার সুপারিশ নিয়ে হাজির হয়েছে মার্কিন-ইজরায়েলী অস্ত্র সেলসম্যানরা। গত কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় বায়ুসেনায় অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের ঘাটতি সরকারের কাছে এক বড় রকমের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন খোদ বায়ুসেনা প্রধান। আন্তর্জাতিক মহলের কাছেও তা অজানা নয়। মোদীর সঙ্গে গত বারের সাক্ষাতেই এই বিমান কেনা বেচার ‘অফার’ দেন ট্রাম্প। আবারও সেই ‘অফারের গুঞ্জন উঠেছে বিশ্ব অস্ত্র বাজারে।
প্রসঙ্গত, একটা ‘এফ-৩৫’ বিমানের মূল্য ৯৯৬ কোটি টাকা। এক ঘণ্টার উড়ানে তার পিছনে অন্তত ৩২ লক্ষ টাকা খরচ হয়। বিভিন্ন সমীক্ষক জানিয়েছেন ভারতের বায়ুসেনা যদি অন্তত এক স্কোয়াড্রন এফ-৩৫ কেনে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে যা অর্থের প্রয়োজন পড়বে, তা ভারতের জাতীয় আয়ে সঙ্কুলান করা কঠিন। যদি অন্তত ৫০ বছর একটি স্কোয়াড্রন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তার পিছনে প্রতি বছর দেশের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অন্তত ১৭ শতাংশ ব্যয় করতে হবে। ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা বাজেটের থেকে তা অন্তত আট গুণ বেশি।
শুধু তাই নয়, এফ-৩৫ সহ যে কোনও যুদ্ধবিমানের সময়োপযোগিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সামরিক বিশ্লেষক ও প্রযুক্তিবিদদের বড় অংশ। খোদ এলন মাস্ক বলেছেন, ড্রোন এবং অন্যান্য রিমোট পরিচালিত যুদ্ধাস্ত্র চলে আসার পর পাইলট চালিত যুদ্ধবিমানের লোপ পাওয়া কার্যত সময়ে অপেক্ষা। বহু মার্কিন জোটসঙ্গীই আর এই বিমান কিনতে চাইছে না। আমেরিকার বায়ুসেনাও আর এই বিমান নিতে চায় না। ফলে লকহিড মার্টিনের গুদামে সারি সারি এফ-৩৫ পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। এই বিমান যাতে আমেরিকা কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে কড়া দামে বিক্রি করে, তার জন্য এই সংস্থার কর্তারা হোয়াইট হাউসের উপর বেশ কয়েক বছর ধরে চাপ সৃষ্টি করছে। ভারতের উপর আগেও এই নিয়ে আমেরিকা চাপ দেয়। চলতি পরিস্থিতিতে এই চাপ আরও বাড়বে বলে কূনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।
দুই প্রতিবেশী দেশের দিন তিনেকের সংঘাতে ভারতের সামরিক পরিকাঠামোর বেশ কিছু দুর্বলতা ও ঘাটতি প্রকাশ্যে এসেছে। অস্ত্র আমদানির বিষয়ে খদ্দের নির্বাচন এবং সংলগ্ন সরকারি নীতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। মোদী সরকারের আমলে অস্ত্র কেনাবেচায় সব থেকে পরিবর্তন দেখা গিয়েছে আমদানির ক্ষেত্রে। দেড় দশক আগে ভারতের যাবতীয় অস্ত্র আমদানির ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ আসত রাশিয়া থেকে। এখন তা কমে ৩৬ শতাংশে এসে ঠেকেছে। অন্যদিকে ফ্রান্সের থেকে আমদানির হার বেড়েছে ৩৩ শতাংশে। ইজরায়েলের বেড়ে হয়েছে ১৩ শতাংশ, আমেরকিার বেড়ে হয়েছে ১০ শতাংশ। অর্থাৎ ভারত পশ্চিমা দেশগুলি থেকে ৫৬ শতাংশ অস্ত্র আমদানি করে থাকে। বোঝাই যাচ্ছে রাশিয়া এই সংঘাতে অন্য বারের মতো নিঃশর্ত ভাবে ভারতের পাশে কেন দাঁড়ায়নি।
রাশিয়ার তৈরি অস্ত্র ফরাসি, ইজরায়েলী বা মার্কিন অস্ত্রের তুলনায় অনেক সস্তা। তবুও ‘ডাইভার্সিফিকেশন’ (বৈচিত্রকরণ)-র নামে এমন স্ববিরোধী বাণিজ্য চুক্তিতে মোদী সরকার রাজি হয়। দেশের মানুষের সামনে দাবি করা হয় যে এই সমস্ত অস্ত্র নাকি রাশিয়ার সস্তা অস্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক ও সময়োপযোগী। তবে এত সংখ্যক সাদা হাতি কিনেও যে যুদ্ধজয় করা যায়নি, তা বুঝে এখন সামরিক বিশেষজ্ঞদের টনক নড়েছে।
একদিকে ভারত যেমন অস্ত্র বৈচিত্রকরণের দিকে এগিয়েছে , পাকিস্তানও অস্ত্র কেনা বেচার জন্য পুরোপুরি আমদানি নির্ভর হয়ে গিয়েছে। এতে প্রযুক্তিগত কোনও লাভ হয়নি, তবে কৌশলগত লাভ কি হতে পারে সেদিকেই নজর রেখেছে পাকিস্তান। ফলে সংঘাতের সময়কালে আন্তর্জাতিক মঞ্চ পাকিস্তানের মতো ভারতকেও সংঘর্ষ বিরতির দিকে এগনোর জন্য চাপ বাড়াতে পেরেছে। আসলে মোদী সরকারের ‘পাঁচ নৌকায় পা দেওয়া নীতি’ আর পাকিস্তানের ‘বিকিয়ে দেওয়া নীতি’-র লড়াই বলে একে ধরা যেতেই পারে। দুই নীতিই চূড়ান্ড অপদার্থ এবং অপমানজনক। কিন্তু তাতে হুঁশ ফিরবেনা কারও।



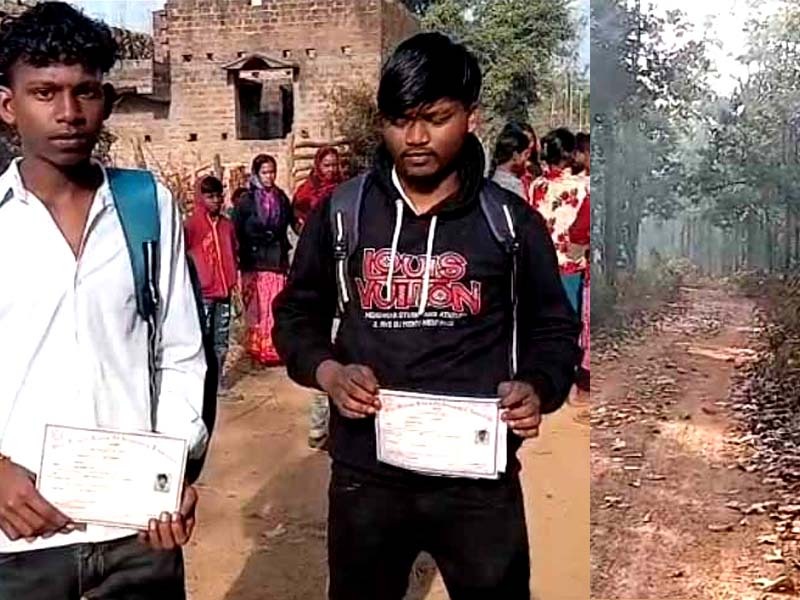




Comments :0