দেবাঞ্জন দে
এসআইআর শুরু হয়ে গেছে বাংলায়। আগেও এই ধরনের ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণের অভিযান চালিয়েছে নির্বাচন কমিশন। লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট— নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, যাতে ন্যায্য ভোটার বাদে মৃত, স্থানান্তরিত, একাধিক স্থানে তালিকাভুক্ত ভোটারদের চিহ্নিত করা যায়। একই সাথে নতুন ভোটারদের যুক্ত করা যায় ব্যাপক আকারে। অতএব সংশোধনীর লক্ষ্য ছিল সংযোজন। অথচ এই বছরের বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে কার্যত পরিণত করা হয়েছে ব্যাপক অংশের গরিব, প্রান্তিক মানুষকে বিয়োজনের মাধ্যম হিসাবে। হাবভাবটা এমনই যেন প্রচুর মানুষকে বাদ দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য। বিজেপি'র নেতারা মোটামুটি কোটিতে পৌঁছে গেছেন বাদ দেওয়ার দৌড়ে। তৃণমূল চেষ্টা করছে তার ভুয়ো ভোটারের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা করতে। মানুষ দিশাহারা হয়ে বুঝে উঠতে পারছেন না যে, গত কয়েক বছর ধরে একের পর এক যে অধিকার প্রয়োগ করে সে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে নানান আইনসভায় পাঠালো, সেই অধিকারই যদি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে সেই প্রতিনিধিরা ন্যায্যতা পাবে কেন!
মানুষ এও বুঝতে পারছেন না— যে কাজ নির্বাচন কমিশন এর আগে অনেক বেশি সময় নিয়ে করেছে, সেই কাজ মাত্র তিন মাসে নামিয়ে আনার হুড়োহুড়িটা কীসের? যে কাজের ভিত্তি হিসাবে বরাবরই থেকেছে সবচেয়ে সাম্প্রতিকতম ভোটার তালিকা, সেই কাজেরই ভিত্তি কেন করা হচ্ছে ২৩ বছর আগের একটি ভোটার তালিকাকে? যে নথিপত্র চাওয়া হয়েছে তার সাথে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রশ্নটাকে বারবার জুড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? নির্বাচন কমিশন কবে থেকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঠিকেদারি পেলো, ওটা তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজ! নথিপত্রের মধ্যেও নির্বাচিত সরকার প্রদত্ত প্যান কার্ড, নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার কার্ড, এমনকি প্রাথমিকভাবে কার্যত গোটা দেশকে লাইনে দাঁড় করিয়ে এগুলির সাথে লিঙ্ক করানো আধার কার্ড (পরে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে যুক্ত হয়েছে যদিও আবার শর্তাবলী প্রযোজ্য মার্কা দিয়ে), কেন থাকবে না? যে প্রক্রিয়া এর আগেও হয়েছে তালিকার নির্ভুল সংশোধনের জন্য তার সাথে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত আলোচনাই বা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? কেনই বা একটি তথাকথিত সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার এহেন অসাংবিধানিক প্রয়োগ ঘটানো, যেখানে এর সাংবিধানিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলোকে অমীমাংসিত রাখা হয়েছে হয়তো ইচ্ছে করেই। যাতে একটা ভয়ভীতির পরিবেশ গড়ে ওঠে। যাতে সেই পরিবেশে রাজনৈতিক, সামাজিক মেরুকরণ তীব্র করা যায় আর ক্রমাগত দেশের বুকে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক মেরুকরণকে জনমানসে লঘু করে দেওয়া যায়।
এই অমীমাংসিত প্রশ্নগুলিই তৈরি করছে সংশয়। সাথে যুক্ত হয়েছে বিজেপি’র নেতাদের ঘৃণা ছড়ানো ও তৃণমূল নেতাদের মিথ্যা ভাষণ। যেমন খুশি বানানো সংখ্যায় বাংলাদেশি বলে বের করে দেওয়ার হুমকির মাধ্যমে আসলে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে। আবার ঘুরপথে এর থেকে মুনাফা তোলার চেষ্টায় তৃণমূল। তাহলে কী এদের মুনাফা করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এসআইআর? বিপদের মুখে উদ্বাস্তু, আদিবাসী, মহিলা, পরিযায়ী শ্রমিক, মতুয়া সম্প্রদায়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরা। সবক্ষেত্রেই তৃণমূল নিজের ভোটব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তারপর দিল্লির নির্দেশে ভাগাভাগি করে নিয়েছে আরএসএস'র প্রকাশ্য এজেন্সি বিজেপি, গোপন এজেন্সি তৃণমূলের মধ্যেই। এসআইআর’র অসাংবিধানিক, অতি দ্রুত প্রয়োগের ফলাফল বিহারেও যেমন বিস্ফোরক হয়েছে। মোট যা বাদ গিয়েছে তার প্রায় অর্ধেক মহিলা ভোটার এবং প্রায় সবটাই গরীবগুর্বো মানুষ।
সঙ্কটে, সংশয়ে, নানা অসুবিধায়, নানাবিধ প্রশ্নে পড়তে চলেছে ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটাধিকারও, সমাজের সবচেয়ে তরুণতর অংশের ভোটাধিকার। যাদের ক্যাম্পাসে ভোটাধিকার পরিকল্পিতভাবে স্থগিত রাখা আছে গত আট বছর ধরে। যাদের ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের অনুশীলন বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় আগে। যাদের মন, মগজ থেকে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র (মানে সংবিধানের প্রস্তাবনা ভারতকে যে যে বিশেষণে ভূষিত করেছে) সেই সমস্ত চেতনাগুলো মুছে দেওয়ার জন্য পুনর্গঠন করা হয়েছে সিলেবাস। যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গণতন্ত্রের মানে বুঝেছে কেবল ইভিএম'র বোতামটুকু টিপতে পারা। এবার কি সেটুকু অনুশীলনের ক্ষেত্রটাও কেড়ে নেবে রাষ্ট্র?
বাংলায় সরকারি শিক্ষার বেহাল দশা। প্রতিদিন বন্ধ হচ্ছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। পরিকাঠামোর জন্য সরকারি ব্যয়ও তলানিতে। সরকারি পরিকল্পনাতেই আগ্রহ কমানো হয়েছে লেখাপড়ার প্রতি। এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের জায়গায় সমাজে উৎপাদিত হয় পরিযায়ী শ্রমিক। সেই ব্যবস্থার ফলাফলেই ১৮-২৫ বছর বয়সি ছেলেরা, যাদের জায়গা হওয়ার কথা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ঘরছাড়া ভিনরাজ্যের স্বল্প মজুরির মজুর এখন। উচ্চ মাধ্যমিক পার করার পর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে আর কলেজমুখী হচ্ছে না। এবছরও সেই সংখ্যা প্রায় লাখ চারেক। উৎসবের মরশুম কাটিয়ে এরা সবাই এখন কোনও না কোনও রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে কাজ করছে। যে ধরনের কাজে এরা যুক্ত হয়, মূলত রাজমিস্ত্রী, স্টোরকিপার, সোনার কাজ, জরির কাজ, হোটেলের ওয়েটারের কাজ, পাথর ভাঙার কাজ, খনির কাজ ইত্যাদি— এসব ছেড়ে বাড়ি ফেরাও সম্ভব নয়। তাতে ঠিকেদারের কাছ থেকে মজুরি মিলবে না। কী হবে এই লক্ষ লক্ষ ছেলেপুলের? কী হবে এদের ভোটাধিকারের? কোনও বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান কি দেবে নির্বাচন কমিশন?
আবার উল্টোপিঠের সমস্যাটা আরেকরকম। রাজ্যের সরকারি শিক্ষা পরিকাঠামোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বেশি টাকা খরচ করে পড়তে যেতে বাধ্য হয়েছে বহু ছেলেমেয়ে। দেশের গবেষণা খাতে ক্রমাগত সরকারি বরাদ্দ কমতে থাকার কারণে বহু মেধাবী ছেলেমেয়ে পাড়ি দিয়েছে বিদেশ। এখন সেমিস্টারের মাঝপথে ফিরে আসা অসম্ভব। গবেষণার মাঝে বিদেশ থেকে ফেরার খরচ বহন করাও সম্ভব নয়। এদিকে ভয়, আতঙ্ক গ্রাস করছে মনে। মার্কিন মুলুকে গবেষণারত এক গবেষক, বাবা-মা'র নাম উঠেছে তালিকায় ২০০৬-০৭ সাল নাগাদ। দাদু মারা গেছেন আশির দশকেই। তাকে যদি নিজের ভোটাধিকার রক্ষা করতে তবে সশরীরে উপস্থিত হতে হয় ট্রাইবুনালে, তাহলে যতটুকু টাকা স্টাইপেন্ড পায় তার সবটাই চলে যাবে যাতায়াতে! কী উপায়? এদের ভোটের অধিকারটুকু এদের টেনে রাখে ভিটেমাটির কাছাকাছি। এরা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অবজ্ঞাজনিত অ্যাকাডেমিক উদ্বাস্তু। তবে কি এর ন্যূনতম ভোট দেওয়া অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে?
পশ্চিমবঙ্গ এখন বাল্যবিবাহে দেশের শীর্ষে। ক্লাস সেভেন-এইটের পড়া মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রামে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে কমে যাচ্ছে ছাত্রীসংখ্যা। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক গার্লস স্কুল। কন্যাশ্রীর ঢক্কানিনাদে চাপা থাকছে বাংলার বাল্যবিবাহে উর্ধগামী গ্রাফ। এই মেয়েরাই যারা এখন ১৮-২৫ বছর বয়সি, তারা হয় স্থানান্তরিত হয়ে চলে গেছে অন্য গ্রামের শ্বশুরঘরে, অথবা পাড়ি দিয়েছে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক স্বামীর সাথে। কীভাবে নথিভুক্ত হবে এরা? পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এরা, এবার কী তাহলে ভোটদানের অধিকার থেকেও?
প্রবল দুর্যোগে দার্জিলিঙ, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। জলের তোড়ে, কাদার ধসে নষ্ট হয়ে গেছে বহু মানুষের জরুরি নথিপত্র। মুর্শিদাবাদ, মালদায় নদীপার ভেঙে ভেসে গেছে একের পর এক গ্রাম। পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক জায়গা মাঝেমধ্যেই চলে যাচ্ছে জলের তলায়। এই দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া নথিপত্র মানুষের দরজায় পৌঁছে ফেরত দেওয়ায় দায় সরকারের। উলটে সরকারই এখন দরজায় কড়া নেড়ে চাইছে সেসব নথিপত্র দেখতে! মানবিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে এই মানুষগুলোর সমস্যা। নথির অভাবে বলপূর্বক নাম বাদ দেওয়া চলবে না কোনোভাবেই।
একসময় এই বাংলায় দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের কাজ পাওয়ার জায়গা– শিল্পাঞ্চল বিশেষত চটকল, চা বাগান, খনি এলাকা জুড়ে নানা রাজ্যের মানুষ কাজের তাগিদে বসতি পেতেছে এখানে বছরের পর বছর। তাদের অনেকের নাম ২০০২ সালের তালিকায় না থাকাই স্বাভাবিক, বিশেষত যারা তার পরে এসেছেন এখানে কাজের সূত্রে। এই সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও তাই খুঁজে পাবে না বাবা-মায়ের নাম ঐ তালিকায়। আবার সরকারের তথ্য সংরক্ষণের গাফিলতিতে আরও অনেক তরুণ ভোটারই বাবা-মায়ের নাম পাচ্ছে না ঐ পুরানো তালিকায়। অনেকেই বেড়ে উঠেছে মা-বাবার পরিচয় ছাড়াই। বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে এই সমস্যাগুলোর জন্য। মাথায় রাখতে হবে এই সমস্যার সম্মুখীন হবে মূলত গরিব, খেটে খাওয়া পরিবারের মানুষজন। বাবা-মায়ের নাম না থাকার দরুন কোনো অংশেরই নতুন তরুণতম ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।
বর্ডার এলাকায় বসবাসকারী গরিব, প্রান্তিক মানুষ নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে জীবনধারণ করে। অল্প কিছুদূর লেখাপড়া করেই স্কুলছুট হয়ে যায় এরা। যুক্ত হয়ে যায় চাষবাস, পাথর কাটা, খেতমজুরি, বিড়ি বাঁধার মতো কাজে। স্কুলের নানা স্তরের সার্টিফিকেট এদের ক্ষেত্রে মান্যতা দিতে হবে বৈধ নথি হিসাবে। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে শিলমোহর দিতে এদের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বৈরীমূলক আচরণ করা যাবে না।
স্কুলস্তরে একটা বড় সমস্যা তৈরি হতে চলেছে। রাজ্যের হাজার হাজার মৃত স্কুলের মৃত্যুর কারণ শিক্ষকের অভাব। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট বলছে রাজ্যের প্রায় ৬৫০০ স্কুল চলছে মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে। তারই মধ্যে বুথ লেভেল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে হাজার হাজার স্কুল শিক্ষক। বিডিও'রা মৌখিক নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে স্কুল বাদ দিয়ে সারাদিন এসআইআর’র কাজ করতে। এভাবে কার্যত বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে আরও কয়েক হাজার স্কুল। লেখাপড়ার আঙিনা থেকে ছিটকে যাবে আরো কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী। কে দায় নেবে? বিডিও, ডিএম, নির্বাচন কমিশন নাকি সরকার?
এই তরুণতম অংশের নির্বাচকমণ্ডলী রেগে আছে দুই সরকারের প্রতি। এদের ডবল ইঞ্জিন রাগ ঘুরিয়ে দিতে পারে চাকা। এরা বুঝে গেছে এদের স্বপ্নহীনতার কারণ তৃণমূল-বিজেপি'র বেকার ম্যানুফাকচারিং নীতি। এদের পড়ার অধিকার, নিজের রাজ্যে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে ক্যাম্পাসে পড়তে যাওয়ার অধিকার, নিজেদের জীবনটাকে উন্নত করে গড়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে দুই সরকারের চক্রান্তে। এই নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এদের ভোটদান থেকে দূরে রাখতে। এরা বিকল্প খুঁজছে। খুঁজছে সৎ পথে, উন্নত জীবনযাপনের উপায়। খুঁজছে ক্যাম্পাসে, লেখাপড়ার মূলস্রোতে ফিরে আসার ডাক। খুঁজছে লাল ঝান্ডাই সেই অবৈতনিক শিক্ষা, উন্নত পরিকাঠামো, নিত্যনতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা গড়া, একের পর এক কাজের সন্ধান, উদ্ভাবনী শক্তির প্রত্যয় । এরা একটা নতুন বাংলা গড়তে চায়। এসআইআর’র অসাংবিধানিক প্রয়োগে এদের সেই নয়া বাংলা গড়ার ভোটটুকু কেড়ে নেওয়া চলবে না।




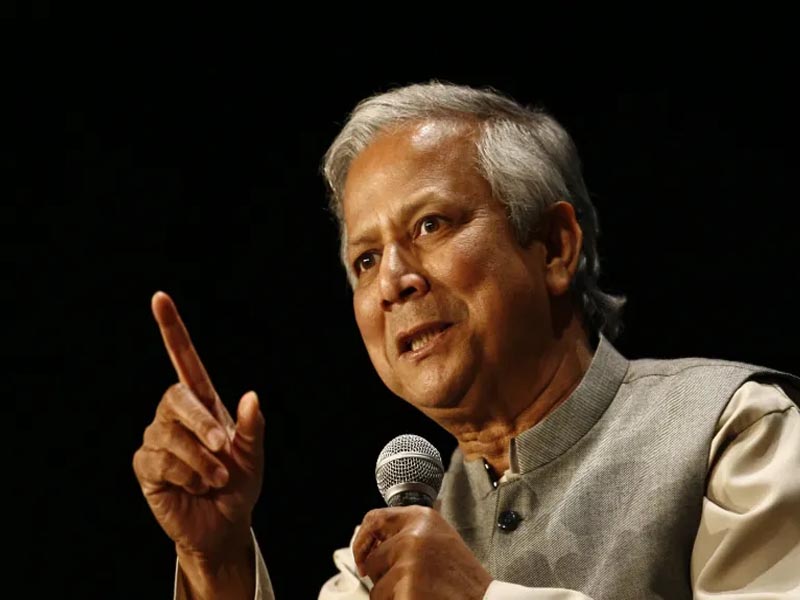



Comments :0