সুব্রত চট্টোপাধ্যায়
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম থেকে তাঁর কবিতা সচেতনভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতের এই উপেক্ষার কথা বোধহয় তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই লিখেছিলেন-’ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,/ আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ’। পাঠকদের মনে পড়বে, প্রায় একই কথা লিখেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম–’ কবি ও অকবি যাহা বল মোরে, মুখ বুজে সই সবই’। হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন, আমরা আলোচনা করছি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা। মেজ বৌদি রেণু দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— ’আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।’ তাহলে প্রশ্ন হল ‘জনতার কবি’ হলে কি ঠিক কবি হওয়া যায় না? আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা, বুদ্ধদেব বসু সুকান্তের কণ্ঠে ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আবার কবিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে, ‘খবুরে কাগজে পদ্য লিখে শক্তির অপব্যয় করছো; তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়।’
আসলে আমাদের দেশে আধুনিক কবিতার জন্ম হয়েছিল ঔপনিবেশিক পরিবেশে। ফলে এক ধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতায় জারিত হয়েছিল আধুনিক কবিতার ব্যাপ্ত ভুবন। গড়ে উঠেছিল বিশুদ্ধ কবিতার একটি ধারণা। আত্মমগ্ন মোহময় আবেগে আবদ্ধ হয়ে গেল আধুনিক বাংলা কবিতা। এর বিপরীতেও একটি স্রোত ছিল। সেই স্রোতকে বারে বারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। আমাদের দেশে যেমন সামন্তবাদ-পুঁজিবাদ পোষিত সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা আছেন, তেমনি চিরকালই গণতান্ত্রিক-সমাজবাদী চিন্তা প্রসূত সংস্কৃতির একটি প্রবাহও ছিল। সুকান্ত এই দ্বিতীয় স্রোতের সার্থক প্রতিনিধি।
আধুনিক বাংলা কবিতার পূর্ণ বলয়টি গড়ে ওঠে বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। আধুনিক কবিতার এই যে পূর্ণ পর্বটি, তার বহু তল বহু রং। কিন্তু একটি জায়গায় সকলের ঐক্য ছিল, তা হলো প্রত্যেকেই ছিলেন নাগরিক কবি। তাই বৃহত্তর জনমানসে সেই সব কবিতার তেমন কোনও আবেদন ছিল না। ঠিক এই সময় পর্বের চারের দশকে আবির্ভাব ঘটে কবি সুকান্তের। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জন মানসের হৃদয়কে তিনি যেন জয় করে নেন।
সুকান্ত ছিলেন যুগের সৃষ্টি এবং যুগ স্রষ্টা। অভ্রান্তভাবে তিনি যুগের ধারা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যুগ-প্রেক্ষাপটের সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা না করলে কবি সুকান্তকে এবং তাঁর কবিতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর কবিতার মূল প্রেরণা রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত। এক অস্থির সময়ে কবি হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সর্বোপরি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন–এই সবকিছুই তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিভাবে পরতে পরতে সুকান্তর কবিতা রাজনীতির বহমান ঘূর্ণাবর্তকে ধারণ করে রেখেছিল, তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
একদিকে দেশে চলছে মুক্তি সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, অন্যদিকে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। এই আগ্নেয় সময়ে সুকান্তের আবির্ভাব। জাপানি ফ্যাসিবাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আক্রমণ করে। বোমা পড়ে চট্টগ্রামে, ফেণিতে ও কলকাতায়। শহর কলকাতার তখন অন্য চেহারা। রাতে নিস্প্রদীপ। মিলিটারির দাপাদাপি। আকাশে জাপানি বোমারু বিমানের অতর্কিত হানা। এই দুর্বিষহ সময়ে লাখে লাখে মানুষ কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে সুকান্ত কলকাতা ছেড়ে যেতে পারেননি। সেই ঝড়ো সময়ের ইতিবৃত্ত লেখা আছে কবি বন্ধু অরুণাচল বসুকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। এই সময়ে তিনি যুদ্ধ বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হলো ‘চট্টগ্রাম ১৯৪৩’, ‘লেনিন’, ‘দিন বদলের পালা’, ‘মণিপুর’ এবং ‘রোম ১৯৪৩’। ‘পূর্বাভাস’ কাব্যের একটি কবিতায় তিনি লিখলেন– ‘‘ সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পুব দরজায়,/ ফেণী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।/ বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,/ বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।’’
১৯৪৩ -এ বাংলায় দেখা দিল মহা মন্বন্তর। দেশের তখন চরম দুর্দিন। একদিকে জাপানি আক্রমণের ভ্রুকুটি, অন্যদিকে ভয়ঙ্ককর দুর্ভিক্ষ। জনরক্ষা সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সুকান্ত ত্রাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর কাজ ছিল খাদ্য আন্দোলন করা, রেশন দোকানে লাইন সাজানো। কবিতায় তিনি লিখলেন– ‘’আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,/ আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।’’ ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করে। এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার পড়েছিল সুকান্তের ওপরে। ‘আকাল’ নামক সেই সংকলনের মুখবন্ধে তীব্র মর্মস্পর্শী ভাষায় কবি লেখেন– ‘’১৩৫০ সম্বন্ধে কোনও বাঙালিকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? কেননা ১৩৫০ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।’’ দুর্ভিক্ষ সুকান্তর মনে গভীর ছাপ রেখে গেল। তিনি কয়েকটি মর্মান্তিক গল্প লিখলেন– ‘ক্ষুধা’, ‘দুর্বোধ্য’ এবং ‘দরদী কিশোর’। সৃষ্টি হলো কয়েকটি অসাধারণ কবিতা– ‘ঐতিহাসিক’, ‘বিবৃতি’, ‘বোধন’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’। ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ কবিতায় নিজের অবস্থান জানাতে গিয়ে তিনি লিখলেন–’’আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,/ প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।’’ দুর্ভিক্ষ যারা সৃষ্টি করল তিনি তাদের প্রতি উচ্চারণ করলেন তীব্রতম ঘৃণা–’’আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই/ স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।’’
পরবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষে পঙ্গু হয়ে যাওয়া কৃষক সমাজকে জাগানোর কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। কৃষকদের উদ্দীপ্ত করাই তাঁর তখন প্রধান দায়বদ্ধতা। তিনি একে একে লিখলেন ‘এই নবান্নে’,’কৃষকের গান’, ‘ফসলের ডাক: ১৩৫১’ ইত্যাদি উদ্দীপনা সঞ্চারী কবিতা। এসবের পাশাপাশি তিনি ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নিজেকে গড়ে তোলেন একজন ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসাবে। পরে ১৯৪৪ সালে ‘কিশোর বাহিনী’র প্রধান হিসাবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইসবেরই পরিণতিতে ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার কিশোর সভা বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্ব পান তিনি। সম্পূর্ণ অভিনব কিশোর সাহিত্যের ধারা গড়ে তোলেন। লেখা হতে থাকে ‘মিঠেকড়া’র ছড়া, ‘হরতাল’-এর গল্পনাটিকা এবং কাব্যনাটিকা ‘অভিযান’। এদিকে বিশ্ব রাজনীতিতে পালাবদল শুরু হয়। ১৯৪৫ এর ৯ মে জার্মানির বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পৃথিবী বিপদ মুক্ত হয়। কবি সুকান্ত সেই পটভূমিতে নতুন রূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কামনা করলেন– ‘’এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণসঙ্গীতের সুর;’’। সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছে, কিন্তু দেশ তখনও পরাধীন। আন্দোলনে আন্দোলনে গোটা দেশ তখন অস্থির। লালকেল্লায় আজাদহীন ফৌজের যোদ্ধাদের বিচার শুরু হয়। প্রতিবাদে ১৯৪৫ এর ২১ নভেম্বর ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হলো। আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর গুলি চালানো হয়। শহীদ হয়ে যায় রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় এবং আব্দুস সালাম। কিছুদিন পরে চট্টগ্রামে ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনের উদ্বোধন হলো সুকান্তের বিখ্যাত ‘ঠিকানা’ কবিতা দিয়ে। সেখানে ধর্মতলায় গুলি চালানোর প্রসঙ্গ এল এভাবে–’’জালালাবাদের পথ ধরে ভাই/ ধর্মতলার পরে,/ দেখবে ঠিকানা লেখা/ ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।’’ ১১ ফেব্রুয়ারি রশিদ আলি দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতায় প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থান ঘটল। দেশজুড়ে চলতে থাকে আন্দোলন ও ধর্মঘট। বিমানবাহিনী ও ডক কর্মীদের ধর্মঘট, সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, কলকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও খিদিরপুরের ব্রেথওয়েট কারখানায় ধর্মঘট অর্থাৎ উত্তাল সারাদেশ। সুকান্ত লিখলেন ‘অনুভব ১৯৪৬’ নামক বিখ্যাত কবিতা– ’’বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,/ আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে,”। সমকাল ও সমাজকে এড়িয়ে গিয়ে আত্মরতিতে অবগাহন করতে চাননি কবি সুকান্ত। সময়ের ঝুঁটিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করেছিলেন তিনি। তাই তাঁর কবিতা এক ঝঞ্ঝামুখর সময়ের অভ্রান্ত দলিল। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের পর সাধারণ মানুষের আবেগকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন কবি সুকান্ত। সংক্ষিপ্ত রচনায় সুকান্তর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছিলেন–’’সাধারণ মানুষের প্রাণের গ্লানি সহজ মর্যাদায় প্রথম বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সুকান্তের কাব্যে। সাধারণ মানুষের জীবনকে সমবেদনায় অন্তর্দৃষ্টিতে দেখবার যে শক্তি সুকান্তের কাব্যের প্রতি ছত্রে অনুরণিত হয়ে উঠেছে সে শক্তি সুকান্ত লাইব্রেরী বিহারিণী সরস্বতীর কাছে পায় নি, সে শক্তি সুকান্ত লাভ করেছিল জীবনের পাঠশালায়–যার অধিষ্ঠান মাঠে গ্রামে, বস্তিতে, মিলে, রাজপথে।”
সুকান্ত সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবি। ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের দিক থেকে পরিণতির একটি স্পষ্ট আভাস তাঁর অল্প বয়সের কবিতাতেই ধরা পড়ছিল। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে, তাঁর কৈশোরের দিনগুলিতে ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তিনি জন্মেই দেখেছিলেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, তাই তাঁর কবিতার ভাষা কিছুটা চড়া ধাতের। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই রাজনৈতিক বক্তব্য সমন্বিত। শোষক-শোষিত সম্পর্ক তাঁর কবিতার রেকারেন্ট থিম। তাঁর কবিতা অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর, নতুন দিনের প্রত্যাশায় উজ্জ্বল ‘‘রক্তে আনো লাল,/ রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।’’ সংহত বাক্যে, সংযত ভাব কল্পনায়, দৃঢ় সংকল্প ঘোষণায় এবং ব্যঞ্জনাগর্ভ পংক্তি রচনায় তিনি ছিলেন অনবদ্য। তাঁর কবিতার পংক্তি প্রবাদে পরিণত হয়েছে, যেমন– ‘এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি’, ‘কয়েকটি পয়সায় কেনা হে কলম তুমি ক্রীতদাস’, ‘অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা’। সতর্ক পাঠকদের চোখে পড়বে যে সুকান্তের কবিতা একটি অনিবার্য পালাবদলের দিকে এগচ্ছিল। ধীরে ধীরে নতুনতর আঙ্গিকের ব্যবহার ঘটছিল তাঁর কবিতায়। সে কবিতা কিছুটা রূপক ধর্মী। লেখা হচ্ছিল ‘সিগারেট’ ‘দেশলাই কাঠি’, ‘চিল’, ‘কলম’ প্রভৃতি কবিতা। এই ধরনের রূপক ব্যবহারে তিনি অনন্য। পরবর্তী স্তরে রূপকের মধ্যে আটকে না থেকে তিনি প্রতীকধর্মিতার দিকে এগিয়ে গেছেন। সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ কয়েকটি কবিতা– ‘চারাগাছ’, ‘একটি মোরগের কাহিনী’, ‘প্রার্থী’ ইত্যাদি। পুঁজিবাদ কিভাবে ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে দেয় তার এক মর্মান্তিক কাহিনি ধরা আছে ‘একটি মোরগের কাহিনী’ কবিতায়। দরিদ্র মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদের উষ্ণ স্পর্শ ‘রানার’ কবিতাটিকে এক মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আসলে এক অশান্ত সময়ের যথার্থ বাণীকার কবি সুকান্ত। বিগত শতাব্দীর চারের দশকের সমস্ত সঙ্কট ও সমস্যাকেই তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। তাই একটি প্রতিবাদী কন্ঠস্বর সব সময়ই তাঁর কবিতায় আবর্তিত হতে দেখি। বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁকে কোথাও কোথাও উচ্চকণ্ঠ হতে হয়েছে কিন্তু যেখানে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ নেই সেখানে কি সুকান্ত ব্যর্থ? একটি দৃষ্টান্ত–”এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে/ এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,/ সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে/ পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।“এই নিভৃত রোমান্টিক কণ্ঠস্বরও তাঁর। আবার রণক্লান্ত সৈনিকের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণার অপরূপ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ‘প্রিয়তমাসু’ কবিতায়। এই ধরনেরই অনন্য দৃষ্টান্ত ‘ঐতিহাসিক’ কবিতার শেষ চার পংক্তি– ”আর মনে ক’রো আকাশে আছে ধ্রুব নক্ষত্র,/ নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,/ অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,/ আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।” কবি সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, আকাশের ধ্রুব নক্ষত্র, নদীর গতিশীলতা, অরণ্যের মর্মরধ্বনি আর পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন যাঁকে প্রেরণা দেয় তিনি ‘চিরকেলে কবিদের’ই একজন।
শতবর্ষে পা রেখে কবি সুকান্ত যেন একথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, অমরত্বের পরোয়া করা শৌখিন মজদুরি তাঁর পথ নয়। তিনি কবিতাকে গড়ে তুলেছিলেন সময়ের ভাষ্য হিসাবে। এ কাজে তিনি যে সফল শতবর্ষ পরে আলাদা করে সে কথা কাউকে স্মরণ করাতে হয় না। বাংলার শত সহস্র সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে কবি সুকান্তের ঠিকানা লেখা আছে। এখানেই তাঁর সার্থকতা। কারণ তিনি তো ‘জনতার কবি’ হতেই চেয়েছিলেন।




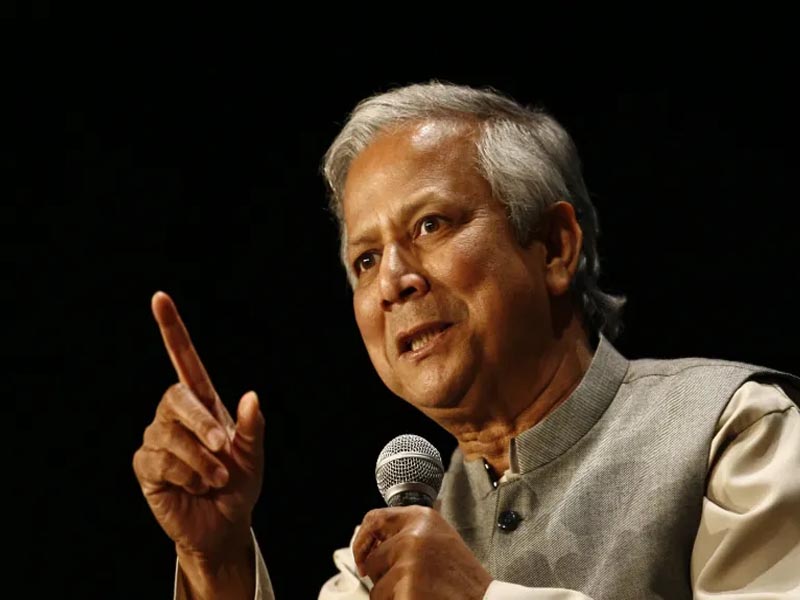



Comments :0