জিয়াদ আলী
উর্দু ভাষার উৎপত্তি এয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর অঞ্চলে। সেখানে তখন চলছে মোগল সেনাদের শাসন। তাদের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের ভাব প্রকাশের ভাষা হিসাবেই উর্দুর উৎপত্তি। সেজন্য এভাষাকে মোগল সেনাদের তাঁবুর ভাষা বা ‘মিলিটারি ক্যাম্প ল্যাঙ্গুয়েজ’ বলে অভিহিত করা হয়। এ ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে বিস্তর ফার্সি ও আরবি ভাষার শব্দ। অথচ ১৯৪৭ সালের ভারতকে ধর্মের নামে দু’ভাগ করার পর পাকিস্তান নামের নতুন রাষ্ট্রের পাঞ্জাবী শাসকরা এই ভারতীয় ভাষাকে তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তানের পূর্বভাগের বাঙালিদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালান।
ফলে পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশে, উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পূর্ব বাংলা ও শ্রীহট্ট দিয়ে তৈরি হয় যে পাকিস্তান নামের নতুন রাষ্ট্র, উর্দু তাদের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষিত হয়। আর যে গুজরাটি বংশদ্ভূত মহম্মদ আলী জিন্নাহ নামের এক লিবারাল ডেমোক্র্যাট ব্যারিস্টার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে নতুন তৈরি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে অভিষিক্ত হন, তিনি একটুও উর্দু ভাষা না জেনে পূর্ব বাংলার ঢাকা শহরে গিয়ে উর্দুকে সেখানকার বাঙালিদের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করে দেন। তারিখটা হলো একুশে মার্চ ১৯৪৮।
নতুন গভর্নর জেনারেলের এই ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ১৯৪৮ সালেই। পূর্ব বাংলার ধর্মত্ববাদী গোঁড়া মুসলমান উর্দু ও আরবি – ফার্সি ভাষার পক্ষপাতী ছিল দেশভাগের বহু আগে থেকেই । তাই এই ভাষিক দ্বন্দ্ব ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে নতুন বিদ্রোহী সত্তার জন্ম দেয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তিরিখে এই বিদ্রোহ বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিস্ফোরিত হয়। এই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও কিছু পথচারী নিহত হন। এঁরা হলেন আবদুল জব্বার, আবুল বরকত, রফিক আহমদ। এ ঘটনায় সালাম ও সফিউর রহমানও শহীদ হন। এ দিনটি তখন থেকেই শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এঁদের স্মরণে ঢাকা শহরে শহীদ মিনার নির্মিত হয়। এই শহীদ মিনার বাংলাদেশের মানুষের কাছে পবিত্র স্থান হিসাবে মর্যাদা পেয়ে এসেছে।
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়েই, ভাষার বিবর্তন নিয়ে নয়। ভাষিক অধিকার বলতে প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত অধিকারের কথাই প্রাথমিকভাবে উঠে আসে। প্রশাসন মানে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। রাষ্ট্র হলো একটা রাজনৈতিক সংস্থা। ভাষার লড়াই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক লড়াইয়ের চেহারা নেয়।
ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতেই প্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষা ও প্রশাসনিক অধিকার অর্জনের লড়াই শুরু হয়।
মানুষের শ্রেণিচরিত্র থাকে। আর্থিক অবস্থান তার মাপকাঠি। ভাষার শ্রেণিচরিত্র থাকে না। কিন্তু ভাষাকেও শ্রেণির স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। একদা বৈদিক ভাষাকে অভিজাততন্ত্রের একচেটিয়া বিষয় বলে মনে করা হতো। একই যুগের মৌলিক ভাষায় কথা বলা মানুষের মনে করা হতো ব্রাত্যজন। আবার বৈদিকজনের লৌকিক ভাষা যখন সংস্কৃত ভাষায় রূপ পেল তখন তা হয়ে ওঠে প্রাতিষ্ঠানিক। শাসকশ্রেণির ভাষা। শূদ্রদের অধিকার ছিল না সংস্কৃতের ওপর। শূদ্র সংস্কৃত উচ্চারণ করলে বা অন্যের মুখে শুনে ফেললে তার কানে শিসে ঢেলে শূদ্রকে বধির করে দেওয়া হতো। তখন ‘পালি’ ও ‘প্রাকৃত’ হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের ভাব প্রকাশের বাহন। প্রাকৃত ভাষারও বিবর্তন হলো। প্রাতিষ্ঠানিকতা ভেঙে রূপ পেল অপভ্রংশে। এই অপভ্রংশ থেকেই এল মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া ও বাংলা প্রভৃতি। এভাবেই সংস্কৃতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত প্রাকৃত ভাষার জন্ম। সেই প্রাকৃতের অপভ্রংশের পূর্বী ও মাগধী রূপ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম, প্রায় হাজারখানেক বছর আগে।
মার্কসবাদ ও ভাষা সমস্যার কথা লিখতে গিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক নেতা জোসেফ স্ট্যালিন বলেন, ‘ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ মিনস অব ইন্টার কোর্স বিটুইন ম্যান টু ম্যান ফর দি সোসাইটি।’ তাই বলা যায় ভাষা হলো জনগণের সামাজিক সম্পদ। ধনি গরিব সকলের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের পর ইহুদি ভাষার অবাধ অধিকার প্রশাসনিক মান্যতা অর্জন করে জোসেফ স্ট্যালিনের উদ্যোগে।
মনুষ্য প্রজন্মের মধ্যে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে এক এক রকমের ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতাকে আশ্রয় করে। আদিম মানুষ প্রথমে মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করত ইশারা, মুখভঙ্গি, সুরসৃষ্টি ও চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে। পাখির সুর, অরণ্যের মর্মরধ্বনি, নদী বা ঝর্নার স্রোতধারা শুনে মানুষের বাক্শক্তি বিকশিত হয়।
১৯৫২ সালের পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার আন্দোলনকে পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা প্রথম দিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চায়নি। বস্তুত, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে চিহ্নিত না করত তাহলে প্রায় অর্ধশতাব্দী পর পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে একুশের সহনীয়তা নিয়ে বাঙালির একাংশ ভাবিত হতো কিনা কে জানে? কানাডায় বসবাস করা প্রবাসী বাঙালিদের কয়েকজন রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আবেদন জানান একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালনের জন্য। ২০১২ সালে আফ্রো-আমেরিকান নাগরিক বারাক ওবামা দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। সে বছর আমার আমেরিকার নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সেটা নির্বাচনী প্রচার পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছিল। আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে তখন কিন্তু পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন নিয়ে তেমন কোনও উদ্দীপনা নজরে পড়েনি। অবশ্য ২০২২ সালে কানাডায় গিয়ে আমার খেদ মিটে গিয়েছিল টরেন্টোসহ সেখানকার একাধিক মহান একুশের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে। এবারের একুশ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।


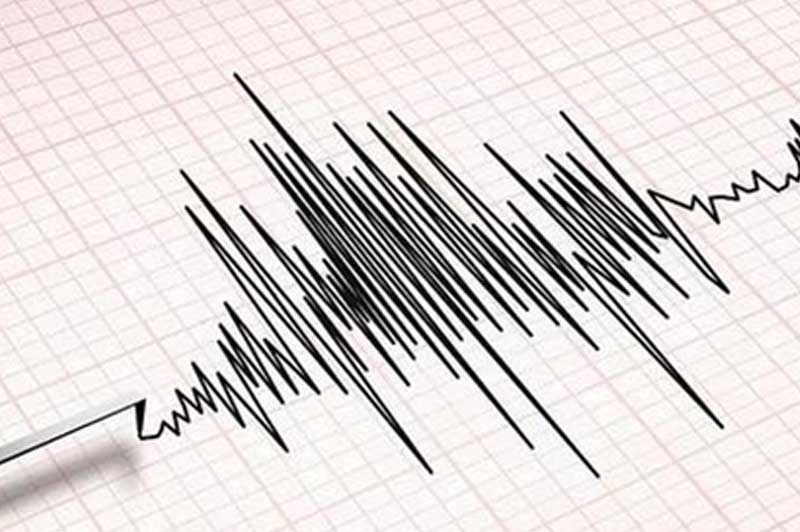





Comments :0