দেবাশিস মিথিয়া
‘কেউ যদি বেশি খাও, খাওয়ার হিসেব নাও / কেনোনা অনেক লোক ভালো করে খায় না….’—এই কথাগুলো শুনলেই ষাটের দশকে ভারতের সেই ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কটের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই সময়ে সরকারি স্লোগান ছিল ‘কম খান গম খান’। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পিএল ৪৮০ চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা থেকে ভারতকে গম আমদানি করতে হতো। খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর এই চরম নির্ভরশীলতা দেশকে বারবার সমস্যায় ফেলছিল। তাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নেন, যেভাবেই হোক দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতেই হবে। দেশের প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিখাত অবহেলিত ছিল; তার উপর খরা ও যুদ্ধের প্রভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। তাই খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকে মূল লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
ঠান্ডা যুদ্ধ থেকে সবুজ বিপ্লব
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা (ঠান্ডা যুদ্ধ) শুরু হয়, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল তারই একটি অংশ। কারণ যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা উভয় পরাশক্তির কাছেই একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্যের জোগান সুরক্ষিত করতে তখন সোভিয়েত ব্লক যৌথ চাষের দিকে যায়, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বাকিরা কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পক্ষ নেয়। এই উন্নত কৃষি উৎপাদনশীলতার মডেলটিই সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত। ১৯৪০-এর দশকে মেক্সিকোতে গম চাষের নতুন কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে এর সূত্রপাত হয়। এই প্রকল্পে অর্থের জোগান দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউন্ডেশন। আন্তর্জাতিকভাবে খাদ্য উৎপাদন ও প্রযুক্তি বিতরণের এই মডেলটি ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশ গ্রহণ করে, যার ফলে ভারতীয় কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের জন্ম হয় এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সাময়িক নিশ্চিত হয়।
ভারতে প্রথম সবুজ বিপ্লব
ভারতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। এর মূল লক্ষ্য ছিল দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি মোকাবিলা করা। এই পরিকল্পনাটি মূলত উচ্চ ফলনশীল বীজ (এইচওয়াইভি), রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনাটির সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মতো— খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে, ভারত শুধু খাদ্যের আমদানি-নির্ভরশীলতা থেকেই মুক্তি পায়নি, বরং কিছু ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য রপ্তানিও শুরু করে। এই সাফল্যের জন্য ড. এম এস স্বামীনাথনকে “সবুজ বিপ্লবের জনক” হিসেবে সম্মান জানানো হয়।
সবুজ বিপ্লবের বিতর্ক
ড. এম এস স্বামীনাথন এবং সবুজ বিপ্লবের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। একদিকে যেমন এর কঠোর সমালোচনা রয়েছে, তেমনি তৎকালীন পরিস্থিতির নিরিখে এর প্রয়োজনীয়তাও জোরালোভাবে স্বীকৃত। সমালোচকরা বলেন, সবুজ বিপ্লব ভারতীয় কৃষিকে বহিরাগত পুঁজির ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। পাশাপাশি রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অত্যধিক ব্যবহার বেড়েছে, ফসলের দেশীয় জাতগুলোকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তাঁদের মতে, স্বামীনাথন আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা পুষ্ট এই মডেলটিকে ভারতের মাটিতে সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত দেশের কৃষি ক্ষেত্রের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করেছে।
তবে, এই সমালোচনার বিপরীতে একটি ভিন্নমতও প্রচলিত আছে। ষাটের দশকে ভারত এক ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বারবার খরা— এই দু’য়ের কারণে খাদ্যের জোগানে মারাত্মকভাবে টান পড়ে। সেই সময় নিয়মিত আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছিল, যা দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছিল। এই পরিস্থিতিতে সবুজ বিপ্লব ছিল একটি অপরিহার্য সমাধান। স্বামীনাথনের নেতৃত্বে উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রয়োগে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত খাদ্যে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এই স্বনির্ভরতা কেবল দুর্ভিক্ষই ঠেকায়নি, বরং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত করেছিল। তাই, স্বামীনাথনের অবদানকে শুধু ‘সাদা’ বা ‘কালো’— এইভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। তিনি যে মডেলটি গ্রহণ করেছিলেন, তার দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব থাকলেও, সেই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় সঙ্কট থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এটি ছিল একটি অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ।
কিন্তু এই আপাত সাফল্যের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল দীর্ঘমেয়াদী সঙ্কট। সবুজ বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে শুধু একটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল এক গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, যা আমাদের দেশজ কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।
বহুজাতিক পুঁজি ও ঋণের জালে কৃষক
সবুজ বিপ্লবের কারণে কৃষকরা উচ্চ ফলনশীল বীজের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এই বীজগুলো মূলত বহুজাতিক কোম্পানির গবেষণাগারে তৈরি হয়েছিল, যার সঙ্গে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের একটি বাধ্যতামূলক প্যাকেজ যুক্ত ছিল। উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও জল সেচের অত্যাধিক ব্যয়ের কারণে প্রান্তিক কৃষকদের প্রাথমিক বিনিয়োগের খরচ বহুগুণ বেড়ে যায়। এই প্রযুক্তিনির্ভর প্যাকেজ গ্রহণ করতে গিয়ে কৃষকদের কৃষি ঋণের জালে আটকা পড়তে হয়। কোনও কারণে ফসলের দাম সামান্য কমে গেলে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে, এই ঋণের বোঝা চাষির গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়ায়। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশের মতো রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা এই অর্থনৈতিক মডেলের নির্মম পরিণতি।
সবুজ বিপ্লবের ফলে, স্থানীয়ভাবে হাজার হাজার বছর ধরে চাষ হয়ে আসা বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ধান, ডাল ও অন্যান্য ফসলের জাত ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো ‘কালোনুনিয়া’ ধান। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া অঞ্চলে একসময় এই বিশেষ জাতের সুগন্ধি ধানটি ব্যাপকভাবে চাষ করা হতো, কিন্তু সবুজ বিপ্লবের ধাক্কায় কৃষকরা উচ্চ ফলনশীল বীজের দিকে ঝুঁকলে এটি অবলুপ্তির পথে চলে যায়।
ড. আর এইচ রিচারিয়া প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন সবুজ বিপ্লব আমাদের “খাবার টেবিলে পুঁজির আক্রমণ” ডেকে এনেছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ধানের জিন-বৈচিত্র্য রক্ষা করা কেবল একটি বৈজ্ঞানিক কাজ নয়, বরং এটি ভারতীয় কৃষির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
মাটি, জল ও পরিবেশের ক্ষতি
সবুজ বিপ্লবে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাটির উর্বরতা কমে গেছে, উপকারী ‘অণুজীব ও কীটপতঙ্গ’ বিলুপ্ত হয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দূষিত হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো অঞ্চলগুলোতে, যেখানে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি, সেখানে জল-নিবিড় ফসল (যেমন ধান) চাষের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়েছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর প্রচুর পরিমাণে কমে গেছে (পাঞ্জাবের কিছু অংশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১মিটার করে নেমে যাচ্ছে) এবং কৃষকদের জন্য জলের সঙ্কট তৈরি করছে। এই জল সঙ্কট খাদ্য সুরক্ষাকে বিঘ্নিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সঙ্কটও ডেকে এনেছে।
এই পরিবেশগত বিপর্যয় ও স্বাস্থ্য সঙ্কট এর সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতিটি দেখা যায় ভারতের একসময়কার শস্যভাণ্ডার পাঞ্জাবে। সবুজ বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় এখানে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে। তার প্রভাবে পাঞ্জাবের মালওয়া অঞ্চলে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা এতটাই বেড়ে গেছে, সেখানকার রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ ট্রেন (ট্রেন নম্বর ৫৪৭০৩, আবোহার-যোধপুর প্যাসেঞ্জার) প্রতি রাতে পাঞ্জাবের ভাতিণ্ডা জংশন থেকে ছেড়ে রাজস্থানের বিকানেরে যায়, স্থানীয়রা সেটিকে ‘ক্যানসার ট্রেন’ বলে ডাকে। এটি সবুজ বিপ্লবের এক মর্মান্তিক পরিণতি।
কৃষির সার্বভৌমত্ব ও রিচারিয়ার লড়াই
ড. আর এইচ রিচারিয়া ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী কৃষি বিজ্ঞানী। তাঁর দূরদর্শিতার জন্য তিনি কেবল সরকারের রোষানল নয়, সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের অসহযোগিতারও শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দমে যাননি, একাই নিজের লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতীয় ধানের জিন-বৈচিত্র্য দেশের জাতীয় সম্পদ এবং এর সত্ত্বাধিকার হারানো মানে ভবিষ্যতে বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে পরাধীন হয়ে পড়া। আজ, মেধাসত্ত্ব আইন এবং বীজ সংক্রান্ত পেটেন্ট আইন চালু হওয়ার পর তাঁর আশঙ্কা প্রমাণিত হয়েছে। বহু দেশীয় ফসলের জাতের উপর আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো পেটেন্ট দাবি করছে।
ড. রিচারিয়ার এই লড়াইয়ের একটি বাস্তব দিক হলো, ওডিশার কটকে তিনি যখন কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন, তখন সেখানে তিনি অসংখ্য দেশীয় ধানের জাতের বিশাল এক সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। ধারণা করা হয়, এই সংগ্রহে প্রায় ১৭,০০০ ধানের জাত ছিল, যার মধ্যে অনেকগুলো খরা-সহনশীল ও রোগ-প্রতিরোধী জাতও ছিল। কিন্তু সরকারি কোপে যখন তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাঁর সেই সংগৃহীত জিন-ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অন্য হাতে চলে যায়। অনেকেই মনে করেন, তাঁর সংগ্রহের অনেক মূল্যবান জাত বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। রিচারিয়ার এই অসামান্য অবদান এবং তাঁর প্রতি সরকারের নির্লজ্জ আচরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কীভাবে ব্যক্তিগত লোভ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জাতীয় স্বার্থের ওপর প্রাধান্য পায়।
দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব: এআই ও ডেটার দখলদারি
বিশ্ব এখন তথাকথিত “দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব”-এর দোরগোড়ায়। এই নতুন বিপ্লব আগের চেয়েও বেশি করে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর হাতে কৃষি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবে। কারণ নতুন এই বিপ্লব সম্ভবত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) এবং আরও উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হতে যাচ্ছে।
এই প্রেক্ষিতে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট পুঁজির প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি নীতিগত সমর্থন ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষত, কৃষি-ব্যবসার ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করার চেষ্টা চলছে, যা দেশের কোটি কোটি প্রান্তিক কৃষককে সরাসরি কর্পোরেট প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেবে।
ইতিমধ্যেই মনস্যান্টোর মতো কোম্পানিগুলো জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বীজ (যেমন বিটি তুলো) ও তার সাথে যুক্ত কীটনাশক বিক্রি করে কৃষকদের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের বীজ ব্যবহার করলে কৃষকদেরকে নির্দিষ্ট কীটনাশকও ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে কৃষকরা বীজ এবং কীটনাশক উভয়ের জন্যই এই কর্পোরেশনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে বিটি তুলোর ব্যাপক ব্যবহার আপাত উৎপাদন বাড়ালেও, বীজের উচ্চমূল্য, বাধ্যতামূলক কীটনাশক প্যাকেজ এবং পরবর্তীকালে, কীটপতঙ্গ ওই কীটনাশকগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করায় কৃষকদের ঋণের বোঝা অনেকখানি বাড়িয়েছে, যা প্রথম সবুজ বিপ্লবের ঋণের ফাঁদকেই মনে করিয়ে দেয়।
এআই-নির্ভর ‘প্রিসিশন এগ্রিকালচার’ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ড্রোন ও সেন্সরগুলি চাষের জমি, মাটির আর্দ্রতা, সারের ব্যবহার এবং ফলন সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সংগ্রহ করবে। এই ডেটাগুলির মালিকানা থাকবে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর হাতে। ভারতে ডিজিটাল কৃষি প্ল্যাটফর্ম এবং ডেটা শেয়ারিং-এর নামে কৃষকের জমির ও ফসলের গোপন তথ্য কর্পোরেটদের হাতে চলে গেলে, এই তথ্যের ভিত্তিতেই তারা ভবিষ্যতে বীজের দাম, সারের চাহিদা এবং ফসলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ইন্ডিয়া ডিজিটাল ইকোসিস্টেম অফ এগ্রিকালচার’ (আইডিইএ)-এর মতো উদ্যোগগুলি ডিজিটাল ডেটা প্রবাহকে ত্বরান্বিত করছে, এটি পরোক্ষভাবে ডেটা কর্পোরেটাইজেশনের পথকেই প্রশস্ত করছে। এর ফলে কৃষক কেবল একটি প্রযুক্তিগত প্যাকেজের ব্যবহারকারী হিসেবেই থাকবেন না, বরং তিনি তথ্য-নির্ভর এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ‘ক্রীড়নকে’ পরিণত হবেন।
টিভি বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং এবং কর্পোরেট প্রচারের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী খাবারের পরিবর্তে প্যাকেটজাত খাদ্যকে উৎসাহিত করা হবে। যেমন, আন্তর্জাতিক খাদ্য কোম্পানিগুলো এখন ‘মিলেটকে’ প্রক্রিয়াজাত পণ্য হিসেবে সুন্দরভাবে প্যাকেট করে বাজারে আনছে এবং তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বিক্রি করছে। এটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নয়, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্যগত ঐতিহ্যকেও অদূর ভবিষ্যতে হুমকির মুখে ফেলবে।
পরিশেষে বলা যায়, সবুজ বিপ্লবের নামে যে “মিথ্যে স্বপ্ন” দেখানো হয়েছিল, তার দীর্ঘমেয়াদী মূল্য ভারতকে আজও দিতে হচ্ছে। দেশের নিজস্ব কৃষি ব্যবস্থা, পরিবেশ এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ড. রিচারিয়ার মতো দূরদর্শী বিজ্ঞানীদের আদর্শকে সম্মান জানানো এবং তাঁদের নীতি অনুসরণ করা এখন আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নচেৎ কর্পোরেট চাপে দেশের প্রান্তিক চাষিরা জমি হারাবেন, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা পুরোপুরি বিঘ্নিত হবে। বড় কর্পোরেশনগুলো কৃষিপণ্য এবং জলের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলে, দেশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়বে, যা এক নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনের জন্ম দিতে পারে।



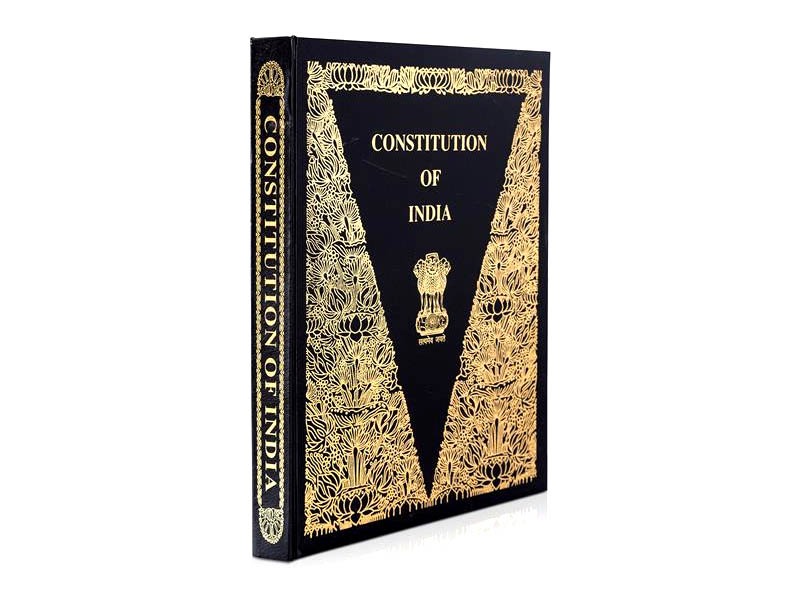




Comments :0