প্রভাত পট্টনায়ক
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে ভারতীয় কৃষকদের আরও বেশি করে রপ্তানিমুখী ফসল চাষ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর অর্থ হলো, কৃষকদের খাদ্যশস্য (যেমন ধান, গম) চাষ করা থেকে সরে আসা দরকার এবং দেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানি করা উচিত। এই পরামর্শটি বহু দিন ধরেই বিশ্বব্যাঙ্ক এবং তাদের বক্তব্যের সাথে সমমনোভাবাপন্ন ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা দিয়ে আসছেন। একই পরামর্শ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোও দিচ্ছে। এই দেশগুলি তাদের কৃষকদের বিশাল ভরতুকি (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট কৃষি উৎপাদনের মূল্যের প্রায় অর্ধেক) দেয়, যার ফলে তারা বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, যা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। তারা চায় এই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ভারতের মতো দেশে বিক্রি হোক। তাই তারা চায় ভারতের মতো দেশগুলি যেন খাদ্যশস্য উৎপাদন বাদ দিয়ে তাদের (সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির) প্রয়োজনীয় রপ্তানিযোগ্য ফসল উৎপাদন করে। ফলে, মোদীর কৃষকদের প্রতি এই পরামর্শ সাম্রাজ্যবাদের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
খাদ্যশস্যের জমি থেকে কৃষিকে সরিয়ে ফেলার এই প্রয়াসটিই মোদী সরকারের বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইনের মাধ্যমে কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আগে থেকে চলে আসা ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (Minimum-Supply-Prices অথবা এমএসপি)-এর যে সরকারি ব্যবস্থা ছিল, তা বাণিজ্যিক বা অর্থকরী ফসলের (cash crops) ক্ষেত্রে তুলে নেওয়া হলেও খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে বহাল ছিল। এই নতুন আইনগুলির মাধ্যমে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্র থেকেও সেই ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। যদি এমনটা হতো, তাহলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের আকর্ষণ কমে যেত এবং কৃষকরা সেই জমি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। কৃষকরা এই আইনগুলির বিরুদ্ধে সফলভাবে এক বছরব্যাপী আন্দোলন করেন, যার ফলস্বরূপ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যবস্থা আবার চালু হয়। এটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং মোদী সরকার, উভয়েরই বিরক্তির কারণ হয়। তবে সাম্রাজ্যবাদীরা বা সরকার কেউই তাদের লক্ষ্য ত্যাগ করেনি; কৃষকদের রপ্তানিযোগ্য ফসল ফলানোর জন্য মোদীর সাম্প্রতিক উপদেশ তারই প্রমাণ।
কৃষক আন্দোলনের সময় সরকারি অর্থনীতিবিদরা এবং বিশ্বব্যাঙ্কের নীতি অনুসরণকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন, খাদ্যশস্যের জমি থেকে অর্থকরী ফসলের (cash crops) দিকে সরে আসা কৃষকদের নিজেদের স্বার্থেই ভালো। তাঁদের মতে, খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এমএসপি) ব্যবস্থা চালু ছিল, সেটাই এই পরিবর্তনকে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু কৃষকরা বাস্তব পরিস্থিতিটি আরও ভালো বুঝেছিলেন। অর্থকরী ফসলের উপর থেকে এমএসপি ব্যবস্থা তুলে নেওয়ার ফলে কৃষকরা বিশ্ববাজারের ব্যাপক মূল্য ওঠানামার (wild fluctuations) শিকার হচ্ছিলেন। এই ধরনের ফসলের ক্ষেত্রে দামের অস্থিরতা খুব বেশি দেখা যায়। এই কারণেই অর্থকরী ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের বিপদ বা ঝুঁকি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই ঝুঁকি আরও বাড়ে কারণ অর্থকরী ফসল চাষের জন্য বেশি ঋণের প্রয়োজন হয়। ফলস্বরূপ, যখনই বাজারে দামের পতন ঘটেছে, কৃষকরা সেই ফসল চাষের জন্য নেওয়া ঋণ শোধ করতে পারেননি। এর ফলে বহু কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। গত তিন দশকে চার লাখের বেশি কৃষক, যাদের বেশিরভাগই (তবে শুধু তারাই নন) অর্থকরী ফসল চাষ করতেন, আত্মহত্যা করেছেন। যখন সরকার খাদ্যশস্যের উপর থেকেও এমএসপি ব্যবস্থা তুলে নিতে চাইল, তখন কৃষকরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কারণ এটি ছিল তাদের শেষ সুরক্ষার দেওয়াল। তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষী প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বব্যাঙ্কের নীতি অনুসরণকারী অর্থনীতিবিদদের চেয়ে কৃষকরা অনেক বেশি ভালোভাবে জানতেন যে, এমএসপি ব্যবস্থা পুরোপুরি উঠে গেলে তাদের জন্য কী ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।
তবে খাদ্যশস্য থেকে নগদ ফসলে জমি স্থানান্তরের আরেকটি অতিরিক্ত বিপদ রয়েছে, যা দাম কমে যাওয়ার সময় ফসল ফলানোর জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে না পারার সমস্যা ছাড়াও আরও বড়। সেটা হলো দেশ এবং কৃষক জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষতি, যা দুর্ভিক্ষের আকারে প্রকাশ পেতে পারে এবং পেয়েছেও। বিশ্বায়নের শাসনকালে খাদ্য থেকে নগদ ফসলে জমি স্থানান্তরের কারণে অনেক আফ্রিকান দেশে এমন দুর্ভিক্ষ ঘটেছে। অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচী তাঁর 'দ্য পেরিলাস প্যাসেজ' (The Perilous Passage) বইয়ে এই ধরনের দুর্ভিক্ষকে খুব উপযুক্তভাবেই ‘বিশ্বায়ন দুর্ভিক্ষ’ (Globalisation Famines) বলে অভিহিত করেছেন।
যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, কোনোভাবে দেশটি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো — যেমন কোনও কঠিন বছরে দাতা দেশগুলোর ‘খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির’ (food aid) থেকে পাওয়ার মাধ্যমে, তবুও আরেকটি গুরুতর সমস্যা থেকে যায়। যে কৃষকরা অর্থকরী ফসল ফলান এবং সেই ফসলের দাম বাজারে পড়ে গেলে, তাদের কাছে সেই খাদ্য সহায়তা এলেও বাজার থেকে খাদ্যশস্য কেনার মতো ক্রয় ক্ষমতা আর থাকবে না। সুতরাং, শুধু ‘খাদ্য সহায়তার’ ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়, এর সাথে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে খাদ্যে ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার যদি এই ভরতুকি না দেয় (বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণ না করে), তবে সেক্ষেত্রেও মন্বন্তরের সম্ভাবনা এড়ানো যাবে না।
খাদ্যশস্য থেকে যদি এমন কোনও অর্থকরী ফসলের দিকে জমি সরানো হয় যা কম কর্মসংস্থানমুখী (less employment-intensive), অর্থাৎ প্রতি একর জমিতে আগের চেয়ে কম সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়, তাহলেও মন্বন্তর বা অন্ততপক্ষে অপুষ্টি বৃদ্ধি হওয়ার সমান ঝুঁকি তৈরি হয়। কারণ এই অবস্থায় যারা বেকার হয়ে যাবেন, তাদের কাছে বাজারে খাদ্যশস্য কেনার মতো ক্রয় ক্ষমতা থাকবে না। যদিও দেশের কাছে হয়তো খাদ্যশস্য আমদানি করার মতো যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আছে, তবুও এই বেকার মানুষগুলোর ক্রয় ক্ষমতার অভাবে তারা খাদ্য কিনতে পারবে না। আগের কারণটির থেকে ভিন্ন কারণে হলেও, এই পরিস্থিতিতেও একটি মন্বন্তরের মতো অবস্থা সৃষ্টি হবে। অমর্ত্য সেনের দেওয়া একটি পার্থক্য ব্যবহার করে বলা যায় - এই পরিস্থিতিকে বলা হবে ‘বিনিময় স্বত্বের ব্যর্থতা’ (Failure of Exchange Entitlement বা FEE)। কারণ বেকার মানুষগুলোর কাছে খাদ্য কেনার সামর্থ্য বা ‘স্বত্ব’ (entitlement) থাকবে না। আর আগের ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা ছিল ‘খাদ্যের জোগান হ্রাস’ (Food Availability Decline বা FAD)। এখানে মনে রাখতে হবে, কম কর্মসংস্থানমুখী অর্থকরী ফসলের দিকে সরলে (যেমন ফলের বাগান বা orchard crops), FEE ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদন কমালে FAD নিশ্চিতভাবে ঘটবে।
এর থেকে বোঝা যায় যে, নয়া-উদারবাদী (neo-liberal) শাসন ব্যবস্থার অধীনে খাদ্যশস্যের জমি অর্থকরী ফসলের দিকে সরিয়ে এনে দেশীয় খাদ্য নিরাপত্তা দুর্বল করে দেওয়া হলে, তা দুর্ভিক্ষের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিশ্বজুড়ে দক্ষিণের অনেক অঞ্চলে, বিশেষত আফ্রিকায়, ঠিক এটাই ঘটেছে। ভারত এত দিন পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরে না আসায় এই সম্ভাবনা এড়িয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু এখন যদি ভারতের কৃষকরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ শোনেন, যিনি নিজেই সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন, তবে ভারতও এই বিপদের মুখে নিজেকে ঠেলে দেবে।
‘বিশ্বায়িত মন্বন্তর’ (globalisation famines)-এর ঝুঁকি ছাড়াও, খাদ্যশস্য আমদানির ওপর নির্ভর করা একেবারেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এর আরও একটি বড় কারণ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে এমন দেশগুলোর বিরুদ্ধে একতরফা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (unilateral economic sanctions) আরোপ করে এসেছে, যারা তাদের আদেশ মেনে চলে না। কিউবা, ইরান, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং ভেনিজুয়েলার মতো বহু দেশ বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞার শিকার। এই নিষেধাজ্ঞার পরিধি বিভিন্ন হতে পারে, তবে এর মূল রূপটি হলো— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে সেই দেশের সাথে কোনও বাণিজ্য করে না এবং একই সাথে অন্য দেশগুলোকেও সেই দেশের সাথে বাণিজ্য করতে বাধা দেয়। যদি কোনও দেশ খাদ্যশস্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কর্তৃক তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে সেই দেশে বড় মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। আর যদি নিষেধাজ্ঞা আরও কঠিন রূপ নেয়, যেমন— নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশের বিদেশে গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ (foreign exchange assets) বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহলে তাদের খাদ্যশস্য কেনার ক্ষমতা আরও কমে যায় এবং মানবিক বিপর্যয় আরও গুরুতর হয়। আজকের দিনে, যখন সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া গাজায় গণহত্যাকে ক্ষমতাসীন চক্র-এর (ruling circles) পক্ষ থেকে নীরব সমর্থন জানানো হচ্ছে, তখন কোনও দেশ যদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তবে এই ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা খুবই বাস্তব।
ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন সরাসরি বাণিজ্যকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন, তখন কোনও দেশের খাদ্য আমদানি-নির্ভরশীল হয়ে পড়া হলো নীতি প্রণয়নে তার স্বায়ত্তশাসন হারানোর সবচেয়ে নিশ্চিত পথ। আজকের দিনে, খাদ্য আমদানির ওপর নির্ভরতা এমন একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে একটি দেশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র (client state) বা অনুগত রাজ্যের স্তরে নেমে আসে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কৃষকদের রপ্তানিমুখী ফসল ফলানোর পরামর্শ দেওয়া, যার অর্থ খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরে এসে মহানগরের (metropolis) চাহিদামতো অর্থকরী ফসল চাষ করা— তা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার অভাব এবং ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে তাঁর নতি স্বীকারের প্রবণতাকেই প্রকাশ করে, যা সত্যিই বিস্ময়কর।



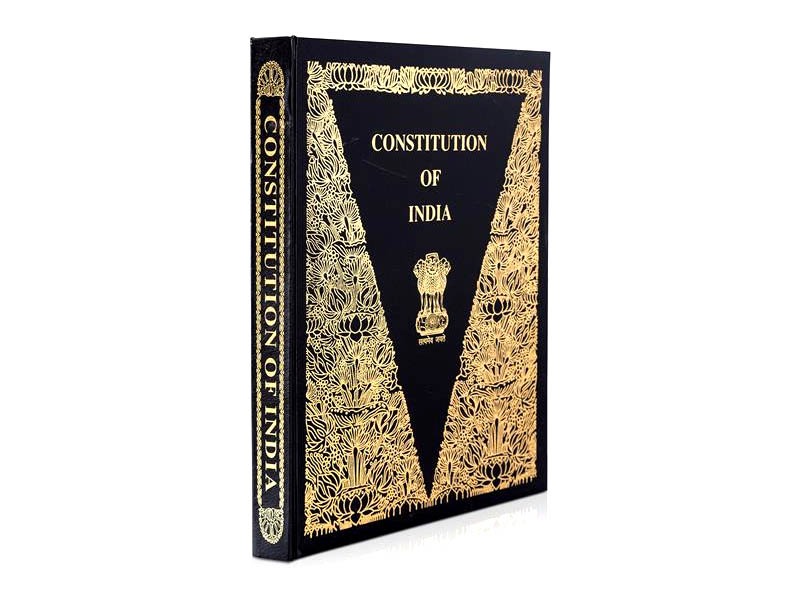




Comments :0