অশোক ভট্টাচার্য
ইদানীং শিলিগুড়ি শহর থেকে যতই বাইরের দিকে যাওয়া যায় চোখে পড়ে অনেক পরিবর্তন। আগে দেখতাম রাস্তার ধারে ছোট ছোট বাজার, দোকান, বহু গাছ। দেখা যেত ছোট ছোট বাড়ি আর সবুজ প্রান্তর, দেখা যেত পাহাড় থেকে নেমে আসা খরস্রোতা নদী। আগে রাস্তা পারাপার করতে দেখা যেত এক পাল হাতিকেও। এখন যেতে যেতে বুঝতেই পারি না কখন শিব মন্দির, আঠারো থাই, কদমতলা, অটল বা হাতি ঘিষা চলে গেল।
সেদিন যাচ্ছিলাম বাগডোগরা। মাটিগাড়াও যেন হারিয়ে গেছে। আর একটি বালাসন সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। আবার মাটিগাড়া থেকে দাজিলিঙ মোড়, চম্পাসারি মোড়, ভক্তিনর থানা মোড় হয়ে সেভক রোডের উপর নির্মিত হচ্ছে দীর্ঘ উড়ালপুল। শোনা যাচ্ছে সেভক সেতুর পাশে তিস্তা নদীর উপর বিকল্প সেতু অনুমোদিত হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে নির্মিত হওয়ার ফলে শহর থেকে মিনিট পনেরোর মধ্যে এখন পৌঁছে যাওয়া যায় ফুলবাড়ি বা বাংলাদেশ সীমান্ত।
এই যে বিরাট উন্নয়ন হচ্ছে তাতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিলিগুড়ি শহরে পৌঁচ্ছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যেই। শহরের মধ্যে বহু গরিব মানুষ যারা বহু কাল ধরে বসবাস করে আসছিল, তারা শহর থেকে বাইরে আরও প্রান্তিক অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। আর এই সমস্ত অঞ্চলে গড়ে উঠছে অজস্র উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট, আবাসন প্রকল্প উপনগরী, বড় বড় মল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি।
এই সমস্ত উন্নয়নের মূল সুবিধা কারা পাচ্ছে? আগে গ্রামগুলিতে যখন যেতাম তখন যাদের সাথে দেখা হতো, আজ গ্রামে গেলে তাদের দেখা পাওয়া যায় না। আগে এই সমস্ত গ্রামগুলিতে গ্রামের মানুষের রোজগারের উৎস ছিল কৃষি। আজ এই সমস্ত গ্রামগুলিতে কৃষির চাইতে অকৃষিতে জমি ব্যবহৃত হচ্ছে বেশি। অনেক গ্রাম পরিণত হচ্ছে আধা শহরে। গ্রামেরও শ্রেণি চরিত্রের পরিবর্তন হচ্ছে। এই সমস্ত গ্রামে আগে যারা বসবাস করত, তারা ছিল মূলত রাজ বংশী, আদিবাসী, নেপাল থেকে আগত নেপালী বা গোর্খা ভাষী কৃষক। দেশ ভাগের পর বিশেষ করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পর এই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেছিল কয়েক লক্ষ বাঙালি উদ্বাস্তু। এদের বেশিরভাগই ছিল নমঃশুদ্র বা তফসিলি জাতি বা নিম্ন বর্ণের হিন্দু, যারা যুক্ত ছিলেন কৃষির সাথে। ছোট নাগপুর বা সাঁওতাল পরগনা থেকে আগত অনেক আদিবাসীরা আজও যুক্ত চা বাগানের শ্রমিকের কাজে। এদের পরিবারের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাঁরা চলে আসছেন শিলিগুড়ি শহরে নতুন কাজের খোঁজে। আজ হাজার হাজার একর কৃষি জমি ছোট চা বাগানে পরিণত হচ্ছে। অথচ এক সময়ে এই সমস্ত কৃষি জমি ছিল রাজবংশী বা আদিবাসি কৃষকদের হাতে।
আজ এই সমস্ত এলাকাগুলিতে অনেক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে তাঁদের রোজগারের উৎসও। যত এই সমস্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে ততই এই সমস্ত অঞ্চলের আদিবাসীরা বা গরিব মানুষরা উন্নয়ন পরিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাঁরা দীর্ঘকালের জীবিকা হারাচ্ছেন, ফলে আর্থিক স্বাধীনতাও সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে। তাঁদের উপর রাষ্ট্র ও পুঁজির আধিপত্য বা কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আত্মসাৎ করা হচ্ছে তাঁদের স্থানকে বা জায়গাকে। এই সমস্ত গরিব জনগোষ্ঠীগুলির অসহায়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সময়ে এই সমস্ত গ্রামগুলিতে চাষবাস বা বসবাস করতো মূলত রাজবংশী মানুষেরা। শুধু গ্রাম নয়, শিলিগুড়ি পৌরএলাকায় সদ্য সংযোজিত অঞ্চলেও বসবাস করতেন রাজবংশী মানুষেরা। আজ এই রাজবংশী জমির মালিকদের এই সমস্ত অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া কঠিন। যারা এক সময়ে ছিলেন জমির মালিক, আজ অনেককেই নিজেদের জমি হারাতে হয়েছে। জোতদার বা ধনী চাষিদের অনেকেও পরিণত হয়েছে ভাগ চাষিতে নিজেদেরই জমিতে। অনেক মানুষ পরিণত হচ্ছেন ক্ষুদ্র ও অসংগঠিত চা বাগানে দিন হাজিরার শ্রমিকে। বহু রাজবংশী কৃষকরা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছেন, বা কেউ কেউ রিকশা চালক হয়েছেন, বহু মানুষের রোজগার হচ্ছে নদী থেকে পাথর বালি তুলে।
নব্য উদারীকরণ আর্থিক নীতির পরিণতিতে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। সমাজ বিজ্ঞান পরিভাষায় একে বলা হয়ে থাকে গেন্ট্রিফিকেশন (Gentrification)। এর বাংলা অর্থ একটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। দীর্ঘকাল ধরে এই অবস্থা দেখা যেত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নগরায়নের ক্ষেত্রে। ১৯৬৪ সালে রথ গ্লাস নামে একজন নগর বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, “একের পর এক লন্ডনের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি দখল নিচ্ছে উচ্চবিত্তরা। ছোট ছোট সাধারণ বাড়িগুলি ... হারিয়ে যাচ্ছে নিজের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে। পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে চমৎকার ব্যয়বহুল বাংলো, অ্যাপার্টমেন্ট। কোনও একটি অঞ্চলে এ ধরনের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন অনুরুপ অঞ্চলগুলিও দ্রুত আক্রান্ত হয়। অচিরেই বিশাল একটি এলাকার শ্রেণি চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে।”
এই পরিবর্তনকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই তথাকথিত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে নতুন করে একদল মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। অর্থনীতির পরিভাষাতে এদের বলা হয়ে থাকে উন্নয়ন উদ্বাস্তু বা ডেভেলপমেন্ট রিফিউজি। যে সংখ্যা ভারতে দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তুদের সংখ্যার থেকেও বেশি। উদারীকরণ আর্থিক নীতির যুগে পুঁজি পরিণত হয়ে থাকে লগ্নিপুঁজিতে। যেখানেই বেশি লাভের সম্ভাবনা থাকে, পুঁজির প্রবণতা সেখানেই বিনিয়োগ করার। ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি উৎপাদনের চারটি উপাদানের কথা - জমি, শ্রম, পুঁজি ও উদ্যোক্তা। বর্তমান সময়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জমিরই রয়েছে সবচাইতে বড় ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলে বসবাসের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। আজ শহরাঞ্চলে জমি ক্রমহ্রাসমান। আবার অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে জমির সরবরাহ বেশি। পরিষেবা বা উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পের জন্য দরকার শহর সংলগ্ন জমি। যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত সেই সমস্ত গ্রামেই জমির লভ্যতা বেশি, সেখানেই পুঁজির হাত প্রসারিত হচ্ছে এই সমস্ত জমির দিকে। এই সমস্ত জমির বাজার দর শহরের চাইতে কম। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে বর্তমানে কর্পোরেট পুঁজির বিনিয়োগের প্রবণতা শহর থেকে গ্রামেই বেশি।
উন্নয়নের সাথে উচ্ছেদের সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছি। এর ফলে মানুষের শুধু জীবিকা হারানোই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মানুষের সামাজিক সম্পর্কও বিনষ্ট হচ্ছে। যে কোনও স্থানের জমির প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, জীবনযাপনের ধরনের ভিন্নভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একেই বলে স্থান তন্ত্র ও স্থানিক বৈশিষ্ট্য। এর সাথে যুক্ত জমির উপর পুঁজির বেপরোয়া কর্তৃত্ব স্থাপন এবং অনুন্নত স্থানে শ্রমজীবী এবং দরিদ্রদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারানো। একেই বলে স্থানিকতার বিনাশ, বিশেষ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্যরও বিনাশ। এই সমস্ত এলাকাতে যে নতুন নতুন পরিষেবাগত উন্নয়ন হচ্ছে, তাতে এই সমস্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনের সাথে তা সম্পৃক্ত নয়। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ এই সমস্ত উন্নয়নকে বলে থাকেন সৃষ্টিশীল ধ্বংস। যদিও এই উন্নয়ন মানে দূরত্বের বিলুপ্তি, উন্নয়নের এই নীতি এই সমস্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের বা আদি অধিবাসীদের অতীত ইতিহাসও ভুলিয়ে দেয়। যা বিভিন্ন শহরের কলোনি বা বস্তি অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে।
একই সাথে দেখা যাচ্ছে উৎপাদনকে ভাগ করে দেওয়া। সংগঠিত থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি স্থানের ওপরে রাষ্ট্রের আধিপত্য। আজকে সেখানে পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুঁজি সবসময় চায় উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধি করে বেশি মুনাফা অর্জন করতে। আজ তারা দুই ভাবে এই মুনাফা বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করেছে। কম শ্রমিক দিয়ে বা অস্থায়ী বা অসংগঠিত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে, সেই মজুরির মূল্য থেকে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা। অন্যদিকে এর মধ্যে দিয়ে উৎপাদনকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ে পুঁজিপতিরা সবচাইতে বেশি পুঁজির সঞ্চয়ন করে উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে (Accumulation By Dispossession )।
এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শাসক শ্রেণি বিভিন্ন অঞ্চলে শুধু মুনাফা অর্জনই করে না, একই সাথে কোনও একটি অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বা মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এইভাবেই এরা সৃষ্টি করে মৌলবাদী ও বিভাজনের রাজনীতি, এর মাধ্যমে পুঁজি মানুষের প্রতিবাদও স্তব্ধ করে দিতে চায়। আর একদিকে যেমন বাড়ছে স্থানকে আত্মসাৎ করার প্রবণতা, অন্যদিকে পুঁজি তার সঞ্চয়ের পদ্ধতিরও একের পর এক পরিবর্তন করে চলেছে। যে জায়গাতে উৎপাদনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন জমির উর্বরতা, চা বাগান, আর্থ-সামাজিক উন্নতির মান, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এগুলোকেও তারা বিনাশ করে দেয়।
আমি আগেই ইতিহাস গত বিনাশের কথা উল্লেখ করেছি। পুঁজি গ্রাম, শহর, পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্রতীর সর্বত্র একমাত্রিক অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে থাকে। এতদিন পর্যন্ত জমির ব্যবহারের (Land Use) যে নীতি মেনে চলা হত, তাকে আজ গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, ১৯৯০ সালের পর থেকে উৎপাদন ভিত্তিক কারখানার বাইরে অসংগঠিত শ্রমিকদের ব্যবহার করা হচ্ছে, সংগঠিত শ্রমিকদের চাইতে অনেক গুণ বেশি। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে, ১৯৯০ সালে মহারাষ্ট্রে দৈনিক স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষের বেশি। ২০০৪ সালে তা কমে হয় ৭ লক্ষ। এভাবে তারা অর্জন করছে অতিরিক্ত মুনাফা। এই অতিরিক্ত মুনাফার কারণটা কী? এক, সংগঠিত শ্রমিক থেকেও অসংগঠিত শ্রমিকদের বেশি নিযুক্ত করে তাদের বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। দুই, শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ বৃদ্ধি করা। উত্তরবঙ্গে চা বাগানগুলিতে স্থায়ী শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ী বা বিঘা শ্রমিকদের দিয়ে বেশি কাজ করানো হচ্ছে। তাদের বিভিন্ন ফ্রিঞ্জ (Fringe) বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে না, এর ফলেও মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফা ও উদ্বৃত্ত মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চা বাগানের জমিও অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার অন্য কাজে বাগানের জমি ব্যবহার করার অনুমতিকে ১৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% করতে চলেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এই নীতির কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে চা বাগানের জমি আরও বেশি ভাবে যাবে কর্পোরেটদের হাতে।
বিগত চার দশক ধরে বাংলায় ও দেশে বেশ কিছু মানুষ কোনও সম্পদ সৃষ্টি না করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে যাচ্ছে। আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে যাচ্ছে। উচ্ছেদ হচ্ছে বাসস্থান আর কর্মসংস্থান থেকে। কিছু মানুষের সে দেশের জীবন যাপনের জলুস বাড়ছে। আর বিরাট অংশের মানুষ বঞ্চনা, বৈষম্য, দুর্দশা, অসমতা আর অসহায়তার শিকার হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে দুর্নীতি ও দুষ্কৃতীর রাজনীতি। এর পেছনেও আছে এক অর্থনীতি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও উন্নয়নও যাচ্ছে বাংলাদেশের পথে। মানুষ চায় বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন, যেখানে উন্নয়নে মানুষের পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে। যেখানে অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা থাকবে। উন্নয়নে থাকবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। আজ উন্নয়নে থাকছে না সামাজিক ও স্থানিক ন্যায়ের ভূমিকা। এই উন্নয়ন কখনও ভারসাম্যমূলক বা বহমান উন্নয়ন হতে পারে না।
জমির সরবরাহ বৃদ্ধি করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই গঠন করেছে ‘ন্যাশনাল ল্যান্ড মনিটাজাইশন কর্পোরেশন’ (NLMC)। এর প্রধান উদ্দেশ্য সরকারি বা বেসরকারি জলাভূমি বা উর্বর জমি বা চা বাগানের জমির নগদিকরণ করা৷ ৩০ শতাংশ চা বাগানের জমিকে অ-চা বাগানে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে দেবার যে নীতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের ল্যান্ড মনিটাইজেশন নীতি। তার প্রভাব পড়বে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপরও । অন্যদিকে স্থায়ী শ্রমিকদের উপর কাজের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হচ্ছে। আজও তাদের ন্যূনতম মজুরি নীতি কার্যকরী হচ্ছে না। বহু চা বাগানের জমির উপর রাষ্ট্রের সহযোগিতায় পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। চা বাগানের জমিতে গড়ে উঠছে উপনগরী, হোটেল, বাণিজ্য কেন্দ্র, বেসরকারি হাসপাতাল ইত্যাদি। অথচ এই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিকরা কোনোভাবেই উপকৃত হচ্ছে না। এই সমস্ত সৃষ্টিশীল ধ্বংসাত্মক উন্নতি থেকে লাভবান হচ্ছে হাতেগোনা কিছু কর্পোরেট ক্ষেত্র। চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাপনের সাথে এই নতুন ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বহু চা বাগানের শ্রমিকরাও পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে জনবিন্যাসগত সামাজিক পরিস্থিতির। যতই গ্রাম বা চা বাগানগুলির শহরের সাথে অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই পুঁজির নজরে পড়েছে এই সমস্ত জমিগুলির দিকে। এভাবেই উত্তরবঙ্গে জমির নগদিকরণ বা মনিটাইজেশনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।


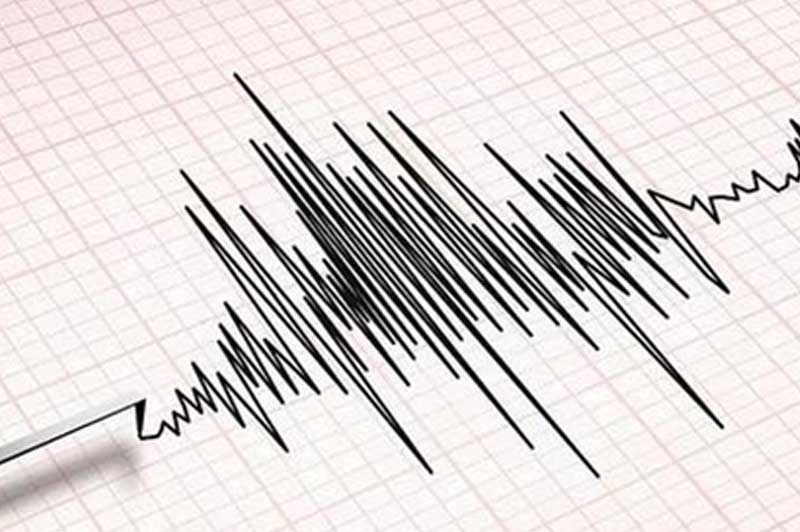





Comments :0