সিলেটের বাংলাও বাংলা, পুরুলিয়ার বাংলাও বাংলা, চট্টগ্রামের বাংলাও বাংলা। বৈধ বাংলা। যদি না, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও কারণে, ব্যবহারকারীরা তাকে অন্য ভাষা বলে দাবি করে। সেটার ভিত্তি অন্য। বাংলা ভাষা নিয়ে অহেতুক বিতর্কের জবাবে জানালেন ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার।
-------------------------
প্রশ্ন: বিজেপি’র আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলছেন বাংলা নাকি কোনও ভাষাই নয়! কোনটা ভাষা আর কোনটা ভাষা নয়? মুখের কথাকে ভাষা হিসাবে বিবেচনা করার কী কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি হয়? যদি তাই হয় তবে সে মাপকাঠি কিভাবে নির্ধারিত হবে?
পবিত্র সরকার: মাপকাঠি হলো মানুষ। অর্থাৎ তাঁরাই যাদের ভাষার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাঁরা যেখানেই থাক, যেরকম কথাই বলুন যদি তাঁরা বলেন যে আমরা বাংলাই বলছি, আমরাও বাঙালি তবে সেটাই তাঁদের বাংলা, তাঁরাও বাঙালি। একটা ভাষার অনেক রকম চেহারা রয়েছে। প্রথমটি স্থানিক বৈশিষ্ট, যাকে রিজিওনাল ডায়ালেক্ট বলে। অনেকদিন ধরেই আমরা জানি যে স্থান অনুসারে ভাষা বদলায়। ম্যাকামুলার বলেছিলেন ১৫ মাইল অন্তর ভাষা বদলে যায়। এই বদল থেমে থাকে না, চলতে থাকে, এখনও চলছে। পাঠ্যবইয়ে এত হিসাব রাখা হয় না। তারা বলে একটি ভাষা বড়জোর চার বা পাঁচটি রূপ থাকে, এমন মতামত কিন্তু খানিকটা সাধারণীকরণ। আসলে যা মনে রাখতে হয় তা হলো অনেকগুলি লক্ষ্মণ মিলে তবে উপভাষার প্রেক্ষিত নির্মিত হয়। একটি জেলাতেও চার পাঁচটি উপভাষা হতে পারে। যেমন একাধিক জায়গার কাছাকাছি অঞ্চলে যারা বসবাস করেন তাদের একে অন্যের ভাষায় মিলের জায়গা অনেক। কিন্তু একেক নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোক নিজেদের একেক ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ বলে দাবি করবেন। এভাবেই একাধিক ভাষা বৈশিষ্ট্য একে অন্যের সঙ্গে মিলে এক একটি উপভাষার জন্ম হয়।
দ্বিতীয়ত যে প্রভাবটি কাজ করে সেটি হলো সামাজিক শ্রেণি বিভাজন। যারা লেখাপড়া বেশি জানে, টাকা পয়সা বেশি রয়েছে তাদের একরকম ভাষা হয়, বাকিদের অন্যরকম। লিঙ্গভেদে ভাষার বদল ঘটে। কখনও সম্প্রদায় অনুযায়ীও ভাষার বদল লক্ষ্য করা যায়।
তৃতীয় প্রভাবটি সরাসরি জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শ্রমিক, কৃষক মজদুর এদের ভাষার সঙ্গে অন্যদের ভাষার তফাৎ হয়। এমনকি খেলোয়াড়দের ভাষাও অন্য হয়, একটু খেয়াল করলেই তাদের অন্যদের ভাষার থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাবে।
এগুলি সবই হচ্ছে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ভাষার বৈচিত্র, আমরা একে সোশিওলেক্ট বলি। এদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি সিলেটের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কি বাংলা বলছেন? তিনি উত্তর দেবেন হ্যাঁ আমি তো বাঙালি, আমি সিলেটি ভাষা বলছি। কারণ তারা যা মনে করে সেটাই তাদের পরিচয়, তাদের আইডেন্টিটি।
প্রশ্ন: আপনি বলছেন ভাষাকে আঁকড়ে ধরে পরিচিতি বা আইডেন্টিটি গড়ে ওঠে?
পবিত্র সরকার: একটি উদাহরণ দিই, তাহলেই স্পষ্ট হবে। খড়গপুর ধরে দীঘার দিকে এগলে, কাঁথির দিকে গেলে কী দেখা যায়? সড়কের একদিকে পশ্চিমবঙ্গ, আরেকদিকে ওডিশা। এদিকের লোকে বলবে আমরা বাংলা বলছি, ওদিকের লোকজন বলেন আমরা ওড়িয়া বলছি। একই ঘটনা দেখা যাবে নরওয়ে আর সুইডেনের ক্ষেত্রে। দু’ধারের একদিকে বলা হবে আমরা নরওয়েজিয়ান বলছি, ওদিকে বলবে আমরা তো সুইডিশ বলছি। এভাবেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সীমানা ভাষার বাঁধন ঢিলে করে দেয়, আবার কখনও করে না। দ্বিতীয়টা দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বেলায়। বাংলাদেশের মানুষ অন্তত এখনও অবধি বলেননি যে আমরা বাংলা বলছি না। মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষার জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। ফলে চট্টগ্রামের লোক যেমন বলবেন যে তারা বাংলায় কথা বলছেন, আবার কুমিল্লার লোকও একইরকম দাবি জানাবেন। তাই আমি বললাম যে মানুষের ওপরেই নির্ভর করবে সামাজিক দিক থেকে তার ভাষাগত কিংবা ভাষা নির্ভর গোষ্ঠীগত পরিচয়টি আসলে কেমন। কমিউনিটি হিসাবে আমরা যে যেভাবে নিজেকে স্পষ্ট করি সেটাই আমার পরিচয়। বাংলা, হিন্দি কিংবা ইংরেজি ভাষার কোনোটাই কিন্তু কোনও এককেন্দ্রিক বা মনোলিথিক ভাষা নয়।
প্রশ্ন: তাহলে প্রমিত ভাষা বলতে কী বুঝব?
পবিত্র সরকার: অসংখ্য ডায়ালেক্ট মিলে এক একটি ভাষা গড়ে ওঠে। সবার মধ্যে থেকে কোনও একটি ডায়ালেক্ট হয়ে ওঠে প্রধান। সেটাই প্রমিত ভাষা বা সুপার ডায়ালেক্ট হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই নির্ধারণের পিছনে কাজ করে সামাজিক প্রতিপত্তি, ক্ষমতার কেন্দ্র ইত্যাদি বিষয়। প্রমিত বলতে আমরা আসলে যা বুঝি তাকে স্ট্যান্ডার্ড বলা চলে। স্ট্যান্ডার্ড ভাষার নিজস্ব ক্ষমতা, ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি সবই অন্যান্য উপভাষার চাইতে বেশি হয়। স্থানভেদে দু’এলাকার মানুষ যখন একে অন্যের সঙ্গে কথা বলেন তখন দুয়ের মাঝে ভাব বিনিময়ের স্বাভাবিক মাধ্যম হয়ে ওঠে ঐ প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা। এই জন্যই অনেকে প্রমিত ভাষাকে মান্য ভাষা বলে ভেবে নেন। এমনকি একজন বিদেশি মানুষও যখন নতুন কোনও ভাষা শিখতে বসেন তিনিও ঐ প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষাকেই শেখেন।
এভাবে এর সম্মান এত বেড়ে যায় যে, এটাই পুরো ভাষাটার পরিচয় দখল করে নেয়, অন্য বৈচিত্রগুলোকে আড়াল করে। সেগুলোও কিন্তু ভাষা, বাংলার হলে বাংলা ভাষারই অংশ। সিলেটের বাংলাও বাংলা, পুরুলিয়ার বাংলাও বাংলা, চট্টগ্রামের বাংলাও বাংলা। বৈধ বাংলা। যদি না, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও কারণে, ব্যবহারকারীরা তাকে অন্য ভাষা বলে দাবি করে। সেটার ভিত্তি অন্য। এইভাবে বাংলার আগেকার কামরূপী উপভাষা (অসমিয়ার গোয়ালপাড়িয়া উপভাষাও খানিকটা) এখন সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে ‘রাজবংশী’ ভাষা হয়েছে।
যাই হোক, এই সব ছুটকো উদাহরণ ছাড়া. এখনও সবই বা়ংলা। কাজেই বাংলাভাষা, সব ভাষার মতোই একটা ভাষাবৈচিত্রের গুচ্ছ মাত্র, একটা অখণ্ড, শিলীভূত ভাষা নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মান্য বা প্রমিত বাংলাই বাংলা, এই সমীকরণের মূলে আছে ওই ভাষারূপটির ব্যাপক ব্যবহার আর মর্যাদা। বিদেশিরা যখন 'আমি বাংলা শিখছি' বলে তারা ওই মান্য বাংলাই বোঝায়, ইশকুল, কলেজের বাংলা পাঠক্রমও মূলত মান্য বাংলার।
ভুলে যাওয়া উচিত না যাকে স্ট্যান্ডার্ড বলা হবে সেটি ছাড়া অন্যান্য উপভাষাগুলিও সবকটিই বৈধ ভাষা, কোনোটাই এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় না। ছাপার অক্ষরে বিশ-পঁচিশ বছর আগে থেকেই আমি এসমস্ত প্রসঙ্গে লিখছি। হযতো বাংলায় লেখা বলে সেগুলি বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চোখে পড়ে না। আসল কথা হলো ভাষা, বিশেষত বড়সড় লিখিত ভাষা একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা অবস্তুক ধারণা। তা কখনোই একটিমাত্র, সংহত, একরূপী (ইউনিফর্ম), অবিমিশ্র, ভূগোলে একস্থানবদ্ধ বস্তু নয়। বাস্তবে তার অনেক ধরনের রূপ আছে।
ঐ মান্য বাংলাই দু’বাংলায়, ত্রিপুরায়, আসামে বিভিন্ন উপলক্ষে চলে। পৃথিবীর নানা জায়গায়, ইংল্যান্ডে, মার্কিন মুলুকে, অস্ট্রেলিয়ায়, জাপানে— নানা অঞ্চলের বাঙালিরা একত্র হলে সেই বাংলায় কথা বলে। কিন্তু সব জায়গাতেই মান্য বাংলা কি একেবারে একরকম? একেবারেই না। মূলত ব্যাকরণটি এক থাকে। কিন্তু এর মধ্যেও বহু স্থানীয় শব্দ ও পদবন্ধ যা ঐ ভাষাকে খানিকটা ‘আঞ্চলিক’ করে তোলে। এতে কিন্তু ‘মান্য’ চেহারাটি অস্পষ্ট হয়ে যায় না। ‘প্রমিত’ একধরনের উচ্চারণও হয়।
প্রশ্ন: তাহলে বাংলা ভাষা নিয়ে এখন যে সব প্রশ্ন ও বিতর্ক তোলা হচ্ছে, অমিত মালব্যরা যা বলছেন সেগুলি অহেতুক?
পবিত্র সরকার: ওদের তো আর এত কথা জানা নেই! খুব ভালো হতো যদি তারা নিজেদের অজ্ঞতা বা কূটনীতি নিয়েই থাকতেন। তিনি কী উদ্দেশে এমন সব কথাবার্তা বলেছেন আমি ঠিক জানি না। কিন্তু এসব বলে তিনি যে নিজের দলের খুব একটা উপকার করেছেন এমনটা বলা যায় না। জানি না, এর পিছনে সেই যে যাকে বলে ‘সেটিং’, সেসব রয়েছে কি না!
যাই হোক, তিনি যদি ভারতের সংবিধানটুকুও পড়ে থাকেন তবে তো অষ্টম তফসিলে ‘বাংলা’ ভাষার স্বীকৃতি দেখতে পাবেন। এমনকি বিভিন্ন অভিধানেও ‘বাংলা’ কথার অর্থ দেখতে পারতেন। এসব উদ্ভট কথাবার্তা আজকের ভারত কিংবা পশ্চিমবঙ্গ কোথাও কেউ মেনে নেবে বলে মনে হয় না।
Bengali Language
অখণ্ড একরূপী ভাষা বলে কিছু নেই
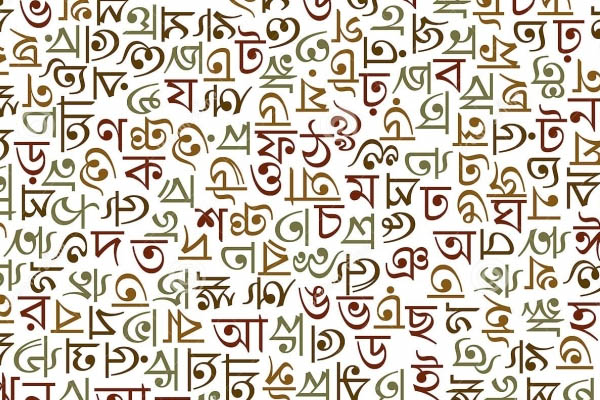
×
![]()



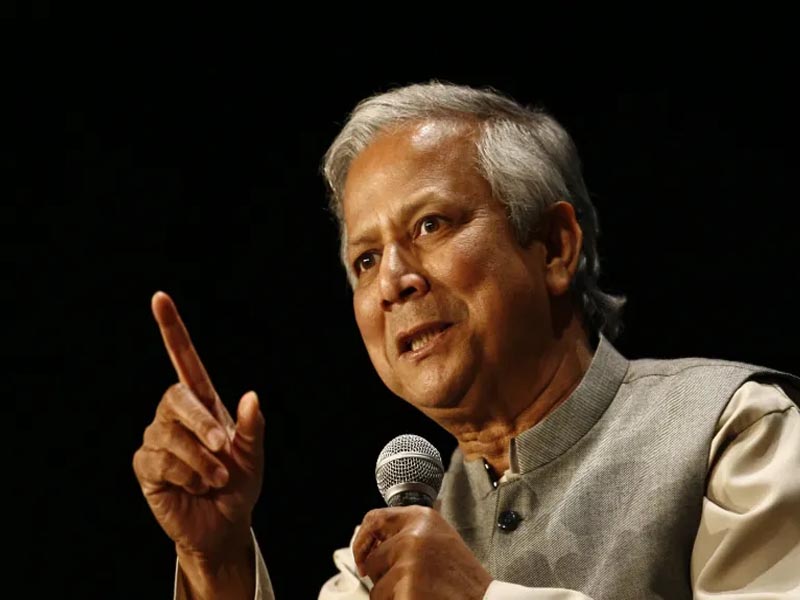



Comments :0