আব্দুল কাফি
কোন পথ দিয়ে এলে তুমি বৈশাখ? বেদনার ভার বয়ে, কোন সংক্রান্তি পেরিয়ে তুমি এলে?
আমাদের বাংলা ভাষার পুরানো সাহিত্যে মাঝে মাঝেই বারোমাস্যা কিংবা বারোমাসী হিসাবে পরিচিত এক ধরনের লেখা দেখতে পাই। সচরাচর কাব্যের নারী চরিত্রেরা তাঁদের বর্ষব্যাপী দুঃখের খতিয়ান মেলে ধরেন সেখানে। পরপর ছয় ঋতুতে, বারো মাসে একেক রকমের কষ্ট সইতে হয় তাঁদের। প্রকৃতির রূপ-বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুঃখী মানুষের বেদনার রং কেমন করে পালটে পালতে যায়, তার হদিশ সেখানে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কবির হাতেই এই বেদনাগাঁথা উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা কিংবা মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন বারোমাস্যা গেয়েছে, তেমনি তার পাশাপাশি দৌলত কাজী কিংবা সৈয়দ আলাওলের কাব্যের বারোমাস্যাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যে পয়লা বৈশাখের দিন নববর্ষ উদ্যাপন করছে মানুষ— এমন দৃশ্য নেই বললেই চলে। এও উল্লেখযোগ্য, অনেক ক্ষেত্রে আবার বারোমাস্যা বৈশাখ মাস দিয়ে নয়, শুরু হয় চৈত্র কিংবা আষাঢ়ে। মৈমনসিংহ গীতিকার বিখ্যাত মলয়ার বারমাসির কথাও মনে পড়তে পারে আমাদের— যেখানে বৈশাখ মাসের কথা আসে নির্মমতার রূপকে—
আইল বৈশাখ মাসের গ্রীষ্ম নির্দয়।
আগুন মাখিয়া অঙ্গে ভানুর উদয়॥
আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ধীরে ধীরে বৈশাখের প্রথম দিনটিকে ঘিরে উৎসব আঁকা হতে থাকে। কোনও কোনও গবেষকের ধারণা এর মূলে আছে পুণ্যাহ উৎসব। মুঘল আমলের রাজস্ব আদায়ের রীতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কিছু ভূমিকাও আছে এর পিছনে। চৈত্র মাসের শেষে ফসল গুছিয়ে খাজনা মিটিয়ে দেবার আয়োজন হিসাবেই পুণ্যাহের সূত্রপাত। শাসকের কাছে পুরানো হিসাব চুকিয়ে দেবার জন্য আসবেন প্রজারা, তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া খাজনা বুঝে নিয়ে, কখনো সখনো কিছু ঋণ মকুব করে, কিছু ক্ষেত্রে নতুন ঋণের বন্দোবস্ত করে দেবার সময় যেটুকু হইচই আমোদ আহ্লাদ হবে সেইটিই পুণ্যাহের উৎসব। এই দিন থেকেই শুরু হবে নতুন হিসাব; নতুন ফসল রচনায়, কৃষিকাজের নতুন উদ্যোগে, নতুন উদ্যমে নেমে পড়বেন মানুষ— তারই আগে আনন্দের আয়োজন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, গোড়ায় এই পুণ্যাহের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সামন্ত প্রভুরা, শাসক পক্ষ, রাজার লোক। রাজস্ব আদায়ের এই রীতি যখন বন্ধ হয়ে গেল, শাসকের তরফে এই উৎসবের উদ্যোগও গেল ফুরিয়ে। কিন্তু সাধারণ কৃষি-সমাজ ততদিনে নিজের আহ্লাদের, আনন্দের একটি পালনীয় দিন পেয়ে গেছে। নবাবের কাছে, জমিদারের কাছে, শাসকের খাজনা মিটিয়ে দেবার “পুণ্য” কাজ বাদ দিয়েও তার আনন্দের অবসর চাই। চৈত্র মাসে তার বছরভর সংগ্রামের সাময়িক ইতি, মাঠের ফসল কুড়ানো এবং তার থেকে রাজার ভাগ পৌঁছে দেওয়া শেষ। এইবার সে আপাতত মুক্ত। অচিরেই আবার নেমে পড়বে মাঠে, শুরু হবে নতুন ফসল-অভিসার।
জমিদারি ব্যবস্থা অবশ্য একটি আবরণ রেখেছিল এই খাজনা আদায় অনুষ্ঠানে। যেন এসব “আদায়” নয় মোটেই, যেন স্বেচ্ছায়, খুশি মনে কৃষক তার ফসলের ভাগ এনে দিচ্ছে জমিদারের বাড়িতে, যেন এসব মোটেই “রাজস্ব” নয় (খেয়াল রাখব, রাজস্ব মানে রাজার যা নিজের অধিকারের জিনিস), এসব আসলে উপহার। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত পঞ্চভূত বইতে একটি কাল্পনিক চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথ এমনই একটি বয়ান হাজির করেছিলেন:
“আমি কহিলাম-- পুণ্যাহ অর্থে জমিদারি বৎসরের আরম্ভ-দিন। আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে। সে টাকা সেদিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ খাজনা দেনা-পাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে একদিকে নিচ লোভ অপর দিকে হীন ভয় নাই। প্রকৃতিতে তরুলতা যেমন আনন্দ-মহোৎসবে বসন্তকে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং বসন্ত তাহা সঞ্চয়-ইচ্ছায় গণনা করিয়া লয় না সেইরূপ ভাবটা আর-কি।”
এতে কোনও সন্দেহই নেই, জমিদার-তনয়েরা যেমনই ভেবে এবং বলে থাকুন, খাজনা মোটেই স্বেচ্ছাকৃত আনন্দের ব্যাপার ছিল না। বসন্ত ঋতুকে প্রকৃতি মহানন্দে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দেয়, পুণ্যাহে তেমন ভাবেই নিজের সঞ্চয় দিয়ে যায় দরিদ্র প্রজাকুল— এই ভাবনায় সত্য নেই, সৌন্দর্যও খুব আছে মনে হয় না। তবে এই কথাগুলি তো রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেননি, বলেছে তাঁর কেতাবের এক পাত্র। উপরে লেখা বয়ানের ঠিক পরে পরেই পঞ্চভূতের অন্য দুই চরিত্র দীপ্তি এবং ক্ষিতি কী বলেছিল সেটিও একবার দেখে নিই--
“দীপ্তি কহিল— কাজটা তো খাজনা আদায়, তাহার মধ্যে আবার বাজনা বাদ্য কেন?
ক্ষিতি কহিল— ছাগশিশুকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায় তখন কি তাহাকে মালা পরাইয়া বাজনা বাজায় না? আজ খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।
আমি কহিলাম— সে হিসাবে দেখিতে পারো বটে, কিন্তু বলি যদি দিতেই হয় তবে নিতান্ত পশুর মতো পশুহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে যতটা পারা যায় উচ্চভাব রাখাই ভালো।”
২
রবীন্দ্রনাথ নিজে এই পুণ্যাহের দিন কী করেছিলেন তার এক চমকপ্রদ খতিয়ান আছে। ১৮৯১ সালের পুণ্যাহের দিনে তরুণ রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে শিলাইদহে উপস্থিত হয়েছেন প্রজাদের মাঝে। খাজনা-আদায় উৎসবে নবীন জমিদার দেখলেন তিনরকম প্রজার জন্য তিনরকম আয়োজন। ব্রাহ্মণদের জন্য উঁচু আসন, অন্যান্য হিন্দুর জন্য জাজিম পাতা আছে আর মুসলমান ও নিম্নবর্ণের জন্য খোলা জমিন। এই অসভ্যতায় আপত্তি জানালেন তিনি, তাতে শোনা গেল, এইটেই পরম্পরা, এমনই হয়ে আসছে। জেদ করে তরুণ কবি জানালেন এই ব্যবস্থা না বদলালে তিনি বয়কট করবেন পুণ্যাহ। নিরুপায় হয়ে সেইদিন জমিদারি কর্তারা সকলের জন্য জাজিম পেতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জমিদারের খাজনা আদায়ের পুণ্যাহ সত্যিকার পুণ্য দিন হয়ে উঠেছিল সেই দিন। হয়তো সাময়িক। হয়তো ভিতরে ভিতরে গালমন্দ করেও মুখে হাসি ফুটিয়ে সেই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল উঁচু বর্ণকে। আর ভ্যাবাচাকা মূর্খ ল্যাঙট আর লুঙ্গি বাহিনী নতুন জমিদারের খামখেয়ালি দেখে খুব একচোট হেসেছিল। ভেবেছিল এও হয়তো বাবুদের এক নতুন মজা। কেউ কেউ মনে মনে আশীর্বাদও করেছিল বৈকি। বছর তিরিশের এই তরুণ রবীন্দ্রনাথ আরও এক দশক বাদে, ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতনে শুরু করবেন অন্য এক উদ্যাপন। সে আর জমিদারের আয়োজন নয়, সে অন্য জিনিস। সে নববর্ষ। ১৪ এপ্রিল সোমবার সেই বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতচন্দ্র সেন ও আরও অনেকে। ঝড় উঠেছিল সেদিন। কালবৈশাখী। তারই মাঝে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ‘আমারে করো তোমার বীণা’৷ সে ছিল আসলে ঝড়ের কাছে নিবেদন— প্রবল ঝঞ্ঝার সুরে আমাকেও তুমি বাজিয়ে তোলো কালবৈশাখী...
খাজনা আদায়ের দিন জমিদারের কাছে পুণ্যদিন। চাষার কাছে, জমি-মজুরের কাছে এই পুণ্যদিনের আবরণটির ওই পারে সত্যিই ছিল উৎসব। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা। ঋণমুক্তি। দু’আনা জিরিয়ে, হইচই নাচ-গান করে, কাচা-কাপড় পরে হাসি আর খুশি বিনিময়। অকারণে যে-যে কাজে সে আনন্দ পায় তাতে নিজেকে মাতিয়ে রাখা। রাজার পুণ্যাহ সরিয়ে ধীরে ধীরে সে মন দেয় বচ্ছরকার দিনে। কীভাবে বাঁচবে নতুন করে, কীভাবে কাজের মাঝে তার গতরে ফুটবে ছন্দ, প্রেম, প্রত্যাশা— তারই পরিকল্পনায় সে মেতে ওঠে। যেন নতুন কেউ আসছে তার বাড়িতে। যেন নতুন লোকটিকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে কোনও খামতি না থাকে। সে সাজে, সাজায় চারপাশ। আলপনা দেয়, আঁকে, নাচে। ছুট লাগায়। যে কাজে সে নিজের মুক্তি টের পায়, নিজের বন্দিত্ব ভুলে যায় সেই কাজে মেতে ওঠে। গান আসে গলায়। অতিথি-বরণ করার ছলে সে নিজের খুশি প্রকাশ করে। প্রকৃতি তার এই অতিথি বরণে হাত মেলায় তখন। নির্দয় গ্রীষ্মকালকেও মনে হয় ঘরে ডেকে বসাই। কারণ এ নতুনের খবর এনেছে।
৩
একা একা কোন উৎসব হয়? কোন আনন্দে আর সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল আমিই থাকে? যত বেশি লোক, তত বড় উৎসব। তত বেশি নিবিড় করে, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নানা "আমি"কে জাপটে ধরে থাকা। অতিথি-বরণ উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য হলো একটি বৃহৎ “আমরা” রচনা। যে কোনও উৎসবই তাই। যে কোনও উৎসবেই মানুষ আমি থেকে আমরা-তে গিয়ে দাঁড়ায়। লেনদেন করে ভাব, ভালোবাসা, আদর, মনোযোগ, সঙ্কল্প। “উৎসবের দিন” নামের একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী— কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ; সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।”
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণ নানাভাবে এমন বেশ কিছু উৎসবের সুযোগ দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই সব উৎসবে মুখ্যত জায়গা জুড়ে থাকে আচার। আর সেই সব উৎসবে যে “আমরা”- টা অনুভূত হয় সেও কোনও না কোনও ধর্মের বেড়ায় বাঁধা। পুণ্যাহ পেরিয়ে যে নববর্ষবরণ এসেছে আমাদের সংস্কৃতিতে, তা ধর্মপরিচয়ের এলাকায় সীমিত নেই। তাতে যে “আমরা”টি ধরা পড়ে সে ভিন্ন গোত্রের। সে সীমানা-বিহীন “আমরা”। ধর্মপরিচয়কে অস্বীকার না করেও এই উৎসব এক বৃহত্তর আমরা গড়ে তোলে। সেই বৃহৎ আমরার মূল পুঁজি হলো হার-না-মানা অপেক্ষা। নতুন করে বেঁচে ওঠার বাসনা। যে মানুষের যেমন স্ফূর্তির অভ্যেস, যাতে সে উল্লসিত হয়, যা সে সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই নিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার উদ্যম। যান্ত্রিক কাজের ফুরসতে নিজেকে অকাজের সৃষ্টিতে আবিষ্কার করার নেশা নববর্ষের মূল রসদ।
নিজের জন্মদিনটিকে নতুন-উদ্যাপনের সঙ্গে বেঁধে ফেলার সুযোগ এসেছিল রবীন্দ্রনাথের। জীবনের শেষ দশকে তাঁর জন্মদিন পালনের উৎসব বৈশাখের পঁচিশ তারিখ থেকে এগিয়ে এসেছিল পয়লা বৈশাখে। রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল তাতে। জীবনের শেষ পয়লা বৈশাখেই রবীন্দ্রনাথের শেষ অভিভাষণ পাঠ করা হয়— সভ্যতার সঙ্কট। রোমাঞ্চিত তৃণদলে কোনও এক নবীনের আগমন-সংবাদ ছিল সেই ভাষণে। অপেক্ষা ছিল। নিজের শেষ জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো পালন করলেন নববর্ষ। জানালেন, অমারাত্রির দুর্গতোরণ ধুলোয় লুটোচ্ছে, মানুষের পৃথিবীতে বেজে উঠচ্ছে বিজয়ডঙ্কা। বৈশাখের সূচনায় আমরা তাই লিখে রাখি আমাদের সূচনার উৎসব।
বৈশাখের পয়লা তারিখটিকে গোড়ায় রেখে বঙ্গাব্দের এই হিসাব কত পুরাতন তা নিয়ে নতুন করে ইদানীং তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে। আকবরের ফসলি সনের হিসাব, নাকি শশাঙ্কের শিলালিপিতে খোদিত অব্দের চিহ্ন— কার পাল্লা ভারী তা নিয়ে ঘোর বুদ্ধবৃত্তির চর্চার আড়ালে প্রায়শই ধরা থাকে বঙ্গাব্দের মালিকানা হিন্দুর না মুসলমানের— এই অশ্লীল বিচারের ঝোঁক। যুক্তি তর্ক, প্রমাণের ভার আকবরি পাল্লায় বেশি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু নববর্ষ উদ্যাপনের যৌথ আহ্লাদে সেসব খুব মাথায় রাখা দরকার কী? ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান ও মহাপণ্ডিত এনামুল হকের একটি চমৎকার প্রবন্ধ ‘বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ’। সেখানে তিনি আমাদের নববর্ষ উদ্যাপনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতের এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন ‘আর্তব-উৎসব’ (আর্তব শব্দের অর্থ ঋতু-সংক্রান্ত) এবং ‘কৃষ্যুৎসব’ (কৃষি-উৎসব) বিবর্তিত হয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের বৈশাখী নববর্ষ। “এর ঐতিহ্য প্রাচীন, কিন্তু রূপ নতুন। নতুন সংস্কার, নতুন সংস্কৃতি, নতুন চিন্তাধারা অবারিত স্রোতে যুক্ত হয়ে এতে সৃষ্টি করেছে এমন এক নতুন আবহ, যাকে একটা দার্শনিক পরিমণ্ডল ব’লে উল্লেখ করতে হয়। এ পরিমণ্ডলে পুরাতন বিলীন, জীর্ণস্তূপ নিশ্চিহ্ন, মিথ্যা বিলুপ্ত ও অসত্য অদৃশ্য। আর নতুন আবির্ভূত, নবজীবন জাগরিত, সুন্দর সুস্মিত ও মঙ্গল সম্ভাবিত। ‘কাল-বৈশাখীই’ এর প্রতীক। সে ‘নববর্ষে’র অমোঘ-সহচর, নব-সৃষ্টির অগ্রদূত, সুন্দরের অগ্রপথিক ও নতুনের বিজয়-কেতন।”
৪
নববর্ষ কীভাবে আসবে আম-জনতার বাড়িতে, আসরে, হৃদয়ে? তার কি কোনও একমাত্রিক চিহ্ন নির্দিষ্ট আছে কোথাও? কোনও নির্দেশিকা, কিংবা কোনও বিধান? সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে প্রকৃতি এবং ভূগোলের গঠন অনুযায়ী আরম্ভের উৎসব আছে নানা ধরনের। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এই বর্ষ-সূচনার অনুষ্ঠানে নানা ধরন, নানা নাম। পাঞ্জাবে, কেরালায়, মহারাষ্ট্রে, আসামে— এমনকি ভারতের বাইরে, থাইভূমিতেও ঈষৎ অদলবদল করে স্থানীয় রুচি ও সংস্কার, অভ্যাস ও সামর্থ্য, পরম্পরা ও কল্পনার উপর ভর করে বহু বিচিত্রভাবে মানুষ সাজিয়েছে তার বর্ষযাত্রার আরম্ভ ক্ষণটিকে। সেইসব আয়োজনের মধ্যে মিশে আছে ইতিহাসের নানা অর্জন— লড়াইয়ের চিহ্ন, আকাঙ্ক্ষার হিসাব, সুখের ও বেদনার নানা কাহিনি। কখনো কখনো মানব গোষ্ঠীর ধর্মাচারের কিছু স্পর্শও তার মধ্যে আছে বইকি। কিন্তু তাকে বারবার ছাপিয়ে গেছে মুক্ত স্বাধীন প্রাণচাঞ্চল্য, বিচিত্র সৃষ্টির উল্লাস।
নতুনের জন্য অপেক্ষা মানুষের চিরন্তন। দুর্বিষহ বেদনায় ডুবে থাকা মানুষ এই অপেক্ষাটুকু নিয়ে বাঁচে। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখে, বলতে পারে— এই যে, আবার শুরু করছি বাঁচা, আবার ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছি, চিৎকার করছি। আবার ধান রুইছি, নিড়ানি দিচ্ছি জমিতে, এই যে ঢুকে পড়লাম কারখানায়, পিঠে তুলে নিচ্ছি মোট, এই যে আবার পা বাড়াচ্ছি যুদ্ধক্ষেত্রে। তার আগে নববর্ষকে বরণ করে নিচ্ছি শরীরে, গতরে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে যে শিল্প আমি রচেছি বারবার আমার এই ভূমিতে, যে গান গেয়েছি আহ্লাদে, প্রতিবাদে, বিক্ষোভে, যে বাদ্যে, নৃত্যে দুলে উঠেছে আমার শরীর— সেই সব দিয়ে তোমাকে বরণ করি বৈশাখ।
জানি তুমি পেরিয়ে এসেছে দাঙ্গা-হাঙ্গামার রাত, একে অপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া অজস্র কটূক্তি, ইট-পাথর, এমনকি বোমা-বারুদ পার করে আসতে হয়েছে তোমায়। ভাঙা দালান ও কুঁড়েঘর, বিষণ্ণ উঠোন আর দাওয়া, সংখ্যায়লঘু আর গুরুর পারস্পরিক বিদ্বেষ, হিংসা, হত্যার পরিসর পেরিয়ে তুমি এসেছ। আজান আর কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি তোমার কানে লেগে আছে মিঠে সুরের মতো। প্রার্থনা আর মোনাজাত তোমার বিকেলের বাতাসে একত্র ভেসে আছে জানি। কিছু কি বিষণ্ণ তুমি? আমাদের অপেক্ষার সামনে এসে বিষাদ কেটে যাক তোমার। এসো তুমি শুরুয়াত, এসো সূচনা, নবীন বর্ষ, এসো বৈশাখ, এসো এসো...
“ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়...”






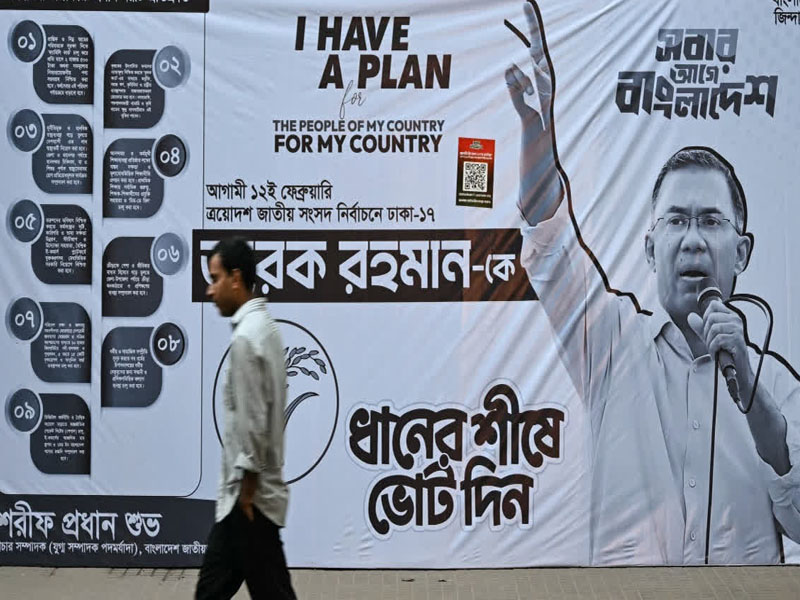

Comments :0