চন্দন মুখোপাধ্যায়
‘ওরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে’! এই উক্তি ব্যবহার করে ইউজিসি-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বাংলার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ২০২৪, ডিসেম্বরে অভিযোগ করেন, "উচ্চশিক্ষায় ইউজিসি যেভাবে চলতে চাইছে, আগামী দিনে পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা পঠনপাঠনের সমান এবং ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে শুধু নয়, এর ফলে জ্ঞান ও সুশিক্ষার অভাবে তাঁরা যেকোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য দাবি নিয়ে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন তুলতে শিখবেন না।" অভিযোগকারী এই ব্যক্তি আর কেউ নন, ব্রাত্য বসু। অথচ যখন ছাত্ররা সেই ব্রাত্য বসুকেই ন্যায্য প্রশ্ন করতে যায়, তখন হয় বিকাশ ভবনে পুলিশ লেলিয়ে দেন অথবা যাদবপুরে তার গাড়ির তলায় চাপা পড়ে প্রতিবাদী মেধাবী ছাত্র। এটাই ওদের দর্শন, শিক্ষাকে এই চোখেই দেখে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সরকার। আর তাই বিজেপি সরকারের ‘ব্যাপম’ দুর্নীতির পর এই রাজ্যে এতবড় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চারিদিক যখন তোলপাড়, সেই সময়েই অন্ধকার দরজা দিয়ে আমাদের নজরের আড়ালে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই এরা ধ্বংস করে দিচ্ছে শুধু তাই নয়, পিছিয়ে পড়া গরিব পরিবারের কেউ যাতে শিক্ষার আলো না পায়, তার ব্যবস্থা করার সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগকেও শেষ করে দিচ্ছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলের করুণ চিত্র উঠে আসে। একজনও ছাত্র-ছাত্রী নেই, এমন স্কুলের সংখ্যায় দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যগুলি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই শিক্ষা মন্ত্রকের ‘ডিপার্টমেন্ট অব স্কুল এডুকেশন অ্যা ন্ড লিটারেসি’র ‘ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস’তৈরি করেছে এই রিপোর্ট। এই রিপোর্টের ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ৩ হাজার ২৫৪টি সরকারি স্কুলে একজনও পড়ুয়া নেই। অথচ এই স্কুলগুলিতে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১৪ হাজার ৬২৭। এদিকে, মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন, এমন ৬ হাজার ৩৬৬টি সরকারি স্কুলে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৯৬। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী মোট বন্ধ হতে যাওয়া স্কুলের সংখ্যা ৮,২০৭। এর মধ্যে প্রাথমিক স্কুল ৬,৭১০, জুনিয়র হাই ১,৪৯৬ এবং হাইস্কুল একটি। স্কুলগুলিতে মোট শিক্ষক ১৯,৮০২ এবং শিক্ষাকর্মী ৭৩৩, মোট পদের সংখ্যা ২০,৫৩৫।
মূল ঘটনাটি লুকিয়ে আছে এর পিছনে। সরকারি ঘোষণায় বন্ধ হওয়া স্কুলের কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের নিকটবর্তী অন্যান্য স্কুলের শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ করা হবে। এর অর্থ স্পষ্ট, সবার অজান্তেই এই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ২০,৫৩৫টি পদ স্রেফ উবে যাবে। এটুকুই সব নয়। এই পদগুলিতে বর্তমানে প্রায় ১২,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী কাজ করছেন। এদের অন্য স্কুলে নিয়োগ করা মানে আরও প্রায় ১২,০০০ এর বেশি শূন্যপদ কিন্তু পূরণ হয়ে গেল। অর্থাৎ এই ৮,২০৭টি স্কুল বন্ধের ঘোষণায় প্রায় ৩০-৩৫ হাজার শূন্যপদের আর কোনও অস্তিত্বই থাকল না। সাধারণ মানুষ, চাকরিপ্রার্থী এবং অভিভাবকরা জানতেই পারছেন না, কিভাবে শূন্যপদ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
এই স্কুলগুলি বন্ধ করার সরকারি যুক্তি কি? ৩ হাজার ২৫৪টি সরকারি স্কুলে একজনও পড়ুয়া নেই। এছাড়াও বলা হয়েছে, তিরিশের কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আছে এমন স্কুলগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী এর মধ্যে এমন স্কুলও আছে যেখানে চল্লিশ এমনকি পঞ্চাশেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী আছে। এই বিতর্কে না গিয়েও এটা বলা যায়, ছাত্র-ছাত্রীর অপ্রতুলতা কখনো সরকারি স্কুল বন্ধ করার যুক্তি হতে পারে না, বিশেষত প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করার ক্ষেত্রে !
আসলে সরকার যখন গরিবের শিক্ষার বিরোধী হয় তখন এটাই স্বাভাবিক। যেমন এই তালিকা প্রকাশ হওয়ার আগেই জঙ্গলমহলে ১৭টি আদিবাসী হস্টেল বন্ধ হয়েছিল সাথে সাতটি জুনিয়র হাইস্কুলও। তার মধ্যে পাঁচটি স্কুলে তখনই একজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন। কেন বন্ধ হয়েছিল? কারণ সরকার ওই জঙ্গলে হস্টেল চালানো জরুরি মনে করেনি। স্কুলগুলিতে শিক্ষক ছিল না, হস্টেলগুলিতে ধীরে ধীরে বন্ধ করা হয় খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। কোনও স্থায়ী হস্টেল সুপার নিয়োগ করা হয়নি। আবাসিক ছেলেমেয়েরা বাধ্য হয়ে হস্টেল ছাড়তে আরম্ভ করে এবং স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনাও বন্ধ করে দেয়।
বাঁকুড়া জেলার রাজকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যা ৪৮, তার মানে এখানে জনঘনত্ব অত্যন্ত কম। যাতায়াতের ব্যবস্থা মসৃণ নয়, যানবাহন অত্যন্ত কম, মানুষের জীবিকা নির্বাহ খুব কঠিন। এইসব অঞ্চলের স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম হওয়াই স্বাভাবিক। তা নিয়ে সরকার একটি মন্তব্যও করেনি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চোদ্দ বছর ধরে শুনছেন জঙ্গলমহল হাসছে। তারপর এবার প্রাথমিক স্কুল অবধি বন্ধ করে দেবার ঘোষণা হয়ে গেল। এবার ভেবে দেখুন, জঙ্গলমহল সত্যিই হাসছে কি না। তাহলে ছাত্র-ছাত্রী নেই যুক্তি কি খাটে?
উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিঙ জেলার অনেকটা জায়গা জুড়ে পাহাড় জঙ্গল, অত্যন্ত দুর্গম। এখানেও প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই খুব কম। এখানে কিন্তু প্রচুর স্কুল আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে একই যুক্তি দেখিয়ে। কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা নিয়ে কাকদ্বীপ সাব ডিভিসনে ৫০টির বেশি স্কুল বন্ধ হতে চলেছে। পাহাড়, জঙ্গল, ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণবঙ্গের বহু জায়গার প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম বা খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্কুলগুলি তুলে দিলে এই শিশুদের পক্ষে ঐ দুর্গম অঞ্চলে দূরের স্কুলে যাওয়া অসম্ভব। তাদের অভিভাবকদের পক্ষেও নিজেদের জীবিকার কঠিন লড়াই থেকে সময় বার করে স্কুলে দিয়ে নিয়ে আসাও অসম্ভব। ফলে এসব অঞ্চলগুলির স্কুল তুলে দিলেই এই শিশুদের জীবনে চিরতরে অন্ধকার নেমে আসবে শুধু নয়, পরের প্রজন্মও ধ্বংস হয়ে যাবে। শিক্ষায় আবার ফিরে আসবে সেই ৭৭ পূর্ববর্তী অন্ধকার খারাপ চেহারা।
শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্টের অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপের অন্যতম বাংলার সাক্ষরতার হার ছিল ১৯৭৭ ৩৮.৮৬ শতাংশ। তা ২০১১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭ শতাংশ, যা সেই সময়ের সর্বভারতীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সাক্ষরতার সাফল্যে ১৯৯১ সালে ইউনেস্কোর বিখ্যাত ‘নোমা পুরস্কার’ পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু তৃণমূলের চোদ্দ বছর শাসনে পশ্চিমবাংলার তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি থমকে গেছে শুধু নয়, আবার নতুন করে মানুষকে নিরক্ষর বানানোর চক্রান্ত হচ্ছে।
আমাদের রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর কতজন ছাত্র ও শিক্ষক আছে এই সংখ্যাটুকুই শুধু জানে, কিন্তু কোন বয়সের শিশুরা কতটা লিখতে, পড়তে, গুনতে শিখল, কিশোররা ভাষা, গণিত বা বিজ্ঞান কতটা আয়ত্ত করল, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিষয়ে কী গবেষণা হলো, কোথায় কতটা এগনো গেল তার কোনও তথ্যই এই দপ্তর রাখে না। তাই এসব তথ্য সরকারিভাবে জানার কোনও সুযোগই নেই। আর তাই স্কুল পড়ুয়াদের পড়াশোনার মান কতটা তলানিতে নেমেছে, সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি ‘প্রথম’-এর মতো দু’-একটি অসরকারি সংস্থার রিপোর্ট থেকে। এদের সমীক্ষায় প্রকাশ, ২০১৮ এমনকি ২০১৪-র তুলনায় এখন প্রাথমিক স্তরে বাংলার শিশুদের পড়া ও গোনার মৌলিক ক্ষমতায় গুরুতর অবনতি ঘটেছে। ২০১৪ সালে অষ্টম শ্রেণির ৭৬.৩ শতাংশ ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণির উপযুক্ত বই পড়তে পারত; ২০২১-এ তা কমে হয়েছে ৬৮.৩ শতাংশ। ২০১৮-তে প্রথম শ্রেণির বাচ্চাদের ২৪.৯ শতাংশের অক্ষরজ্ঞান ছিল না, ২০২১-এ হয়েছে ৩২.১ শতাংশ। প্রথম শ্রেণিতে ১ থেকে ৯ গুনতে পারত না, ২০১৮-তে ২০.৪ শতাংশ, ২০২১-এ বেড়ে হয়েছে ৩০ শতাংশ। বর্তমানে প্রতিদিন সেই চেহারা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।
গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্কুলে সরাসরি নিয়োগ বন্ধ, অথচ স্বাভাবিক নিয়মে অবসর গ্রহণ চলছেই। মানে, শূন্যপদগুলো শূন্যই পড়ে থাকছে তাই নয়, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু কোথাও একজন বা কোথাও যৎসামান্য শিক্ষক নিয়ে এত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া এত স্কুলে চলবে কিভাবে? স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের আর্থিক সাধ্যের বাইরে গিয়েও মাসে ২-৩ হাজার টাকা সাম্মানিকের বিনিময়ে কিছু অস্থায়ী বা আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এইরকম অ-সাম্মানিকের মাধ্যমে কেন এইভাবে শিক্ষক নিয়োগ করতে হচ্ছে! কোনোরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া নিজেরা কোনোভাবে টাকা জোগাড় করে ওই স্কুলের কর্তৃপক্ষের এইটুকুই দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। অনেক শিক্ষিত বেকার যুবদের সামনে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও রাস্তাও খোলা নেই।
একই অবস্থা কলেজগুলিতেও। স্কুলের মতো কলেজেও অতিথি লেকচারার নিয়োগ করা হচ্ছে যৎসামান্য টাকায় প্রতি ক্লাস হিসাবে। এর পাশাপাশি কলেজে ‘স্টেট এডেড কলেজ টিচার’(স্যাক্ট) প্রকল্পের অধীনে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যেখানে ইউজিসি’র সব শর্ত পূরণ না করলেও প্রার্থীদের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। এটা কলেজ সার্ভিস কমিশনের একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা, যেখানে সর্বোচ্চ বেতন মাসে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা (১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে) এবং সর্বনিম্ন কুড়ি হাজার। সিএসসি নিয়োগের অনিশ্চয়তার কারণে এই গেস্ট এবং স্যাক্ট শিক্ষক ছাড়া কলেজগুলি অচল, অথচ একটি কলেজের কোনও বিভাগে স্থায়ী ও স্যাক্ট মিলে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক থাকলে সেই কলেজগুলি আর স্থায়ী শিক্ষকের জন্য আবেদন করতেই পারে না। আবার বিপরীতে স্যাক্ট’র অধীনে কর্মরত থাকলে সেই শিক্ষকের পক্ষেও পরবর্তী ইন্টারভিউতে কলেজে স্থায়ী চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাছে সাবজেক্ট অনুযায়ী অনেক কম শূন্যপদের হিসাব পৌঁছচ্ছে, স্থায়ী কলেজ শিক্ষক হিসাবে খুব কম সংখ্যক প্রার্থী সুযোগ পাচ্ছেন। এইভাবে স্কুলে এবং কলেজে নির্দিষ্ট বেতনক্রমের স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে, তার জায়গা নিচ্ছে অস্থায়ী কাজ। এখনকার নবীন কলেজ শিক্ষকদের বেশির ভাগই স্যাক্ট বা অতিথি শিক্ষক, স্কুলের ক্ষেত্রে ‘প্যারাটিচার’বা আংশিক অস্থায়ী শিক্ষক। অর্থাৎ এক জন ছাত্র গবেষণা করার সময় যে বৃত্তি পাচ্ছেন, ‘স্যাক্ট’-এ তার চেয়ে অনেক কম বেতনে তাঁর কর্মজীবন শুরু করছেন। স্থায়ী জীবিকা হিসাবে যিনি অধ্যাপক বা শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন, সব রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী হয়ে যাচ্ছেন, কারণ আর কোনও উন্নততর বিকল্প তাঁর কাছে নেই। ভেতরের খেলা আরও আছে। স্নাতকোত্তরের পর যাঁরা পিএইচ ডি ডিগ্রি পেতে চান, তাঁদের নেট, গেট এইরকম কিছু কঠিন পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি জোগাড় করতে হয়। তারপর গাইডের অধীনে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে ৪/৫ বছর পরে ডিগ্রি পান। কিন্তু যারা সেভাবে কাজ করার সময় পাচ্ছেন না, অথবা আর্থিকভাবে সচ্ছল, অথচ ডিগ্রিটা দরকার তারা বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচুর টাকার বিনিময়ে পিএইচডি’র জন্যে নাম লিখিয়ে ৩/৪ বছরের মধ্যে তাঁদের ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। স্যাক্ট শিক্ষকদের অনেকেই এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে বাধ্য হচ্ছেন, যাতে তাঁদের বেতনক্রম কিছুটা সংশোধন হয়। এই পদ্ধতিকে ‘ডিগ্রি কেনা’জাতীয় দুর্নীতির সঙ্গে তুলনা না করলেও, শিক্ষাগত যে উত্তরণের জন্য ছাত্ররা পিএইচডি’র মতো একটি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ শুরু করে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন, এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খুব সামান্যই সেটা পাওয়া যায়। এইভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সমান্তরাল এক-একটি চক্র ‘বৈধ’ ভাবেই ঘুরে চলেছে। আর এই শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কাজকে আরও উৎসাহিত করতে এবছর ইউজিসি ঘোষণা করেছে, সরকারি বা বেসরকারি সব পিএইচডি’র মূল্য সমান।
এইভাবে চূড়ান্ত বৈষম্যের অদৃশ্য রেখায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা। শর্ত অনুযায়ীই আংশিক সময়ের, আংশিক বেতনের শিক্ষক তাঁর দ্বিগুণ তিনগুণ বেতনের শিক্ষকদের সমান দায়িত্ব নিতে চাইবেন না। আবার সব নিয়মিত কাজ মাত্র এক-দু’জন স্থায়ী শিক্ষকের উপর পড়লে সেটাও কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়। দুই দল শিক্ষকদের মধ্যে ভাগাভাগিতে বিপদে পড়ে যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। এইভাবে একেবারে ‘বৈধ’ পদ্ধতিতেই স্কুল-কলেজের পড়াশোনা সরকার নীরবে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই তুলে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত।
একটা সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, স্কুল শিক্ষা দপ্তর অন্যান্য দপ্তরকে তালিকা পাঠিয়ে আরজি জানিয়েছে, ফাঁকা স্কুল অন্য কাজে লাগানোর জন্য। ফাঁকা স্কুলে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগেরও পরিকল্পনা চলছে। যেখানে একটা বাথরুম করতে অনুপ্রেরণা লাগে, সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে উঠছে। বেসরকারি স্কুলে ‘নিয়ন্ত্রণহীন ফি’ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তাঁর পর্যবেক্ষণ, “আলু কেনাবেচার মতো শিক্ষা কেনাবেচা করছে বেসরকারি স্কুলগুলি। টাকা ছাপানোর যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের। সরকার কেন পদক্ষেপ করছে না?”
এভাবেই শিক্ষা দুর্নীতির সাথে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই অন্তর্জলিযাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে




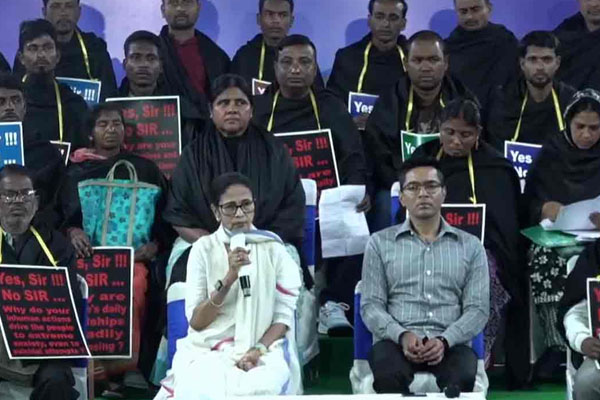



Comments :0