দেবাশিস মিথিয়া
বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে, ‘ডোল পলিটিক্স’ বা ‘পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি’ নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলি সরাসরি নগদ হস্তান্তরের (ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার) প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করছে, কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ফল দেশের অর্থনীতি এবং উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই ‘নির্বাচনী অনুদান’ ভারতীয় রাজনীতিতে আজ এক অনিবার্য বাস্তবতা। এর ফলে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হলো, আমরা কি দেশের দীর্ঘস্থায়ী উন্নতির দিকে মনোযোগ দেব, নাকি তাৎক্ষণিক ভোগের ক্ষণস্থায়ী মোহে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেব?
নির্বাচনী অনুদান: তাৎক্ষণিক লাভ
সম্প্রতি বিহার সরকার নির্বাচনের ঠিক আগে ‘মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা’ নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল, যার অধীনে মহিলাদের এককালীন ১০,০০০ টাকা অনুদান এবং পরবর্তীতে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই মডেলটি অনুদান এবং ক্ষুদ্র ঋণের মাঝামাঝি একটি অবস্থান— অর্থাৎ এটি একটি মিক্সড মোড। যদি এই ১০,০০০ টাকা সফলভাবে ব্যবসার প্রাথমিক মূলধন (সিড ক্যাপিটাল) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং মহিলারা পরবর্তীতে উৎপাদনশীল ঋণের দিকে যান, তবে এটি একটি সফল স্বনির্ভরতার মডেলে রূপান্তরিত হতে পারে। অন্যথায়, এটিও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী অনুদানের জালেই আটকে থাকবে।
অনুদান প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো দ্রুত গরিব মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছে দিয়ে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো, যা স্থানীয় বাজারে সাময়িক গতি আনে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘র্যা ন্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালস’ (আরসিটি)’ দেখিয়েছে নগদ হস্তান্তর কিছু পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে সুফল দেয়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো পশ্চিমবঙ্গের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ এবং মধ্য প্রদেশের ‘লাডলি বেহেনা যোজনা’ ।
তবে, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়লেও, মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। প্রাপ্য এই বিপুল সরকারি অর্থ (যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য বছরে মোটা অঙ্কের বরাদ্দ) বেশিরভাগটাই অনুৎপাদনশীল ভোগ বা দৈনন্দিন খরচের খাতে ব্যয় হয়। ফলে এই বিশাল ব্যয়ভার সরকারি কোষাগারে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। এর অনিবার্য ফল হলো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা পরিকাঠামোর মতো উৎপাদনশীল ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি সঙ্কুচিত হতে বাধ্য হয়। তাছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে এই অনুদান পাওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের নির্ভরশীলতা বা ‘ফ্রি-রাইডার’ মানসিকতা তৈরি হয়। এর ফলে কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের আগ্রহ কমে যায় এবং তাঁরা স্থায়ীভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সংক্ষেপে বলা যায়, এই প্রকল্পগুলি দারিদ্রের সাময়িক উপশম করলেও, দারিদ্রের মূল কারণ বা কাঠামোগত সমস্যাগুলিকে দূর করতে পারে না।
ক্ষুদ্র ঋণ: মুক্তির পথ
বহু অর্থনীতিবিদ মনে করেন, অনুৎপাদনশীল নগদ অনুদানের চেয়ে ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রোফিনান্স)-এর মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষদের, বিশেষত মহিলাদের স্বনির্ভর করার কৌশল সমাজের জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর। এর কারণ হলো: ক্ষুদ্র ঋণ বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) মডেল দরিদ্র মানুষকে নিছক গ্রহীতা নয়, বরং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই ক্ষুদ্র ঋণের অর্থ সাধারণত কুটির শিল্প, পশুপালন বা ছোট ব্যবসার মতো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এটি ঋণগ্রহীতার জন্য একটি স্থায়ী আয়ের উৎস তৈরি করে। এ বিষয়ে বিহারের ‘জীবিকা’ প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গের ‘আনন্দধারা’ প্রকল্পের কথা বলাই যায়।
এই মডেলে ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক শৃঙ্খলা তৈরি হয়। ঋণের টাকা ‘আবর্তনশীল তহবিল’ হিসাবে বারবার ব্যবহৃত হয়ে একটি সুস্থায়ী অর্থনৈতিক চক্র গড়ে তোলে। এসএইচজি থেকে পাওয়া এই ঋণ মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বহুলাংশে বাড়ায়, যা দারিদ্র দূরীকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখে।
তবে, উন্নয়নমূলক অর্থায়নের ক্ষেত্রে, অনুদান ও ঋণের মধ্যে পছন্দের বিষয়টি নির্ভর করে যে দেশে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উপর। অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে, যেখানে দারিদ্র ও ঋণের বোঝা অনেক বেশি, অথবা যেখানে সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি বেশি, সেখানেই সাধারণত অনুদান বা নগদ সাহায্যকে বেশি কার্যকরী ভাবা হয়। কারণ, অনুদান জরুরি খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলা বা মানবিক সহায়তা বিতরণে তাৎক্ষণিক কার্যকর।
কিন্তু ঋণ ব্যবস্থার মূল সুবিধা হলো, ঋণ শোধ করার একটা বাধ্যবাধকতা থাকে। এই বাধ্যবাধকতাটাই এক ধরনের আর্থিক শৃঙ্খলা তৈরি করে। ফলে যারা ঋণ নেন, তাদের মধ্যে সম্পদ ব্যবহারে অনেক বেশি যত্নশীল ও দায়িত্বশীল মনোভাব তৈরি হয়। এই পদ্ধতিটি গ্রহীতাদের আর্থিক দায়িত্বহীনতা কমায় এবং দেওয়া মূলধনটির নিয়মিত ব্যবহার ও ধারাবাহিক আবর্তন নিশ্চিত করে। এই চক্রটি হলো: ঋণ – বিনিয়োগ – আয় – ঋণ পরিশোধ – নতুন ঋণ। অর্থাৎ, এটি একটি সুস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যা অনুদানের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।
হস্তান্তর: কেন ভুল?
অর্থনীতিতে নগদ টাকা সরাসরি মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার যে নীতি (নগদ হস্তান্তর) চালু রয়েছে, তার দু’ধরণের প্রভাব দেখা যায়। একদিকে, এর তাৎক্ষণিক সুবিধা, অন্যদিকে, দেশের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্বাস্থ্যের ওপর এর মারাত্মক চাপ।
মধ্য প্রদেশের ‘লাডলি বেহেনা যোজনা’-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, প্রতি ১ টাকা হস্তান্তরের ফলে অর্থনীতিতে ১.৭ টাকার সমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তৈরি হয়। তবে, মনে রাখতে হবে যে এই অনুদানের টাকা মূলত দৈনন্দিন ভোগ বা খরচের খাতে ব্যয় হয়।
নগদ হস্তান্তর গরিব পরিবারের দৈনন্দিন খরচের বোঝা কমালেও, তা কিন্তু নতুন উৎপাদন বা ব্যবসায় বিনিয়োগের উৎসাহ জোগায় না। এই অনুদানকে যদি কোনও উৎপাদনশীল কাজ বা ব্যবসার প্রাথমিক মূলধনের (সিড ক্যাপিটাল) সাথে না জুড়ে, শুধু একটি ‘নিরাপত্তা জাল (সেফটি নেট)’ হিসাবে দেওয়া হয়, তখন তা দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে পারে না।
ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির দীর্ঘদিনের ধারণা ছিল যে মানুষ কাজ না করে আয় করতে পারলে (নন-লেবার ইনকাম), তিনি কর্মবিমুখ হয়ে পড়তে পারেন। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, দরিদ্র মানুষ এই ধরনের অর্থ পেলেও কাজ করার স্বাভাবিক আগ্রহ হারায় না। প্রকৃত সমস্যা অন্য– আর্থিক অনুদান তাঁদের ভোগের ক্ষেত্রে অর্থের অভাব দূর করলেও, উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতে পারে না। ফলে তাঁদের ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছেকে তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন না।
আশ্চর্যের বিষয় হলো, দরিদ্র মানুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, নীতি নির্ধারকরা ‘নগদ অর্থ হস্তান্তরের’ প্রক্রিয়াকে ‘ম্যাজিক বুলেট’ বা ‘সর্বরোগের দাওয়াই’ মনে করলেও, উপকারভোগীরা কিন্তু তা মনে করেন না। যখন বিহারের গ্রামীণ এলাকার মানুষদের সামনে নগদ অনুদান এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো বৃহত্তর সামাজিক উন্নতির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়, তখন ৮৬ শতাংশ মানুষ তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন।
জনতুষ্টি: আর্থিক ঝুঁকি
নগদ অনুদানের ব্যাপক বণ্টন সরকারি কোষাগারকে ঋণের ভারে জর্জরিত করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থায়ী ভিত্তি দুর্বল করে দিতে পারে। এটা জানা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি অনুদান দেওয়াকেই নির্বাচনী হাতিয়ার করছে। দেশের যেকোনো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ‘প্রতিযোগিতামূলক জনতুষ্টি’ (কম্পিটিটিভ পপুলিজম)-এর এক বিপজ্জনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই প্রবণতায় রাজনৈতিক দলগুলি ভোটারদের আকৃষ্ট করতে নগদ হস্তান্তরের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে—যেমন মহারাষ্ট্রে দেওয়া ₹১,৫০০ টাকার প্রতিশ্রুতি এখন ₹৩,০০০ টাকায় পৌঁছেছে। এই ধরনের ভোট-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা দেশের ১৪টি রাজ্যে প্রায় ২০% মহিলাদের কাছে নগদ অর্থ পৌঁছে দিলেও, তা রাজ্যগুলির রাজস্বের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে।
এই বিপুল ব্যয়ভার সামলাতে রাজ্য সরকারগুলির সামনে দুটি পথ খোলা: হয় অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া, নয়তো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে খরচ কমিয়ে দেওয়া। মধ্য প্রদেশ গত দুই বছরে ২৭,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। একইভাবে, মহারাষ্ট্রের রাজস্ব ঘাটতি প্রায় ৪৫,৮৯১ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। এছাড়াও, এই অনুদান ব্যবস্থার একটি বড় সমস্যা হলো, এটি অভ্যন্তরীণ সম্পদ একত্রিত করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়াও, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ে, যার ফলে প্রভাবশালীরা এই অর্থ আত্মসাৎ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ তার জ্বলন্ত উদাহরণ।
রাজস্ব ব্যয় বনাম মূলধনী ব্যয়
ডোল পলিটিক্স বা বিনামূল্যে অনুদান বিতরণের রাজনীতি, স্বল্পমেয়াদি রাজস্ব ব্যয় (রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বা আরই) এবং দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী বিনিয়োগ ব্যয় (ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বা ক্যাপেক্স)-এর মধ্যেকার অপরিহার্য ভারসাম্যটি নষ্ট করে দিচ্ছে। যখন এই ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ব্যয় মূলধনী বিনিয়োগকে সঙ্কুচিত করে দেয় (‘ক্রাউডিং আউট’), তখন দেশের উন্নয়নের মূল ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রস্তাবনাগুলিতে এই সমস্যাটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: রাজ্য সরকার সামাজিক পরিষেবা খাতে প্রায় ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাজস্ব ব্যয় বাড়িয়েছে, কিন্তু মূলধনী বিনিয়োগ (ক্যাপেক্স) প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছে। একইভাবে, মধ্য প্রদেশের ‘লাডলি বহেনা যোজনা’-এর উচ্চ ব্যয় রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর চাপ সৃষ্টি করায় ১৪টি অন্যান্য ভরতুকি প্রকল্পে আপস করতে হয়েছে।
মূলধনী ব্যয়ের তুলনায় রাজস্ব ব্যয়ে এই অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি গভীর রাজনীতি লুকিয়ে রয়েছে। এর কারণ হলো: রাস্তা বা হাসপাতাল তৈরির মতো পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ (মূলধনী ব্যয়) থেকে রাজনৈতিক ফায়দা আসতে অনেক দেরি হয়, অন্যদিকে নগদ অনুদান (রাজস্ব ব্যয়) ভোটারকে সরাসরি ও তাৎক্ষণিক সুবিধা দেয়, যা দ্রুত নির্বাচনী জয় নিশ্চিত করে। রাজনীতির এই তাৎক্ষণিক প্রলোভন আর্থিক বিচক্ষণতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় বলেই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বন্ধ করা কঠিন। আসলে এটি একটি নিছক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নয়, বরং একটি গভীর রাজনৈতিক ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ।
বামফ্রন্ট: বিকল্প মডেল
ডোল পলিটিক্সের পাইয়ে দেওয়ার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১)। তারা তাৎক্ষণিক ‘নগদ হস্তান্তর’ -এর সাহায্যে ভোট কিনতে না গিয়ে, বরং কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দরিদ্রদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিয়েছিল। তাদের এই নীতির প্রধান উদ্যোগ ছিল ‘অপারেশন বর্গা’, যা প্রজাস্বত্ব নথিভুক্ত করার মাধ্যমে ভাগচাষিদের আইনি সুরক্ষা দিয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে জমি বণ্টন করে জমির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও, বামফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সুসংগঠিত করা শুরু হয়, যা গোষ্ঠীর মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা এবং তৃণমূল স্তরে সক্ষমতা তৈরির ওপর জোর দেয়। যদিও এই মডেলে কিছু ত্রুটি ছিল, তবুও এটি প্রমাণ করে যে দারিদ্র স্থায়ীভাবে দূরীকরণের জন্য কাঠামোগত পরিবর্তনই হলো সঠিক পথ।
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সামাজিক প্রভাব এর অর্থনৈতিক সাফল্যের চেয়েও বহু গুণ বেশি। এই ঋণ, বিশেষত মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায়, দরিদ্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ খুলে দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক মূলধন (পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা) বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া, মহিলাদের হাতে যখন ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ আসে, তখন পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়।
স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর এই ইতিবাচক ভূমিকা একটি সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি তৈরি করেছে। এর ফলস্বরূপ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ কর্মসূচিতে (এসবিএলপি) গোষ্ঠীগত সমর্থন এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্তের কারণে ঋণ পরিশোধের হার অত্যন্ত বেশি থাকে। ঋণ পরিশোধের এই উচ্চ হার বাজারেও আস্থা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে, ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের ক্ষুদ্র ঋণ খাতে মোট ঋণ বিতরণ বেড়ে ৪.০৯ লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে। তবে, শুধুমাত্র ঋণ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত ও সুস্থায়ী ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি আর্থিক সাক্ষরতা, দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা তৈরির মতো কর্মসূচিতে নিবিড় বিনিয়োগও অপরিহার্য।
শেষ কথা: নীতি হোক দৃঢ়
বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, নগদ হস্তান্তরকে কখনোই বৃদ্ধির চালিকা শক্তি (ইঞ্জিন অব গ্রোথ) হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, বরং এটিকে আপৎকালীন সুরক্ষা (সেফটি নেট) হিসাবে কাজে লাগানো উচিত। গবেষণায় দেখা যায়, নগদ হস্তান্তর যখন উৎপাদনশীল অনুদানের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তা খরা বা অন্যান্য বাহ্যিক আঘাতের বিরুদ্ধে পরিবারগুলিকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেয়। অতএব, নীতিগতভাবে অনুদানের ভূমিকা হওয়া উচিত ঝুঁকি হ্রাস করা এবং মৌলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এর ফলে পরিবারগুলি ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার করে উৎপাদনশীল ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত হবে।
‘ডোল পলিটিক্স’ বা অনুদানের রাজনীতি আর্থিক শৃঙ্খলাকে দুর্বল করে, কিন্তূ ক্ষুদ্র ঋণ এবং এসজিএইচ – এর মডেলগুলি সেই শৃঙ্খলাকে জোরদার করে। নীতিনির্ধারকদের সামনে এখন একটাই পথ খোলা – অনুৎপাদনশীল রাজস্ব ব্যয় (আরই) বন্ধ করে, দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী ব্যয়ে (ক্যাপেক্স) বিনিয়োগ বাড়ানো। ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ক্ষমতায়নের মডেলে মনোনিবেশ করা। এটি নিশ্চিত করতে এফআরবিএম (ফিসকাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট) আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং ক্যাপেক্স-এর জন্য বাধ্যতামূলক বরাদ্দ রাখা জরুরি। আসলে, ভোটের বৈতরণী পার হতে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি (ব্যতিক্রম বামপন্থী দলগুলি) দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিকে এমন এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, যার মাশুল গুনতে হচ্ছে গোটা জাতিকে। তাই এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি এখনই বন্ধ হওয়া আবশ্যক!




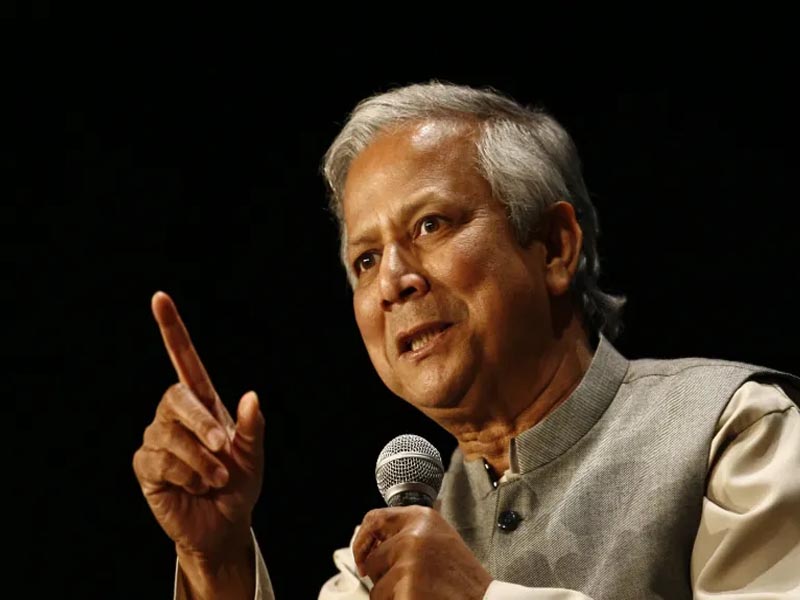



Comments :0