আবীর মজুমদার
চল্লিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি থেকে গোটা এক দশক ধরে জনগণের ব্যথা-বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার লড়াইয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের (আইপিটিএ) সামনের সারিতে ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। পরে আইপিটিএ’র সাথে আপাত বিচ্ছেদ ঘটলেও ঋত্বিকের সত্তায় ও শিল্পে গণনাট্য থেকে গেছে আজীবন-ছাইচাপা আগুনের মতো। গণসংস্কৃতি আন্দোলনে ঋত্বিকের সেই ভূমিকার রূপরেখাটুকু তার জন্ম শতবর্ষের শুরুতে একটু ফিরে দেখা যাক।
১৯৪৩ সাল। ইংরেজ আর কালোবাজারি কারবারীদের যৌথ ষড়যন্ত্রে বাংলা তখন এক ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের শিকার। গ্রাম উজাড় করে নিরন্ন মানুষ শহরমুখী। আকাশে উড়ছে যুদ্ধবিমান, বাতাসে বারুদের গন্ধ। খিদের জ্বালায় বহু পরিবার সন্তানদের, ঘরের মহিলাদের বিক্রি করে দিচ্ছেন সামান্য চালের বিনিময়ে। প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন একঝাঁক প্রগতিশীল, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকার, বুদ্ধিজীবী। ভাবনার জগতে শুরু হলো এক ‘তুমুল শ্রাবণের চাষবাস’। সেই কবন্ধ সময়ে শহরময় কাতর ‘ফ্যান দে মা, ফ্যান দে’ আর্তনাদকে ক্যানভাসে জীবন্ত করে তুললেন জয়নুল আবেদিনের মতো শিল্পী। গড়ে উঠল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (আইপিটিএ)। গান নাটক সহ বিভিন্ন উপস্থাপনায় সলিল চৌধুরি, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সোমনাথ হোর, উৎপল দত্তের মতো দিকপাল শিল্পীদের গণনাট্য সঙ্ঘে উপস্থিতি বিপন্ন সময়ে পথনির্দেশিকা হয়ে উঠল ক্রমে।
এল ১৯৪৬ সাল। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কলকাতায় নিহত হলো আট হাজার মানুষ। আহত কুড়ি হাজারের বেশি। ধর্ষিতা হলেন বহু নারী। ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকা এই ঘটনাকে অভিহিত করল ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ নামে। ওপার বাংলায় রাজশাহী কলেজ ছেড়ে এই সময়েই ছিন্নমূল ঋত্বিক চলে এলেন বহরমপুর। তারপর দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতায়। যুক্ত হলেন আইপিটিএ’তে। এই সন্ধিক্ষণে হারিয়ে গেল আড়বাঁশির সুর, উন্মুক্ত আকাশ ছাওয়া ঋত্বিকের পদ্মার পারের জগৎ। চিরদিনের মতো। বাকি জীবন ঋত্বিক যা খুঁজে বেড়ালেন; কখনো চলচ্চিত্রে, কখনো গল্পে, নাটকে।
ইতিমধ্যেই গণনাট্যের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে আগুন, জবানবন্দি, ল্যাবরেটরি’র মতো কালজয়ী সব নাটক। সেই স্ফুলিঙ্গই দাবানল হয়ে দেখা দিল বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’-এ। অভিনয় করলেন ঋত্বিক। ১৯৫০ সালে বীরু ভট্টাচার্যের ‘ঢেউ’ নাটকে বৃদ্ধ কৃষকের ভূমিকায় অনবদ্য হয়ে উঠল ঋত্বিকের রূপায়ণ। নাটক নির্মাণ ও পরিচালনায় এলেন এরপর। পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহের দাঙ্গার স্মৃতি আর দেশভাগ নিয়ে ঋত্বিক রচিত অসামান্য নাটক ‘দলিল’ ১৯৫৩ সালে বোম্বেতে গণনাট্য’র অধিবেশনে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এই নাটকের একটি সংলাপ, ‘বাংলারে কাটিবারে পারিছ কিন্তু দিলটারে কাটিবারে পারনি’- সেই সময় খুব বিখ্যাত হয়েছিল। কলকাতার ৫০টি আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে ঋত্বিক রচিত ‘জ্বালা’ নাটকটি (১৯৫০) হয়ে থাকল ডকুমেন্টারি থিয়েটারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই নাটকের সংলাপে (‘চিন্তা বহু হয়েছে, আসল দরকার পৃথিবীটাকে বদলানো’) ঋত্বিক সরাসরি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। অর্থাৎ, শিল্প ভাবাবে মানুষকে আর একদিন মানুষ তার চারপাশের পরিস্থিতিটাকে বদলাতে লড়াই করবে। এককথায়, অবজেকটিভ রেসপন্স খুঁজে নেবে তার সাবজেকটিভ ফ্যাক্টরকে। ঠিক যেমন “দ্য টাস্ক অব ইয়ুথ লিগ’-এ লেনিন লিখেছিলেন। সেসময় ঋত্বিকে আপ্লুত কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি সি যোশী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘You are the only true people Artist’।
গণনাট্য-উত্তর পর্বে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে ঋত্বিকের ‘সাঁকো’ নাটকটি আজও যেন মনে হয় সমান প্রাসঙ্গিক। এই নাটকে ব্যবহৃত একটি গান আজও স্মরণীয়- ‘‘চক্র পথে ঘুইরা মোর মন হইল উদাস/বাতাস তবু আভাস দেয় নতুন ভোরের বাস/ব্যথায় আমার বুক যে ভাঙে আশা ভাঙে না/সাথে আছে হাজার মানুষ তুফান ডরিনা”।
‘বিসর্জন’ নাটকে অভিনয়ের পর থেকেই ঋত্বিকের মনে হচ্ছিল, ‘থিয়েটার ইজ ইনঅ্যাডিকোয়েট’। আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে গেলে লাগবে আরও বড় মাধ্যম। অতএব এবার গন্তব্য সিনেমা।
বিমল রায়ের ‘উদয়ের পথে’ যে প্রগতিশীল চলচ্চিত্রের ভাবনাকে উসকে দিয়েছিল, তা যেন আরও তীব্রতা পেল নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ ছবিতে। এই ছবিতে অভিনয়ের আগে ‘তথাপি’ ছবিতে সহকারী পরিচালক ছিলেন ঋত্বিক।
মনে করিয়ে দেওয়া যাক, দেশভাগের ক্ষত তীব্রভাবে ছিন্নমূল ছবিতে তুলে ধরায় ‘পুরস্কার’ হিসাবে স্রষ্টা নিমাই ঘোষকে একরকম রাজ্যছাড়া করল তৎকালীন সরকার (১৯৫০)। ছবিতে দেখানো হয় নলডাঙা গ্রামের জনপ্রিয় যুবক শ্রীকান্ত কিভাবে দেশভাগ, দাঙ্গার কবলে পড়ে সপরিবারে উদ্বাস্তু হলো, পৌঁছালো শিয়ালদহ স্টেশনে। বাড়ির মালিক লেঠেল লাগিয়ে তুলে দেয় শ্রীকান্তর পরিবারকে। তখনই জন্ম নেয় শ্রীকান্তর সন্তান যে যন্ত্রণাক্লিষ্ট কলকাতা শহরে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে জন্ম নেওয়া এক উদ্বাস্তু নাগরিক। এই ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে ঋত্বিক খুব কাছ থেকে বোঝার সুযোগ পান নতুন ধারার ছবির আসল গন্তব্য। সেখান থেকেই তিনি নির্মাণ করেন তাঁর প্রথম ছবি ‘নাগরিক’। কালের পরিহাসে যে ছবি মুক্তি পায় ঋত্বিকের মৃত্যুর পর। বহিরঙ্গের পালিশ না থাকলেও ছবিটি হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক। ছবির মূল চরিত্র রামুকে আমরা প্রথম দৃশ্যে দেখি একটি অসামান্য টপঅ্যাঙ্গেল শটে। নেপথ্যে ঘোষক বলেন, ‘সেই আকাশের তলায় তাকে দেখেছিলাম প্রচুর নাগরিকের মাঝে একটি মাত্র নাগরিক।’ ঈঙ্গিত স্পষ্ট, রামু বিচ্ছিন্ন কোনও নাগরিক চরিত্র নয়, হাজার হাজার উদ্বাস্তু যুবকের প্রতিনিধি যারা দারিদ্রের সাথে লড়াই করেও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। পরিবারকে নিয়ে রামু উদ্বাস্তু হয়ে পৌঁছায় বস্তির নতুন ঠিকানায়। তখন থেকেই তারা প্রান্তিক। চেনা শহরের কয়েকজন উদ্বাস্তু, পরিচয়হীন নিঃসম্বল নাগরিক।
ঋত্বিকের ‘অযান্ত্রিক’ (১৯৫৮) একেবারে অন্য ধারার ছবি। যেখানে সময়ের ট্রান্সসিশনকে ঋত্বিক ধরলেন একটি পুরানো গাড়ির বাতিল হয়ে যাওয়া এবং তার মালিক বিমলের সাথে গাড়িটির এক মানবিক সম্পর্ক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে। প্রায় নির্বাক এই ছবিটি সম্পর্কে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক জর্জ শার্দুল বলেছিলেন, ‘এই ছবি যদি কান ফেস্টিভ্যালে দেখানো হতো তাহলে হাসতে হাসতে বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্টারি হতে পারত।’ কিন্তু ঋত্বিক যে নীলকণ্ঠ। তাই অমৃতে নয় গরলেই তাঁর একমাত্র অধিকার!
ঋত্বিকের সবথেকে আলোচিত এবং একই সঙ্গে সমালোচিত তাঁর দেশভাগ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র ট্রিলজি- ‘মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১) এবং সুবর্ণরেখা-র (১৯৬৫) জন্য।
‘মেঘে ঢাকা তারা’ একটি উদ্বাস্তু পরিবারের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি দেশভাগের প্রোথিত ক্ষত কিভাবে মূল্যবোধকে ভেতর থেকে ধ্বংস করেছে তারই উপাখ্যান। যেখানে নীতার (সুপ্রিয়াদেবী) রোজগারেই সংসার চলে। আর তাকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে পরিবারের বাকি সদস্যদের জীবনযাত্রা। দারিদ্র, খিদের অপমানে নীতার মা-ও যেন বলি দিতে চান নিজের মেয়েকে। মৃত্যুর আগে, ‘‘দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, দাদা আমি বাঁচব’’- নীতার এই সংলাপটির আর্তনাদ আমাদের কুঁকড়ে দেয়। তারপর ঋত্বিক আলগোছে উপসংহারে রেখে যান আরেকটি উদ্বাস্তু মেয়ের পায়ের চটি ছিঁড়ে যাওয়ার দৃশ্য (ঠিক যেমন নীতার ছিঁড়ে গিয়েছিল)। একলহমায় নীতা বা নীতারা ব্যক্তি থেকে শ্রেণির প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হয়।
এরপর ঋত্বিক নিজেই প্রযোজনা করেন ‘কোমল গান্ধার’। বলা হয়, কিন্তু ছবির ন্যারেটিভ বোঝার মতো ‘ফিল্ম লিটারেসি’ তখনো যে এই বাংলায় তৈরি হয়নি! রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে’, আর বিষ্ণু দে তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন বাংলাদেশে। সেখান থেকেই ঋত্বিক শুরু করলেন তাঁর ছবিটি, কারণ তার বাংলাদেশের মনন তখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বহু শতাব্দীর সুর, কথা মিলিয়ে ছবিতে জন্ম নিল এক অদ্ভুত দ্যোতনা— যাতে বেজে উঠল মিলনের সুর। ভৃগুর আক্ষেপ- ‘কি নির্মল ছন্দে শুরু করেছিলাম জীবনটা, এইভাবে কি শেষ হয়ে যাওয়া উচিত?’ আর অনসূয়ার বিলাপ- ‘পদ্মার ওপারে আমাদের দেশ ছিল। আজ ওটা বিদেশ’। ঋত্বিক এই দৃশ্যে এক অনবদ্য ‘বাফার শট’ ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিলেন দেশভাগের অন্ধকার- ”The great Betrayal- inglorious end of glorious struggle” ছবির শেষ দৃশ্যে অনসূয়া, ভৃগুর দুটো হাত এসে মিলে যায়। ক্যামেরা টিল্ট আপ করে দেখায় একটা পাতাহীন শুকনো গাছ আকাশের দিকে ডালপালা ছড়িয়ে আছে। যেন ভাঙা বাংলায় এইভাবেই দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের সাঁকো নির্মাণ করলেন ঋত্বিক।
‘সুবর্ণরেখা’ ছবিতে ঋত্বিক আর শুধু পরিচালক নন। তিনি চলচ্চিত্রের এক দার্শনিক তখন। চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মতে, ঋত্বিক এই ছবিতে প্রথম ‘সাবঅল্টার্ন স্টাডি’ প্র্যাকটিস করলেন। বাগদি বউয়ের নাম কৌশল্যা আর তার ছেলের নাম অভিরাম। ঋত্বিক যেন এই ছবিতে নতুন রামায়ণ লিখলেন। যে মহাকাব্য আসলে দেশের অন্ত্যজ মানুষের দ্বারা রচিত। আর সুবর্ণরেখা হয়ে থাকল চলচ্চিত্রে বাংলার সবথেকে জটিল, বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের এক উৎকৃষ্ট নান্দনিক দৃষ্টান্ত।
‘নাগরিক’ ছবিতে রামু জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হলেও নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখা ছাড়েনি, ‘অযান্ত্রিক’-এ বিমল ভেঙে যাওয়া গাড়িটির দিকে তাকিয়ে দুঃখ পেলেও হেসে ওঠে যখন দেখে একটি শিশু ভেঁপু বাজাতে বাজাতে দৌড়ে যাচ্ছে। এই তো জীবনচক্র। ‘সুবর্ণরেখা’-এর শেষে ঈশ্বর সীতার মৃত্যুর পর তার ভাগ্নেকে নিয়ে এগিয়ে বলে নতুন বাড়ির সন্ধানে, যেখানে প্রজাপতি গান গায়। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবিতেও ঋত্বিক শেষ দৃশ্যে দেখালেন বাসন্তির মৃত্যুর পরেও শুকিয়ে যাওয়া নদীতে চর জেগে উঠেছে। সেই চরের মধ্যে থেকে ছুটে আসছে একটা নগ্ন শিশু, যে আসলে জীবনের নতুন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নতুন জীবনের জন্ম হচ্ছে, কারণ সভ্যতার শেষ নেই তার শুধু ইতিবাচক বাঁক থাকতে পারে।
ঋত্বিকের ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবিতে ছোট্ট কাঞ্চন কলকাতার পালিয়ে গেছিল এল ডোরাডোর খোঁজে। কিন্তু সে ফিরে এসেছিল স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে। এই কাঞ্চন জীবন পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে যখন ফিরে এলেন নীলকণ্ঠ বাগচী হয়ে (যুক্তি-তর্ক আর গল্প) তখন সমাজের রক্তবমন শুরু হয়েছে। দিনবদলের স্বপ্নে বিভোর একদল উদ্দাম বিপ্লবীদের সামনে তাঁর স্বীকারোক্তি— ‘তোমরাই তো সব। দ্য ক্রিম অব বেঙ্গল বাট মিসগাইডেড।’ নীলকয়ণ্ঠ উপলব্ধি করেন— ‘সব পুড়ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে, আমিও পুড়ছি, কিছুতো একটা করতে হবে।’ মদন তাঁতি পায়ে বাত হবে বলে খালি তাঁত চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি মহাজনদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। নীলকণ্ঠও নাম, যশ, অর্থ, খ্যাতির জন্য আপস করতে নারাজ। এই প্রত্যয়ই তো ঋত্বিকের জীবনের প্রকৃত সত্তা, দিকনির্দেশ।
সাম্প্রতিক বাংলার সীমাহীন অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে এই দ্রোহকালপর্বে ঋত্বিক যেন আজও শিঁরদাড়া সোজা রেখে কালের কণ্ঠস্বর সংলাপ করে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আমাদের দিকে ‘‘ভাবো ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো, তোমরা ভাবলে কাজ হবে’’।




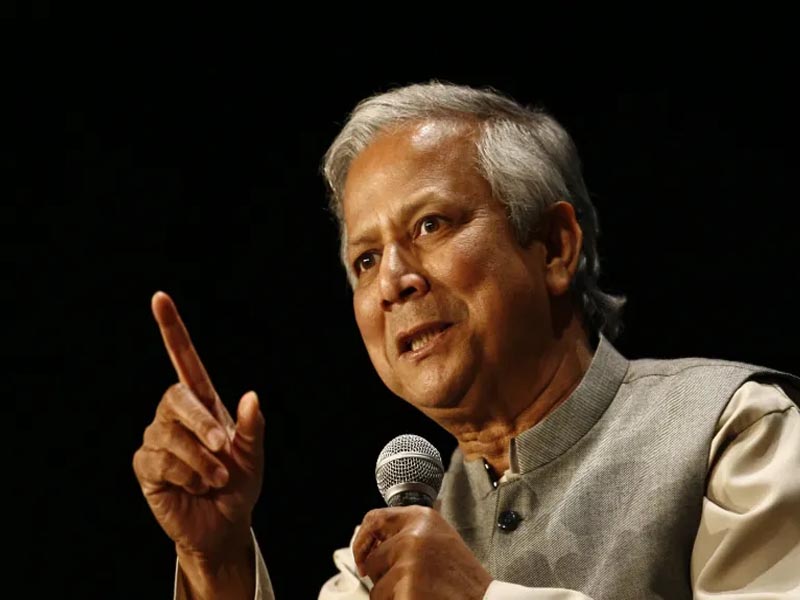


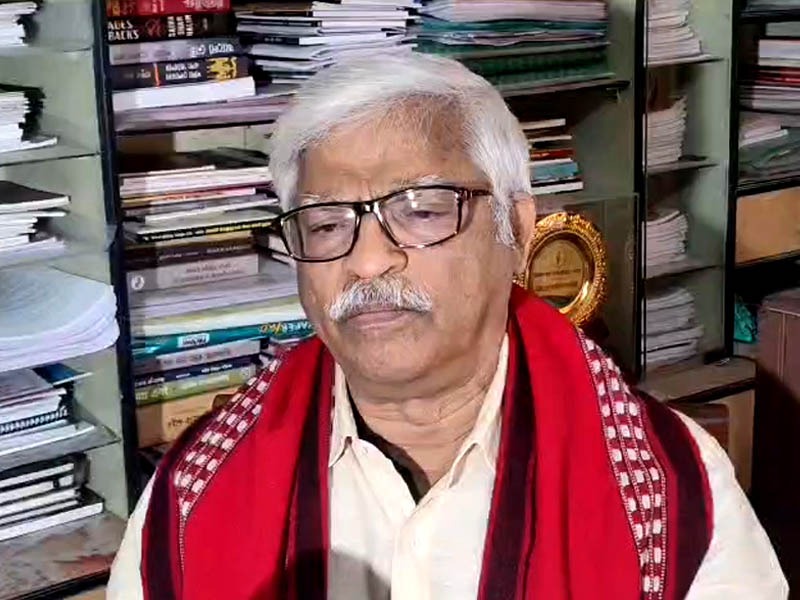
Comments :0