উৎসবে অনুভবে
মুক্তধারা
প্রবন্ধ
দেবী বনাম শোষণ : দুর্গাপুজোর শ্রেণী-রাজনীতি।
অয়ন মুখোপাধ্যায়
১ অক্টোবর ২০২৫, বর্ষ ৩
কলকাতার শহরে এখন উন্মাদনা। গলির মোড়ে মোড়ে গেট বাঁধা হয়েছে, লাইটিং সাজানো, প্রতিটি ক্লাব প্রতিযোগিতা করছে কে বেশি দর্শক টানবে। দুর্গাপুজো বাংলার প্রাণের উৎসব, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আনন্দের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে কঠিন প্রশ্ন—দেবী কি সত্যিই অসুরবিনাশিনী, নাকি তিনি আজ পুঁজির এক সাংস্কৃতিক মুখোশ?
মার্কস লিখেছিলেন—“The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.” (Communist Manifesto, 1848)।
দুর্গাপুজোকে যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে পড়া যায়, তবে স্পষ্ট হবে—এখানে দেবী ও অসুরের পৌরাণিক লড়াইয়ের আড়ালে চলছে বাস্তব শ্রেণীসংগ্রাম—শ্রমজীবী বনাম শোষক।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: গ্রাম থেকে শহর, জমিদার থেকে কর্পোরেট
দুর্গাপুজোর শিকড় গ্রামীণ বাংলায়। কৃষিনির্ভর সমাজে শরৎকালের ফসল কাটার উৎসবই ছিল দেবীর আগমনের মূল ভিত্তি। দেবী ছিলেন উর্বরতার প্রতীক, জমি ও কৃষির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক।
১৭শ শতকে জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো জমকালো রূপ নেয়। প্রাচীন কলকাতায় শোভাবাজার রাজবাড়ি, পথুরিয়াঘাটের চৌধুরির বাড়ি, বাগবাজারের দত্তবাড়ি—সবই ছিল জমিদার শ্রেণির প্রতিপত্তি দেখানোর মঞ্চ। দেবী সেখানে একদিকে ভক্তির প্রতীক, অন্যদিকে জমিদারির ক্ষমতার প্রকাশ।
১৯শ শতকের মধ্যভাগে গড়ে ওঠে “বারোয়ারি পুজো”—যেখানে পাড়ার লোক মিলে সামষ্টিকভাবে পুজো করে। একদিকে এটি গণতান্ত্রিক রূপ, অন্যদিকে স্থানীয় বণিক, বাবু, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষমতা প্রকাশের মঞ্চ।
আজকের ২১শ শতকে দুর্গাপুজো পুরোপুরি শহুরে স্পেক্টাকল। কোটি টাকার বাজেট, বহুজাতিক কোম্পানির স্পনসরশিপ, টিভি রিয়েলিটি শো, সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার—সবকিছু মিশে গেছে। অর্থাৎ দেবী এখন গ্রামীণ কৃষি থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন কর্পোরেট ক্যালেন্ডারে।
শ্রমের অন্তরালে দেবী
প্রতিমার দিকে তাকালে আমরা দেবীকে দেখি—দশভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দিনী। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে চোখে পড়ে প্রতিটি হাতের আঙুলে মাটি লেগে আছে কুমোরের।
কুমোরটুলি হচ্ছে দুর্গাপুজোর আসল গর্ভ। হাজার হাজার শ্রমিক—কেউ বাঁশ কাটছে, কেউ খড় মুড়ছে, কেউ কাদা মাখছে, কেউ রঙ তুলছে। রাত জেগে কাজ চলে। অথচ এই শ্রমিকদের আয় অতি সামান্য। বড় ক্লাব বা কর্পোরেট পুজো কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও মজুরি ঠিকমতো মেলে না।
একই ছবি মণ্ডপশিল্পীদের ক্ষেত্রেও। যাঁরা বাঁশ, কাপড়, ত্রিপল, থার্মোকল দিয়ে চোখ ধাঁধানো থিম তৈরি করেন, তাদের অধিকাংশ দিনমজুর। আলো লাগানো বিদ্যুৎকর্মী, খাবারের দোকানের কর্মচারী, সিকিউরিটি—সবাই শ্রমজীবী।
মার্কস Economic and Philosophic Manuscripts (1844)-এ লিখেছিলেন:
“The worker becomes all the poorer the more wealth he produces.”
শ্রমিক যত সম্পদ সৃষ্টি করে, সে তত গরিব হয়।
দুর্গাপুজোর অর্থনীতিই তার প্রমাণ। শ্রমিক দেবীর জন্ম দেন, অথচ আনন্দে অংশ নেন না।
পৌরাণিক অসুর বনাম বাস্তব অসুর
পুরাণে মহিষাসুর হল অন্যায় শক্তির প্রতীক। দেবী তাকে বিনাশ করেন। কিন্তু আজকের দিনে অসুর কাকে বলা যায়?
কর্পোরেট শক্তি, যারা পুজোকে বিজ্ঞাপনের যন্ত্র বানিয়েছে।
মধ্যবিত্ত ভোগীশ্রেণি, যারা শ্রমিকের ঘামকে ভোগের উৎসবে রূপান্তরিত করে।
রাজনীতির কারবারি, যারা পুজোর নামে ক্ষমতার প্রদর্শন করে।
অর্থাৎ অসুর বিনাশের প্রতীকী মঞ্চ আজ তৈরি হচ্ছে অসুরদের টাকাতেই।
মতাদর্শ ও ভোগ
মার্কস Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1844)-এ লিখেছিলেন:
“Religion is the opium of the people.”
ধর্ম মানুষকে বাস্তব যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখে।
দুর্গাপুজোও তাই। মানুষ এক সপ্তাহ আনন্দে ডুবে থাকে, ভুলে যায় বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি। উৎসব মানুষের মনোযোগ সরিয়ে দেয় বাস্তব সংগ্রাম থেকে।
আলথুসার Ideology and Ideological State Apparatuses (1970)-এ ব্যাখ্যা করেছিলেন—ধর্ম, উৎসব, শিক্ষা—সবই মতাদর্শগত যন্ত্র, যা রাষ্ট্র ও পুঁজির আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। দুর্গাপুজো আজ সেই যন্ত্রগুলির একটি।
দেবী পণ্য হয়ে ওঠেন
আজ দেবী আর শুধু আধ্যাত্মিক প্রতীক নন। তিনি বাজারজাত কমোডিটি। প্রতিমা, মণ্ডপ, ফ্যাশন, খাবার, পর্যটন—সবই পণ্য।
মার্কস Capital (1867)-এ বলেছিলেন “the fetishism of commodities”—মানুষ পণ্যকে দেবত্ব দেয়। দেবীর প্রতিমাও আজ সেই পণ্য ফেটিশের অংশ।
গাই ডেবোর্ড Society of the Spectacle (1967)-এ লিখেছিলেন:
“The spectacle is not a collection of images; it is a social relation among people, mediated by images.”
দেবী আজ সেই স্পেক্টাকলের কেন্দ্র—যেখানে প্রতিমা, আলো, ছবি, সেলফি—সবই বাজারের মাধ্যম।
গ্রামশি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য
অ্যান্টোনিও গ্রামশি তাঁর Prison Notebooks-এ বলেছিলেন—শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক আধিপত্যও তৈরি করে। দুর্গাপুজো সেই আধিপত্যের নিখুঁত মঞ্চ।
কর্পোরেট শক্তি দেবীকে ব্যবহার করছে সংস্কৃতির প্রতীক বানাতে, যাতে শোষণ আড়ালে থেকে যায়। শ্রমিক দেবীর শরীর গড়লেও, কর্পোরেট তাঁর চারপাশে তৈরি করছে আধিপত্যের আখ্যান।
সমকালীন প্রেক্ষাপট
আজকের কলকাতার দুর্গাপুজো একদিকে UNESCO “Intangible Cultural Heritage” স্বীকৃতি পেয়েছে (২০২১), অন্যদিকে শ্রমিকরা তাদের মজুরি নিয়ে আন্দোলন করছে। এই বৈপরীত্যই দুর্গাপুজোর প্রকৃত মুখ।
বছরে প্রায় ৭০-৮০ হাজার কোটি টাকার বাজার তৈরি হয় দুর্গাপুজোকে ঘিরে (ASSOCHAM রিপোর্ট)।
কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত।
ফ্যাশন ও খাদ্য শিল্পে ব্যাপক মুনাফা হলেও কর্মচারীরা নিম্নমজুরি পান।
অর্থাৎ দেবীর নামে বিপুল সম্পদ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু শ্রমিক গরিবই থেকে যাচ্ছে।
দার্শনিক উপসংহার
তাহলে প্রশ্ন: দেবী কে? মুক্তির প্রতীক, নাকি শোষণের হাতিয়ার?
তিনি একই সঙ্গে দুটোই। একদিকে অসুরবিনাশিনী, অন্যদিকে পুঁজির প্রদর্শনী। একদিকে শ্রমিকের সৃজনশীলতা, অন্যদিকে কর্পোরেটের আধিপত্য। এই দ্বন্দ্বই তাঁকে জীবন্ত করে।
কিন্তু যদি দেবী সত্যিই অসুরবিনাশিনী হন, তবে আজকের অসুর হলো—
দারিদ্র্য
বৈষম্য
বেকারত্ব
কর্পোরেট লোভ
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন
মার্কস Theses on Feuerbach (1845)-এ লিখেছিলেন:
“Philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.”
দেবীর ক্ষেত্রেও তাই। তাঁকে কেবল ব্যাখ্যা করলেই চলবে না। তাঁকে সংগ্রামের প্রতীক বানাতে হবে।
যদি দেবী সত্যিই অসুরবিনাশিনী হন, তবে তাঁর বিজয়া হবে শ্রমিকের মুক্তিতে, শোষকের পরাজয়ে। তখন দুর্গাপুজো আর কেবল প্রদর্শনী থাকবে না, হয়ে উঠবে ইতিহাস বদলের উৎসব।

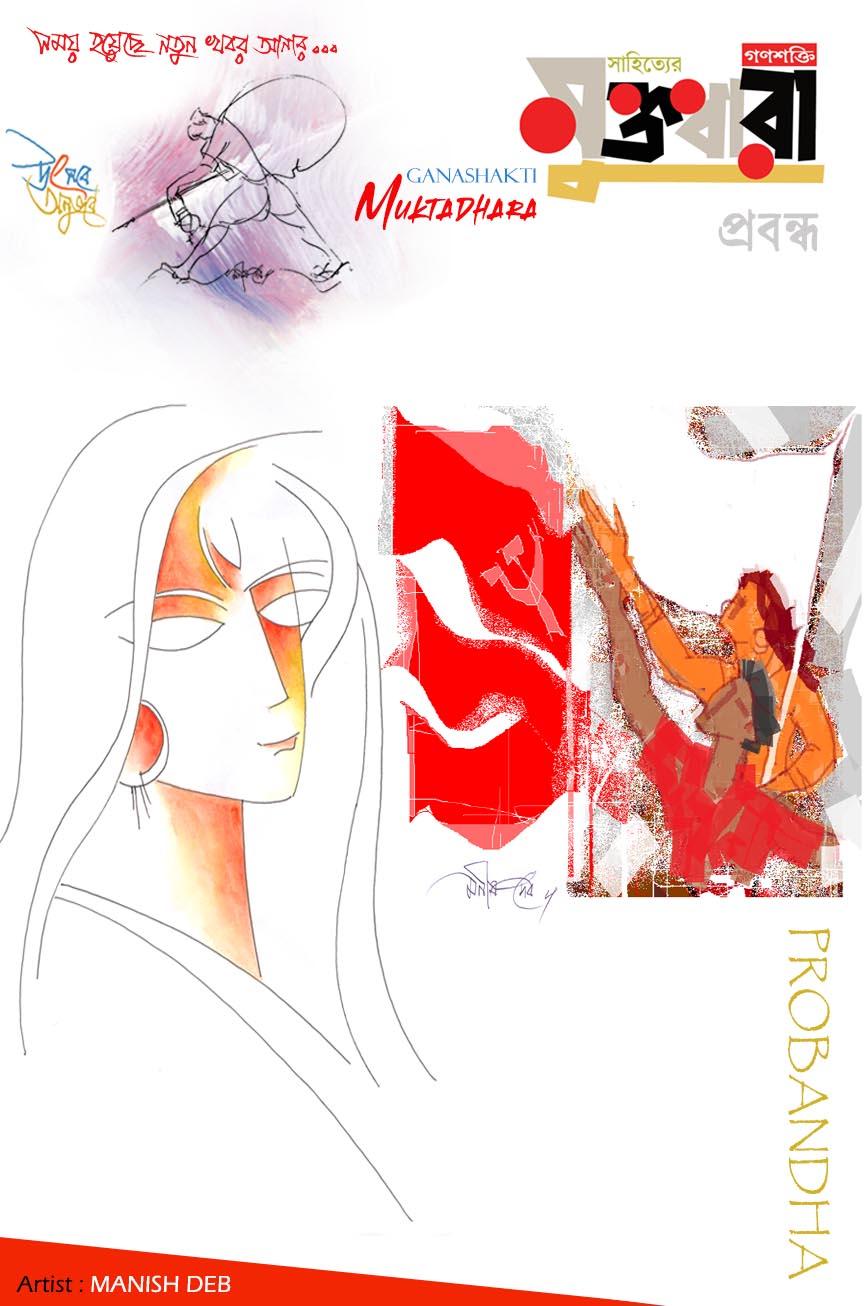
Comments :0