স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে ২০২২-এর আগস্টে কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি লিখেছিলেন প্রবন্ধ— ভারত @ ৭৫। তিনি তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল মার্কসবাদী পথ পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধর অংশ বিশেষ উল্লিখিত হলো।
-----------------------------------
১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন মহাত্মা গান্ধী,যা তিনি ‘চৌরি চৌরা ঘটনা’-র পর প্রত্যাহার করে নেন। ১৯২১ সালে গড়ে ওঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৫ সালে জন্ম হয় আরএসএস’র। সেই পর্ব থেকেই এই তিনটি পৃথক ধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সুতীব্র সংগ্রামের সূচনা হয়। ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের চরিত্র কী হবে, এবং কেমন হবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকাঠামো– এগুলিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল ত্রিধারার এই দৃষ্টিভঙ্গিগত সংগ্রাম।
স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চরিত্র কেমন হবে– এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এই তিন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা ধারাবাহিক সংগ্রামের জন্ম হয় সেই পর্বেই। ভারতবর্ষ হলো বহুত্ববাদী এবং নানাবিধ বৈচিত্রসম্পন্ন দেশ– এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়ে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, দেশ হিসাবে ভারতের ঐক্য এবং ভারতের জনগণের ঐক্য সংহত করা যাবে তখনই, যখন বহুতর বৈচিত্রের মধ্যে অন্তর্লীন সাধারণত্বের যোগসূত্রটিকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে এবং যখন ভারতের বহুত্ববাদের প্রতিটি প্রকাশকে– ভাষাগত, জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সম্মান জানানো হবে এবং সেগুলিকে দেখা হবে সমতার নীতির ভিত্তিতে। এই নীতি আরও একটি বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তা হলো, এই বৈচিত্রের ওপর অভিন্নতা বা একত্ববাদ চাপিয়ে দেওয়ার কোনোরকম চেষ্টা হলে তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর সামাজিক বিস্ফোরণ।
এই উপলব্ধির ভিত্তিতে মূলধারার কংগ্রেসি দৃষ্টিভঙ্গি যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিল তা হলো, স্বাধীন ভারতকে গড়ে তোলা উচিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে। একই লক্ষ্যের প্রতি সহমত পোষণ করেও কমিউনিস্টরা আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ভেবেছিল। তাদের ভাবনাটা ছিল এরকম– ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে আরও সংহত করতে হলে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায় এবং সেটা একমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব।
এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞেয়বাদী অবস্থান ছিল তৃতীয় ধারার। সেই ধারার যুক্তি ছিল, স্বাধীন ভারতের চরিত্র নির্ধারিত হওয়া উচিত দেশের মানুষের ধর্মীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি ছিল দ্বিবিধ– একদিকে মুসলিম লিগ ‘ইসলামিক রাষ্ট্র’-এর দাবির পক্ষে এবং অন্যদিকে আরএসএস ‘হিন্দু রাষ্ট্র’-এর দাবির পক্ষে সওয়াল করে যাবে। ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের দাবিটি সফল হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত বিভাজনের মধ্যে দিয়ে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই বিভাজনে আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়া, মদত দেওয়া ও প্ররোচনা জোগানোর কাজটি করেছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকেরা এবং সেই প্রক্রিয়ার সবরকমের পরিণাম এখনও পর্যন্ত উত্তেজনা ও কুসংস্কারকে তীব্রভাবে জিইয়ে রেখেছে। তবে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকারেরা স্বাধীনতার সময়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক ভারতকে উগ্র অসহিষ্ণুতায় জারিত, ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি ‘হিন্দু রাষ্ট্র’–এ বদলে দেওয়ার প্রকল্প সফল করার প্রয়াস তারা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে গেছে। এককথায়, সমসাময়িক ভারতে মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক সঙ্ঘাত আসলে এই তিন ধারার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা। একথা বলাও নিষ্প্রয়োজন যে, এই সংগ্রামের ওঠাপড়াই ‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’র বা ‘আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা’র বাস্তবায়ন বা অর্জন প্রক্রিয়ার দিশা ও অন্তর্বস্তুকে নির্ধারিত করে দেবে।
আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা: ভারতীয় মহাজাতিত্ব
ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে উৎখাত করে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতীয় জনগণের মহাকাব্যিক সংগ্রামের পর্বেই ‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’ বা ‘আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা’–র ধারণাটি আত্মপ্রকাশ করে। ‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’ বা ‘আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা’ বলতে ঠিক কী বোঝায়? সহজ কথায় বললে, বহুস্তরে-বিন্যস্ত, জটিল বহুমাত্রিকতা বিষয়ে সচেতন থেকেও, এই ধারণাটি যে ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো ভারত এমনই একটা দেশ যে নিজের বিপুল বৈচিত্রকে অতিক্রম করেই সমগ্র দেশের জনগণের অত্যন্ত শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) ঐক্য অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ২০১০ সালে নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হেম্যান সেন্টার ফর হিউম্যানিটিজ-এ অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে ভারতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে একাধিক বক্তা ভাষণ দেন। সেই সব ভাষণ সংশোধিত হয়ে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ সংকলনের ভূমিকায় অধ্যাপক আকিল বিলগ্রামি (আকিল সে সময় ছিলেন হেম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর হিউম্যানিটিজ সেন্টারের চেয়ারপার্সন) ‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’ বা ‘আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা’–র বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ বিষয়ে তখন যা বলেছিলেন সেটা এরকম:
‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’-কে জাতির এমন একটা আদর্শ হিসাবে দেখা যেতে পারে– যে আদর্শে, ভেস্তফালিয়ার শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর ইউরোপে যা কিছু আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেগুলির সম্পূর্ণ গতিপথকেই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে তখন যে বিষয়টা সামনে এসেছিল তা হলো একটা নতুন ধরনের রাষ্ট্রের বৈধতা খোঁজার বাধ্যবাধকতা। রাষ্ট্রের ‘স্বর্গীয় অধিকার’, যে অধিকার আরোপিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সম্রাট বা সাম্রাজ্ঞীর ওপর— এই ধরনের পুরানো ঘোলাটে ধারণার কাছে, সেই পরিস্থিতিতে, নতুন করে আবেদন জানানোর কোনও সুযোগও ছিল না। ভেস্তফালিয়ার শান্তিচুক্তির পর ইউরোপে নতুন যা কিছু আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই সব বিষয়গুলি একদল নতুন ধরনের প্রজাদের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের নতুন একটা রূপের মধ্যে বৈধতা খোঁজার চেষ্টা করেছিল। সেই নতুন ধরনের প্রজারা হলেন ‘নাগরিক’। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের নতুন রূপের অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটা মনস্তত্ত্বেরও একইসঙ্গে বৈধতা খোঁজার চেষ্টা চলছিল। অস্তিত্বের সেই নতুন রূপটি হলো ‘নেশন’ বা ‘জাতি’। পরে এই অনুভূতিরই নাম দেওয়া হয়েছিল ‘জাতীয়তাবাদ’। এবং এই অনুভূতি নাগরিক জনতার মধ্যে জাগিয়ে তোলার দরকার হয়ে পড়েছিল। জাতির অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য ইউরোপ যে সাধারণ প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছিল তা হলো, জাতির মধ্যেই একটা বহিঃশত্রুকে খুঁজে বের করা, জাতির মধ্যেই থাকা সেই বহিরাগতকে, সেই ‘অপর’–কে খুঁজে বের করা (আইরিশ ও ইহুদি এই দুটো নাম করা যায়) যাদের ঘৃণা করতে হবে এবং পদানত করে রাখতে হবে। আরও কিছু সময়ের ব্যবধানে, এই বিষয় সংক্রান্ত আলাপ–আলোচনাকে আরও বেশি সংখ্যাতত্ত্ব ও রাশিবিজ্ঞান ভিত্তিক করে নিয়ে, অপর বা বহিরাগতের নাম দেওয়া হলো ‘সংখ্যালঘু’। এবং যে পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে জাতির জন্য অনুভূতিকে সৃষ্টি করা ও জাগিয়ে তোলা হয়েছিল তার নামকরণ করা হলো ‘মেজরিটারিয়ানিজম’ বা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ।’ (সোশাল সায়েন্টিস্ট, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১১)
আরএসএস–বিজেপি’র লক্ষ্য হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আধুনিক ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে বদলে দিয়ে তাদের ‘হিন্দু রাষ্ট্র’-এর ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করা। এই বিষয়টা, এক অর্থে, সেই ভেস্তফালিয় মডেলেই ফিরে যাওয়া, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে পদানত করে রাখে (মূলত মুসলিম: জাতির ভেতরে বহিরাগত শত্রু) এবং এই মডেল ‘ভারতীয় মহাজাতিত্ব’–এর বিপরীতে ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদ’–কে উৎসাহ দেয়। এ হলো, বস্তুত, সেই ধরনের জাতীয়তাবাদের ধারণায় ফিরে যাওয়া ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলের আলোচনায় যার আধিপত্য ছিল ভারতের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝড় ওঠার আগে। ‘মেজরিটারিয়ানিজম’ বা ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ’–এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র– চরম অসহিষ্ণু ফ্যাসিবাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ যার আরেক রূপ— নাকচ করে দেয় সেই মূল বিষয়টিকেই, যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মহাজাতিত্ব-র চেতনা বিকশিত হয়ে উঠেছিল এবং যে চেতনার মধ্যে বিধৃত ছিল ‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’ বা ‘আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা’। এই ‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’ আসলে ‘একটা নতুন ধরনের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব’–এর উদ্ভবেরই প্রতিফলন।
আরএসএস–বিজেপি’র ধ্বজাধারীরা ‘আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’ বা ‘আধুনিক ভারত গঠনের ভাবনা’কে নিছক একটা আধিবিদ্যক ধারণা বলে উড়িয়ে দেয়। ভারতীয় (হিন্দু) জাতীয়তাবাদকেই তারা প্রদত্ত বাস্তবতা বলে জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতীয় জনগণের মহাকাব্যিক সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ভারতীয় মহাজাতিত্ব (‘দ্য আইডিয়া অব ইন্ডিয়া’)–র বিরুদ্ধে বিজেপি এখন এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎপদতাকে, যার নাম ভারতীয় (হিন্দু) জাতীয়তাবাদ। এবিষয়ে আকিল বিলগ্রামি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ তিনটিগুরুত্বপূর্ণ দশকে জনগণের যে বিশাল ও ধারাবাহিক জমায়েতগুলি ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে সেটা সম্ভব হতো না যদি না এই ধরনের একটা বিকল্প এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার আদর্শ তাদের অনুপ্রাণিত করত।’ (সোশাল সায়েন্টিস্ট, ভল্যুম ৩৯, নভেম্বর ১-২, ২০১১)।
ভারতের ভাষাগত, ধর্মীয়, জাতিগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বৈচিত্র আমাদের জ্ঞাত বিশ্বের যে কোনও দেশের তুলনায় অনেক বেশি বিশাল ও পরিব্যাপ্ত। সরকারিভাবে এর আগে যে বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়েছে তা হলো, ভারতে রয়েছে অন্তত ১৬১৮টি ভাষা, ৬৪০০ জাতিবর্ণ, ৬টি প্রধান ধর্ম যার মধ্যে ৪টির জন্ম এদেশেই। রয়েছে নৃতাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত ৬টি জাতিগোষ্ঠী। এইসব উপাদানকে একসঙ্গে রেখেই একটা দেশ হিসাবে ভারতকে রাজনৈতিকভাবে শাসন করা হচ্ছে। এই বৈচিত্রের অন্য এক পরিমাপ হলো ভারতে পালিত হয় ২৯টি প্রধান ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উৎসব এবং সম্ভবত এদেশেই রয়েছে বিশ্বের অন্য সব দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ধর্মীয় ছুটির দিন।
যারা বলেন এই বিশাল বৈচিত্রকে ব্রিটিশরা ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তারা এই তথ্যটা ভুলে যান যে, এই উপমহাদেশকে দু’টুকরো করার কাজটি করেছে ব্রিটিশেরাই, যার পরিণতিতে ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল এবং বিশাল সংখ্যক মানুষ সাম্প্রদায়িক পরিযানে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের রয়েছে একটা কলঙ্কজনক ইতিহাস। সে ইতিহাস হলো তারা ফেলে রেখে গেছে এমন সব উত্তরাধিকার যা এখনও তাদের উপনিবেশ হিসাবে থাকা দেশগুলির ক্ষতচিহ্নকে বিষিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে এমন ঘটনা ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও ঘটছে প্যালেস্তাইন ও সাইপ্রাসে। স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষের দেশজোড়া সংগ্রামই দেশের বৈচিত্রকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল এবং ৬৬০-র বেশি সামন্ততান্ত্রিক ছোট ছোট রাজ্যকে আধুনিক ভারত হিসাবে সংহত করেছিল, যা থেকে উৎসারিত হয়েছিল এক নিখিল–ভারতীয় চেতনা।




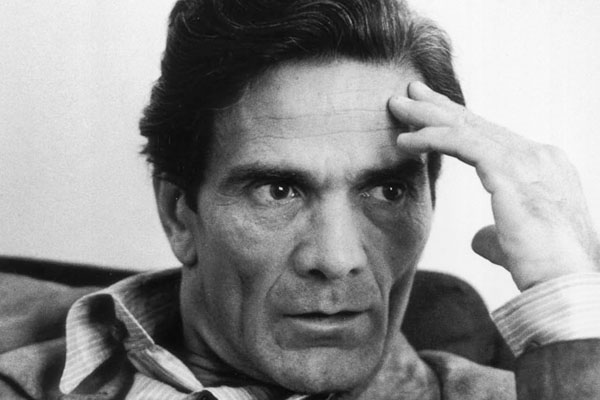
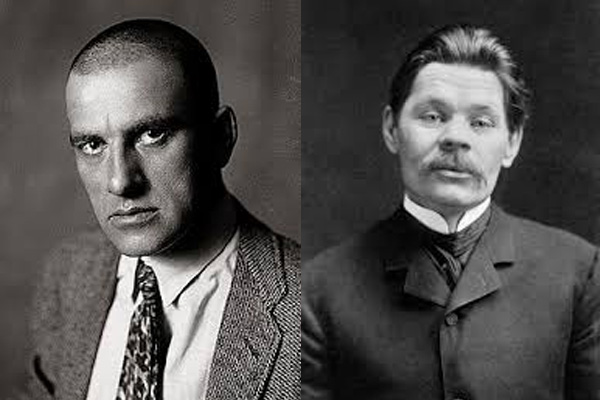


Comments :0