সূর্য মিশ্র
লেনিনের দার্শনিক ‘নোটবই’-এর প্রথম লেখাটি মার্কস এঙ্গেলসের প্রথম পুস্তক ‘দ্য হোলি ফ্যামিলি’র সংক্ষিপ্তসার নিয়ে কিছু মন্তব্য। আপসহীন মার্কস তখন জার্মানিতে চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়ামের রাজত্বে ‘বন’ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনার ভাবনা ছেড়ে দিয়েছেন। সেনসরশিপে অতিষ্ঠ হয়ে কোলোনে ‘রাইন গেজেট’ পত্রিকার সম্পাদকের পদও ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই অবস্থায় তখন স্ত্রী জেনিকে সঙ্গে নিয়ে প্যারিসে চলে আসতে হয়েছে তাঁকে। অন্যদিকে ম্যাঞ্চেস্টারে এঙ্গেলসের ১ ‘সোশাল অ্যাপ্রেন্টিস’ পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনিও ফিরলেন জার্মানিতে। মার্কস আর এঙ্গেলসের দু’জনেরই জন্ম জার্মানির রাইন প্রদেশে, তবে আড়াই বছরের ব্যবধানে। ১৮৪৪ সালের আগস্টের শেষদিকে এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে জার্মানি যাওয়ার পথে প্যারিসে এলেন মার্কসের বাসস্থানে, ছিলেন দশদিন। তখন এঙ্গেলসের বয়স ২৪ পেরোয়নি, আর মার্কস সবে ২৬ পেরিয়েছেন। এই দশদিনেই মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে নিজেদের মধ্যে সহমতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দু’জনেই নব্য হেগেলবাদীদের সঙ্গে সমস্তরকমের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, মার্কস আগে, এঙ্গেলস তার কিছু পরে।
এর আগে ১৮৪২ সালে নভেম্বরের মাঝামাঝি এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময়ে বাবার নির্দেশে ম্যাঞ্চেস্টারে ‘আরমেন এঙ্গেলস’ এর যৌথ মালিকানাধীন স্পিনিং মিলে ব্যবসা ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষানবীশের কাজে যোগ দিতে এঙ্গেলস যাচ্ছিলেন, পথে কোলোনে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তখন কথাবার্তা বেশিদূর এগোয়নি। মার্কস তখন রাইন গেজেট পত্রিকার এডিটর ইন চিফ, এডগার বাউয়ারকে তিনি তখন বচনবাগীশ কমিউনিস্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন। ব্রুনো ও এডগার দুই ভাই ও তাঁদের অনুগামী ইয়াং হেগেলিয়ান গোষ্ঠী এবং তাঁদের পরিচালিত ‘দ্য ফ্রি’ ক্লাবের সঙ্গে এঙ্গেলসের যোগাযোগ ছিল। এঙ্গেলসের প্রভাবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তখন রাইন গেজেট পত্রিকা কেবল ধর্মতত্ত্ব, নাস্তিকতা ছাড়া রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে লেখালেখিতে বিরোধিতা করছিল এবং ইংলন্ডে শ্রমিকদের ‘চার্টিস্ট’ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করছিল। তাদের লেখায় সর্বহারা শ্রেণিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সাথে সাথে কয়েকজন বাছাই করা বীরপুরুষের ওপরেই ইতিহাস রচনার ভূমিকা দিয়েছিল।
লেনিন লিখেছেন, ‘এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে না আসা পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী হননি’ (লেনিন রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২২)। এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে এসে স্পিনিং মিলের দায়িত্ব পালন করার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা শ্রমিকদের বস্তিতে ও তাঁদের কর্মস্থলে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে লিখেছিলেন ‘ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা’। একজন আইরিশ শ্রমিক ম্যারি বার্নসকে সঙ্গে নিয়ে একটার পর একটা শ্রমিক মহল্লায় ঘুরেছিলেন এঙ্গেলস, পরে ১৮৪৩ সালে তাঁর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন— ঠিক সেই বছরই মার্কস জেনিকে বিয়ে করে প্যারিসে দেশান্তরিত হয়েছেন। এঙ্গেলসের লেখা ‘The outlines of a critic of political economy’ তখনই মার্কসের নজর কেড়েছিল। তখন থেকে ১৮৫৭ সালে মার্কসের লেখা Contribution to the critique of political economy’র প্রথম অংশ প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে নিরন্তর আলোচনা ও পত্রবিনিময় চলেছিল দুই অভিন্নহৃদয় কমিউনিস্ট মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে। কিন্তু মার্কসবাদের সূচনা লগ্ন হলো ‘The Holy Family’ দু’জনের প্রথম যৌথ রচনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে।
মার্কস-এঙ্গেলস প্যারিসে নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছিলেন কে কোন বিষয়ে লিখবেন। এঙ্গেলস তাঁর দায়িত্বাধীন অংশটি প্যারিসে থাকার সময় লিখে দিয়েছিলেন। মার্কসের লেখার অংশটি নভেম্বর পর্যন্ত চলেছিল কারণ তিনি ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও বসন্তে লেখা ইকনমিক ফিলজফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্টের কিয়দংশ, ফরাসী বিপ্লব নিয়ে অনুসন্ধান এবং আরও কিছু বিষয়ে সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদি মূল বিষয় লেখার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এর ফলে বইটির আকার অনেকটা বেড়ে যায়, পরোক্ষে প্রাথমিক সেনশরশিপের (তৎকালীন জার্মান রেগুলেশন অনুযায়ী) নজরদারি এড়াতেও সুবিধা হয়। বইটির মূল নামকরণ ছিল ‘ক্রিটিক অফ ক্রিটিক্যাল ক্রিটিসিজম এগেনস্ট ব্রুনো বাউয়ার অ্যান্ড কোং’। ছাপার আগে ব্রুনো এবং এডগার বাউয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের অনুগামীদের শ্লেষাত্মক আক্রমণের জন্য ‘হোলি ফ্যামিলি’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়। অবশ্য ব্রুনো বাউয়ার প্রকাশিত ‘জেনারেল লিটারেসি গেজেট’ নামক মাসিক পত্রিকাটির মাত্র প্রথম ৮টি সংখ্যার (ডিসেম্বর, ১৮৪৩ থেকে অক্টোবর, ১৮৪৪) বিরোধিতাই মার্কস-এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন, তাঁদের পুস্তকের ভূমিকা অংশে।
লেনিন তাঁর ‘দার্শনিক নোটবুক’-এ প্রথম লেখাটি এই ‘দ্য হোলি ফ্যামিলি’ নিয়েই লিখেছেন। এই লেখার সময়কাল ১৮৯৫ সালের ৭ মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সীমিত। তখন লেনিনের বয়স ২৫ বছর। অর্থাৎ মার্কসবাদের সূচনাপর্বে ২৪ ও ২৬ বছর বয়সী দুই হবু মার্কসবাদী যুবকের লেখা প্রায় সাড়ে তিনশো পাতার পুস্তক প্রকাশনার পাঁচ দশক পরে ২৫ বছর বয়সী এক উদীয়মান মার্কসবাদী বিপ্লবী কীভাবে তাঁর নোটবুকে ২৮ পাতার নোট লিখেছেন তা মনে রেখে, লেনিনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই ‘নোটবুক’ পড়া আমাদের শুরু করতে হবে।
শুরুতেই লেনিন কোন অধ্যায় মার্কসের লেখা, কোনটার লেখক এঙ্গেলস, আর কোনটা দু’জনের লেখা, তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মার্কস এঙ্গেলসের লেখা থেকে কেবল নির্বাচিত অংশগুলি উদ্ধৃত করেছেন এবং কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে নিজে মন্তব্য লিখেছেন, দু-একটি ক্ষেত্রে ‘বোরিং’ বলেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লেনিন নিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন, মার্কস এখানে হেগেলের দর্শন থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। লেনিন লিখেছেন, মার্কস এঙ্গেলস শুরু করেছেন জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ব্রুনো বাউয়ার সম্পাদিত ‘লিটারেসি গেজেট’ মাসিক পত্রিকার লেখার ধরন (style), বিষয়বস্তু (theme), ইতিহাসের বিকৃতি, অনুবাদে গুরুতর ভ্রান্তি ইত্যাদির সমালোচনা দিয়ে। এরপর শুরু হয়েছে প্রুঁধোর সমর্থনে বাউয়ারকে মার্কসের জবাব ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা। একেই লেনিন হেগেলীয় দর্শন থেকে মার্কসের সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণ বলে চিহ্নিত করেছেন (critical gloss no 1)। (ক্রিটিক্যাল গ্লস বলতে এখানে মার্কসের ‘প্রতিভাদীপ্ত সমালোচনা’ বলে বুঝতে হবে।) মার্কস এই অংশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মজুরি, শ্রম, মুনাফা, মূল্য, ইত্যাদির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ধর্মের অতি মানবিক রূপের সমালোচনা সহ অ্যাডাম স্মিথের পুঁজিবাদের তত্ত্বের, ডেভিড রিকার্ডোর সমালোচনার পাশাপাশি প্রুঁধোর প্রশংসা করেছেন। এডগার বাউয়ারের উদ্দেশ্যে মার্কস তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে এই অংশকে শেষ করেছেন– ‘যদি প্রুঁধো যথাযথ সিদ্ধান্তে আসতে না পারেন তার কারণ হলো, তাঁর দুর্ভাগ্য যে তিনি জার্মান না হয়ে ফরাসী হয়ে জন্মেছিলেন।’
লেনিনের ভাষায় মার্কসের দ্বিতীয় প্রতিভাদীপ্ত সমালোচনা (Critical Gloss No 2) হলো – ‘এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে ইংলিশ ও ফরাসী প্রলেতারিয়েতের একটা বৃহৎ অংশ এখনই তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য নিয়ে সচেতন এবং তারা সর্বক্ষণ এই সচেতনতাকে উন্নততর করে চলেছে পুরোপুরি স্বচ্ছ বোঝাপড়ায় পৌঁছনোর লক্ষ্যে।’ প্রুঁধো সম্পর্কে মার্কস কিছু সমালোচনামূলক যা লিখেছেন সেটি চিহ্নিত করে লেনিন মন্তব্য করেছেন, মার্কস তাঁর পুরো সিস্টেমের (মতবাদের) মূল বিষয়, উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে বলছেন। মার্কস মূল্যের শ্রমতত্ত্ব পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন।
তৃতীয় ‘ক্রিটিক্যাল গ্লস’-এর শুরুতেই মার্কস লিখেছেন, ‘‘এডগারের না জানার কথা নয় যে তিনি ও তাঁর ভাই ব্রুনো বাউয়ার ‘অসীম আত্মচেতনা’র পক্ষে যুক্তি খাড়া করেই এগিয়েছেন, আবার ‘গসপেল’ এর গঠনমূলক বার্তাগুলির মধ্যে তার সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন, যদিও এই দু’টি পরস্পরবিরোধী। প্রুঁধো মনে করেন সমতা, সাম্য হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির গঠনমূলক নীতির অবদান, যদিও এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি পরস্পরবিরোধী।’’ এরপরেই মার্কসের মন্তব্যকে লেনিন দু’টি পার্শ্বরেখা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। মার্কসের মন্তব্য, ‘উদাহরণস্বরূপ এডগার যদি বিমূর্ত চিন্তায় ফরাসী সমতার সঙ্গে জার্মান আত্মচেতনার তুলনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন, প্রথমটি ফরাসী ভাষায় অর্থাৎ রাজনীতির ভাষায় বলছেন এবং তা সুচিন্তিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।’ লেনিন চিহ্নিত এই অংশের পরেই মার্কস লিখেছেন, ‘বিশুদ্ধ চিন্তায়, মানুষের আত্মচেতনা হলো তার নিজের সঙ্গে সমতা। প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষের চেতনা হলো মানুষের নিজের সম্পর্কে চেতনা, অন্য মানুষদের তাঁর নিজের সঙ্গে সমান এবং তাঁদের সঙ্গে সমতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব। ফরাসী অভিব্যক্তি (expression) অনুযায়ী সমতা হলো, মানবিক সারমর্মের ঐক্য, মানব প্রজাতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং তার প্রজাতি সম্পর্কে মনোভাব, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি সম্পর্কে অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের জন্য।’এরপরেও লেনিন চিহ্নিত অংশে মার্কস লিখেছেন, ‘এডগারের মতে আমরা বারবার একই জায়গায় ফিরে আসি... প্রুঁধো লিখছেন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে। তিনি আত্মনির্ভর সমালোচনার জন্য লেখেন না, বা কোনও বিমূর্ত নিজের তৈরি স্বার্থেও নয়। তিনি লেখেন বিশাল বাস্তব ঐতিহাসিক স্বার্থে। তিনি কেবল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে লেখেন না, তিনি নিজেই মেহনতীও (oeuvre - manual worker) বটে।’
মার্কসের লেখা সম্পর্কে লেনিনের মন্তব্য ‘খুবই চিত্তাকর্ষক হলো মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labor Theory of Value)’ । বাউয়ারের অভিযোগ যে প্রুঁধো শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্য কিনে ফেরত নিতে পারে না বলে গুলিয়ে ফেলেছেন। মার্কস এর জবাবে বলেছেন, কাল্পনিক (Speculative), ২ভাববাদী ইথারীয় সমাজতন্ত্র এবং তার বিপরীতে গণ (mass) সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ।’
এঙ্গেলসের লেখা অংশ উদ্ধৃত করে লেনিন মন্তব্য করেছেন যে, এঙ্গেলস ফয়েরবাখের উষ্ণ প্রশংসা করেছেন। এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেছেন ‘ইতিহাস কিছু করে না, যুদ্ধ বা ধনসম্পদ লুট করে না, কেবল মানুষ, বাস্তবে জীবন্ত মানুষই এসব করে। মানুষ তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা করে ইতিহাস তা ছাড়া কিছু নয়।’ ফয়েরবাখের বস্তুবাদী দর্শনের প্রেক্ষাপটে এঙ্গেলস লিখেছেন, চূড়ান্ত সমালোচনা (absolute criticism) কি তাহলে প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান জার্মান নয়? ভাববাদ বলছে বস্তুবাদের পুরাতন দ্বন্দ্বগুলির বিরুদ্ধে ফয়েরবাখের প্রশ্নে সবদিক থেকে সংগ্রাম এবং অতিক্রম করার পরেও তাদের মৌলিক গোঁড়ামিকে সর্বাপেক্ষা কুৎসিত রূপে হাজির করে এবং খ্রিস্টান জার্মান আত্মার (spirit) জয় ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে মার্কসকে উদ্ধৃত করেছেন লেনিন। ‘বিশেষত সুবিধাগুলি তুলে দিয়ে বাণিজ্য লোপ পায় না, বরং তা প্রকৃত অর্থে মুক্ত বাণিজ্যের রূপ পায়, ঠিক তেমনই ধর্মের বেলায়। সুতরাং ধর্মের বিকাশ হয় তার কার্যকর (ব্যবহারিক/ফলিত) সার্বজনীনতায় কেবল যেখানে কোনও বিশেষ সুবিধাভোগী ধর্ম নেই।’বুর্জোয়া সমাজের নতুন ঝড়ঝঞ্ঝা চিহ্নিত করতে মার্কসের উদ্ধৃতিকে লেনিন চিহ্নিত করেছেন, যেখানে মার্কস লিখেছেন, ‘ফ্রান্সের জমিতে প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তি, যার কাঠামো বিপ্লবের হাতুড়ি দ্বারা বিধ্বস্ত এবং যে জমির বিপুল সংখ্যক নতুন মালিকদের বিপুল উদ্দীপনায় এখন সর্বব্যাপক কৃষির আওতায়, মুক্ত কলকারখানায় প্রথম নাড়াচাড়া— এসব হলো নতুন করে গড়ে ওঠা বুর্জোয়া সমাজের কিছু লক্ষ্মণ।’
নব্য, বাম ? ফয়েরবাখের বস্তুবাদী সমালোচনার সমালোচক হেগেলিয়ান বাউয়েররা। তাঁদের হিরো ৩রুদলফ-ইউজেনে সুয়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘প্যারিসের রহস্য’এর নায়ক। তাঁদের মডেল ৪‘ইয়ং ইংল্যান্ড’ তথা রক্ষণশীল টোরি দলের মডেল। মার্কস-এঙ্গেলস তাই এদের ‘সমালোচনামূলক সমালোচনা’র সমালোচনা লিখেছিলেন।
পাঠকের বোঝার সুবিধার্তে উল্লিখিতি হলো। (সম্পাদক)
১) ‘সোশাল অ্যাপ্রেন্টিস’ কোনো একক রচনা না হলেও, এটি এঙ্গেলসের জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়কালকে বোঝায় যখন তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা, গভীর পর্যবেক্ষণ এবং মার্কসের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একজন পরিণত সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিকে রূপান্তরিত হন। তার প্রারম্ভিক লেখালেখি এবং 'ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' গ্রন্থটি এই সামাজিক শিক্ষানবিশ-এর গুরুত্বপূর্ণ ফসল।
২) ভাববাদী ইথারীয় সমাজতন্ত্র (Idealistic Utopian Socialism) উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে বোঝায়। এই মতবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে একটি নিখুঁত ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তবে বিপ্লবী সংগ্রামের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে।
৩) রুদলফ উপন্যাসটিতে একজন রহস্যময় ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন, যিনি প্যারিসের অন্ধকার গলিতে ঘুরে বেড়ান এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেন। অর্থাৎ শুধুই কল্পনা, প্রকৃত পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করেন না হেগেলিয়ান বাউয়েররা।
৪) ‘ইয়ং ইংল্যান্ড’ (Young England) ছিল ১৮৪০-এর দশকে ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির (টোরি পার্টি) একদল তরুণ, উচ্চবিত্ত ও আদর্শবাদী সদস্যের একটি গোষ্ঠী। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে একটি আদর্শায়িত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার করা। এরাও প্রগতির পথে না গিয়ে ইতিহাসকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়।







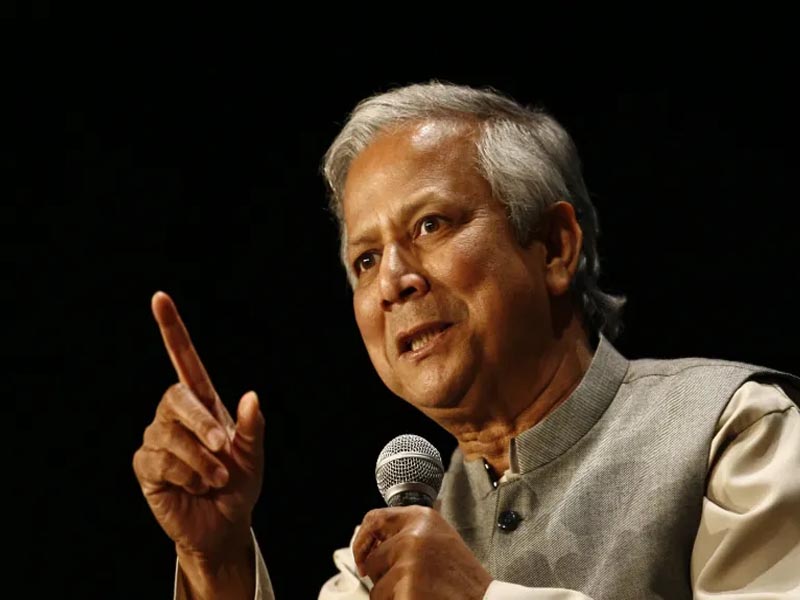
Comments :0