সবচেয়ে বড় কথা, বোকামি করো না, (পার্টিতে) লা-পরোয়া ভোট দিয়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য দেশছাড়া হয়ে কোনও লাভ নেই। বিশ্বাস করো, অপমানটা আমাদের পক্ষে খুব আমল দেওয়ার ব্যাপার নয়। মার্কসবাদী বিপ্লবীদের চাই ধৈর্য আর সাহস; গর্বের গরজ তাদের নেই। দিনকাল খারাপ, আমরা এক অন্ধকার চৌরাস্তায় আছি। এসো, আমাদের শক্তি মজুত রাখি; সময় এলে ইতিহাসই আমাদের ডাক পাঠাবে।
কথাগুলো খুব হালের মনে হচ্ছে? আসলে ভিক্টর সার্জকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন গেওর্গ লুকাচ, ১৯২৯-এ (পরিশিষ্ট দ্রঃ)। বারেবারেই এমন সময় আসে: মূলে একমত হলেও ঘটে যায় মতান্তর। বেশিরভাগ লোক যা ভাবছে, তার সঙ্গে নিজের ভাবনা মেলে না। আবার সবার বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েও কোনও ফায়দা নেই। তবু মনে হয় : ফায়দা না-ই বা হলো, ইতিহাসের কাছে প্রমাণ রাখা চাই। তাতে যা হয় হবে।
সবাই যে এমন ভাবে, তা নয়। আপত্তি থাকলেও অন্যদের মতকেই কেউ বা মেনে নেন নীরবে, বা প্রায় নীরবে। বাকি সকলের বিরুদ্ধে একার মত বলতে ভরসা হয় না। লোকে সেই নিয়ে ঠাট্টা করবে, বেইজ্জত হতে হবে—এই ভেবেও গুটিয়ে যান কেউ কেউ।
হরে-দরে ব্যাপারটা অবশ্য একই। যে মুহূর্তে ঘটনা ঘটছে, কখনও কখনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেই মুহূর্তেই। যদি অগাধ আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে হয়তো নিজের মত নিয়ে লড়ে যাওয়া চলে। অন্য লোককেও দলে টানা যায়। কিন্তু সকলের অবস্থা তো এক হয় না...। নিজের ওপর আস্থা থাকে না সব ব্যাপারে। তখন কী করা যায়?
এইরকম এক পরিস্থিতিতেই কথাগুলো বলেছিলেন লুকাচ। প্রত্যেকটা কথাই বেশ দামি। ভেঙে ভেঙে দেখা যাক।
১. অ প মা ন। ওটা একটা বিলাসিতা। আমাদের সাধ্যের বাইরে। ঘর-সংসারের ব্যাপারেও কি— একটা বয়সের পর— অপমান-অভিমান সাজে? কিছু জিনিস মেনে নিতে হয়। আর সেখানে অন্য পাঁচজনকে নিয়ে কাজ, একটা উচিত লক্ষ্য ও নীতি নিয়ে কিছু করার প্রশ্ন, সেখানে মান-অপমান একেবারেই অচল। ও জ্ঞানটা টনটনে হলে ঘরে বসে থাকাই ভালো। পরের কাজ, দেশের কাজে নামাই উচিত নয়।
২. তার বদলে চাই ধৈর্য আর সাহস। ধৈর্য— কারণ হাতে হাতে ফল পাওয়া বড় একটা হয়ে ওঠে না। অনেকদিন ধরে অনেক লোকের চেষ্টায় অবস্থা আস্তে আস্তে পেকে ওঠে। তখনই আসে ছুরি চালানোর সময়। কাঁচা ফোঁড়ায় ছুরি বসালে হিতে-বিপরীত হওয়ার ভয়।
আর সাহস? শুধু ঝুঁকি নেওয়ার হিম্মত নয়, অপমান সইবার সাহস। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে যা ঠিক বলে জেনেছি, তাকে ধরে রাখার সাহস। ভুল করলে কবুল করার সাহস কোনও চাপের মুখেই মূল নীতিকে বিসর্জন না দেওয়ার সাহস।
৩. গ র্ব: মান-অপমানের মতো এটাও একটা বিলাসিতা। পরের জন্য কাজ করবো— গর্ব করবো নিজেকে নিয়ে— সে কখনও হয়? লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই সমস্ত উদ্যম-উদ্যোগ। গর্বকে সেখানে খর্ব করতেই হবে। ক্ষমতার কম-বেশি থাকে, সবাই একই ধরনের (বা সমান) আত্মত্যাগ করতে পারে না। এক জায়গায় কিন্তু আমরা এক: নিজেকে নিয়ে গৌরবের কোনও দাবি আমাদের নেই।
তার মানে কি এই যে, কোনও গর্বই থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। সেটাও কিন্তু ব্যক্তিগত নয়। সেই গর্ব কাজ নিয়ে, কাজের গুণমান নিয়ে আর সেই সূত্রে সহ যোদ্ধাদের নিয়েও। কে করলো— সেটা কখনই বড় কথা নয়, কী করলো— সেটাই আসল কথা। কাজটাই সব, গৌরব কিছু নয়’ (ডি টাট ইস্ট আল্লেস, নিশটস ড্যের রুহম)—বলেছিলেন গ্যয়টে-র ফাউস্ট।
৪. দি ন কা ল খা রা প— সে তো হবেই। চিরদিন তো আর এক যায় না। নিজেদের দোষেই আমরা অনেক বিপদ ডেকে আনি। তাছাড়া শত্রুপক্ষও তো আর মরে যায়নি। তাদেরও দিন আসে। আবার ফেরে আমাদেরও সুদিন। গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করছে কে কেমন কাজ করছে, তার ওপর। ভালো সময়কেও চিরকাল ধরে রাখবো কী করে? তার কিছুটা আমা দের হাতে সবটা তো নয়। দুর্ঘটনাও ঘটে। আর শত্রু পক্ষের জোর এখন আমাদের চেয়ে অনেক— অনেক বেশি। শুধু টাকার জোর বা অস্ত্রর জোর নয়, বহু জায়গায় বুদ্ধির জোরও।
ওদের হাতে আইন, নিয়মকানুন
ওদের হাতেই প্রায়শ্চিত্ত, জেল
না-ই বললাম পিডি-অ্যাক্টের কথা!
নাই বললাম রাজা-উজিরের কথা!
ওদের হাতেই গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক
মেশিনগান অথবা হাতবোমা
না-ই বললাম লাঠিগদার কথা।
মুশকিল এই যে, সুদিনের সময়ে দুর্দিনের কথা আর মনেই পড়ে না, আবার দুর্দিনের সময়ে সুদিনের কথা মাথায়ই আসে না। অথচ দুটোকে মেলাতে না পারলে হয় হতাশ পরাজয়বাদ, নয় অবোধ আশাবাদ। দুটোই সমান অকম্মের। ছোঁয়াচে আর ক্ষতিকর।
৫. অ ন্ধ কা র চৌ রা স্তা। এর চেয়ে সার্থক কোনও তুলনা ভাবাই যায় না। একে চৌরাস্তা— কোন পথে যাবো, সেটা ঠিক করাই এক সমস্যা তার আবার অন্ধকার— চারটে পথই যে সরেজমিন করে দেখবো, তার উপায় নেই। সবই সমান আবছা।
তো? ন যযৌ ন তস্থৌ? এই সময়েই আসে প্রচণ্ড এক ছটফটানি। মরিয়ার মতো মনে হয়: ঢুকে পড়ি যে-কোনও একটায় চোখ বুঁজে, কোথাও না কোথাও পৌঁছাবোই। উঁকি মারার ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু সর্বদা লাভ হয় না। যাকে ভেবেছিলুম বেরোনোর রাস্তা, আসলে হয়তো সেটা কানাগলি। ফেরার পথও আর ঠাহর করা যায় না তখন শুধুই অনুতাপ: কেন মরতে এইদিকে এলুম!
তবে কি শুধুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার ডান-পা তুলে বাঁ-পা ফেলা, আবার বাঁ পা তুলে ডান পা? এগোচ্ছি না এক কদমও, ঠায় দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়?
এরও কিন্তু দরকার আছে। পথ যেখানে না-জানা, সময় যখন শত্রু— তখন একটু থমকে দাঁড়ানোই ভালো। আমরা যারা ভবিষ্যতের জন্য লড়ি, তারা বাঁচি এই বিশ্বাসেই।
ইতিহাসই আমাদের ডাক পাঠাবে
৬. দি ন আ স বে ই।— তবে কি ইতিহাসকে মানুষের বাইরের কোনও শক্তি বলে ধরছি? ভাগ্য বা কর্মফলের মতো? তা নয়। আমাদের নিয়তি আমরা নিজেরাই গড়ি। যে যা চাই, সবসময়ে অবশ্য তা পাই না। অন্য লোকেও অন্য জিনিস চাইছে। তার জন্য চেষ্টাও করছে। তার সঙ্গে টক্কর লাগবেই। তবু চেষ্টা তো করে চলতেই হয়— পরিস্থিতি বুঝে। তাতে হারও আছে, জিতও আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজ আমাদের মধ্যে থাকলেও, সঙ্গে নেই, কিন্তু তাঁর কবিতা রয়েছে:
হেরেছি? তাতে কী?
কখনও যায় না শীত
এক মাঘে।....
আছে
লড়াইতে হারজিত।
এসো, নিচু হয়ে ভরি—
শুকনো বারুদ
আশার নতুন খোলে
বীরের হৃদয়
যেন লক্ষ্য না ভোলে।
অন্ধকারের পর্দা থাকুক
টানা।
সবুজ পাতায় ঢেকে দাও
আস্তানা।
মুখে এঁটে নাও মুখোশ;
আস্তে কথা।
চুপ
যেন টের পায় না অবাধ্যতা!
দিন আসবেই। আমরা কি নিজের আখের গোছানোর জন্য লড়তে নেমেছি? আমরা চাই মানুষের মুক্তি— খাওয়া-পরা-থাকার অভাব থেকে, বঞ্চনা আর শোষণ থেকে, কুসংস্কার আর অলীক ধর্মবিশ্বাসের দাসত্ব থেকে, নিয়তি আর পূর্বজন্মের অপরাধের নাগপাশ থেকে। যাতে সহজ বিশ্বাসে মানুষ ছুঁতে পারে মানুষকে— মনের সব কালো কেটে যায় যুক্তির আলোয়। যে যা ভাবে পারি, তার জন্যই তো লড়ছি। এখন আমরা সে লক্ষ্য থেকে বহু দূরে। তবু ইতিহাসে তো আমরা দেখেছি: এক-একটা সময়ে দূর আর দূর থাকে না; সামনে আর পিছনে— দু’দিকেই তার চাকা ঘোরে সমান জোরে। ফরাসি বিপ্লবের ঠিক দুশো বছর পরে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সমেত গোটা পূর্ব ইউরোপে চোখের সামনে এই যে এতগুলো প্রতিবিপ্লব হয়ে গেল— এতেই ইতিহাসের শেষ? আর কখনও বিপ্লব হবে না? শুধুই প্রতিবিপ্লব হবে? একের পর এক? প্যারি কমিউন (১৮৭১)-এর পতনের পর আর কি বিপ্লব হয়নি? রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) এতকাল পরেও প্রতিবিপ্লব যদি জিতেও যায়, তার মানে কি এই যে, আর কোনোদিনই কিছু হবে না?—হবেই। দিন আসবেই।
সেদিন কবে আসবে, কী করে আসবে, কারা আনবে— সে আমাদের জানা নেই অন্ধকার চৌরাস্তার কথা নাহলে বলা কেন? আর ঠিক সেই জন্যই অকাজে আত্মক্ষয় করে লাভ নেই। বরং খেয়াল রাখা দরকার, অযথা যেন শক্তির অপচয় না হয়। সময় এলে ঝাঁপিয়ে পড়ার তফাতটুকু থাকে। দেহের, মনের। বিশেষ করে মনের।
ব্যাখ্যাটা হয়তো সবার মনে ধরবে না। না ধরারই কথা। চারধারের ঘটনাকে প্রত্যেকেই তো এক চোখে দেখছেন না। দিনকাল যে খারাপ— তার হিসাব সকলের এক নয়।
একটা গল্প মনে পড়ে গেল। থই থই বন্যার জলে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মাত্র লোক। দূর থেকে তাঁকে দেখে একটি ছেলে জানতে চাইলো:
—দাদা, ওখানে জল কত?
—যতটা ভাবছো, তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি একটা কুঁড়ের চালে দাঁড়িয়ে আছি।
স্রোতের উলটোমুখে সাঁতরাতে চাইলে এখন বীরত্বের প্রমাণ হবে না, প্রমাণ হবে নির্বুদ্ধিতার। আমরা যে মরি নি— আত্মহত্যা করে (কাদম্বিনীর মতো) সেটা জানান দেওয়ার কোনও মানে হয় না। বরং স্রোত ঘুরলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে শরীর-মন চাঙ্গা রাখা চাই।
ইওরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থানের যুগে সার্জকে কথাগুলো বলেছিলেন লুকাচ। তাঁকেও তার মতো বিপ্লবীদের সত্যিই পরে ডাক পাঠিয়েছিল ইতিহাস। তাঁরা লড়েছিলেন, জিতেছিলেন। ঘরোয়া লড়াইয়ে, ফালতু কাজিয়ায় এখন যদি সব শক্তি খতম করে ফেলি, ঠিক সময়ে আর সে ডাকে সাড়া দেওয়া যাবে না। এখন, এই সময়ে আমাদের এখানে, ছত্রাখান অবস্থায় দাঁড়িয়েও লুকাচের কথাগুলোই মাথায় রাখা দরকার: সবচেয়ে বড় কথা, বোকামি কোরো না, (পার্টিতে) লা-পরোয়া ভোট দিয়ে আনন্দ পাওয়ার জন্যে দেশছাড়া হয়ে কোনও লাভ নেই। বিশ্বাস করো, অপমানটা আমাদের পক্ষে খুব আমল দেওয়ার ব্যাপার নয়। মার্কসবাদী বিপ্লবীদের চাই ধৈর্য আর সাহস; গর্বের গরজ তাদের নেই। দিনকাল খারাপ, আমরা এক অন্ধকার চৌরাস্তায় আছি। এসো, আমাদের শক্তি মজুত রাখি; সময় এলে ইতিহাসই আমাদের ডাক পাঠাবে।
পরিশিষ্ট
ভিক্টর সার্জ (১৮৯০-১৯৪৭) : নৈরাজ্যবাদী, বলশেভিক, ট্রটস্কিবাদী, শোধনবাদী-মার্কসবাদী, শেষে একেবারেই (তাঁর নিজের ভাষায়) ‘ব্যক্তিবাদী’। পৈতৃক সূত্রে রুশ, জন্ম ও শিক্ষা বেলজিয়ামে, লিখতেন ফরাসিতে। মারা যান মেক্সিকোয়, রাষ্ট্রহীন উদ্বাস্তু হিসাবে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রচার, পরিচালনা ইত্যাদির কাজে যুক্ত থাকার সময়ে লুকাচের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।
গেওর্গ লুকাচ (১৮৫৮-১৯৭১): হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট, দার্শনিক, সাহিত্য-সমালোচক। পার্টি ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে, বারবার বিরোধ হয়েছে— গ্রেপ্তার ও তাড়ন সত্ত্বেও নিজের পথ থেকে সরেননি (যেমন সরেছিলেন সার্জ ও আরও অনেকে— যেমন সরছেন এখন কিছু দুর্বলচিত্ত লোক।
সার্জ তাঁর স্মৃতিকথায় (মেমোয়ার্স অব আ রেভলিউশনারি ১৯০১-১৯৪১, লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭। প্রথম প্রকাশ ফরাসিতে, ১৯৫১, অধ্যায় ৫) বলেছেন, ১৯২৬ নাগাদ ভিয়েনায় লুকাচ তাঁকে এই কথাগুলো বলেন। কিন্তু মিশেল ল্যোউই (Michel Lowy) দেখিয়েছেন, এটি ১৯২৯-এ মস্কোয় ঘটে থাকাই সম্ভব (গেওর্গ লুকাচ : ফ্রম রোম্যান্টিসিজম টু বলশেভিজম, লন্ডন : এন এল বি, ১৯৭৯, পৃ. ২০০ টীকা ২০ ও ২১ দ্র.)।
প্রথম গানটির লেখক বের্টল্ট ব্রেশট, অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ (মা, গোর্কির উপন্যাসের নাট্যরূপ, কলকাতা : প্রফুল্লকুমার ঘোষ/দে বুক স্টোর, ১৯৭৩, পৃ. ৪১-৪২)। দ্বিতীয় কবিতাটি (‘রংরুট’) আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যত দূরেই যাই (কলকাতা : ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৩৭২, পৃ. ৩৩)-এ।


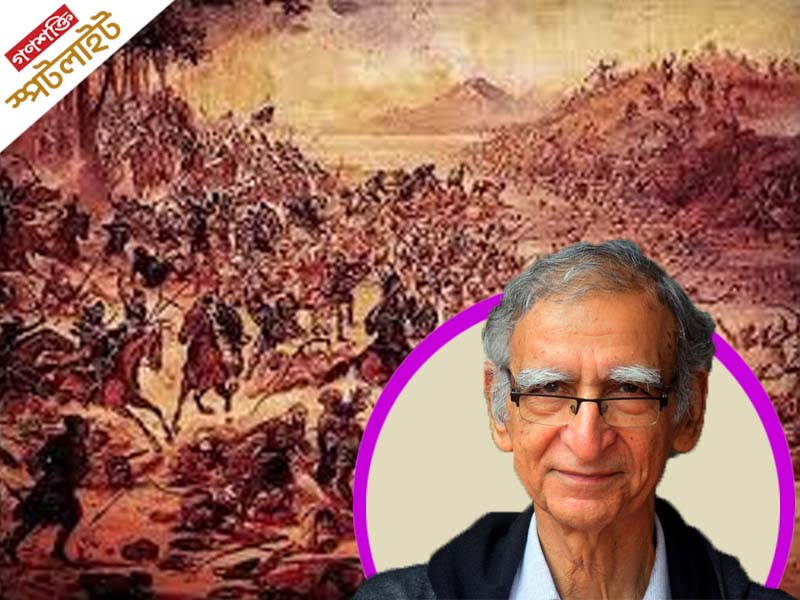





Comments :0