ডাঃ ফুয়াদ হালিম
৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আমাদের বক্তব্য একটাই, তা হলো স্বাস্থ্যের অধিকার আমাদের সকলের। এই অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যেক মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু তাঁর আগে দেখা দরকার আন্তর্জাতিক সূচকের আঙ্গিকে আমরা ভারতবাসীরা কোন স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছি।
————————————————————————————————————————————————
সুচক ২০১৪ ২০২২ পার্থক্য
----------------------------------------------------------------------------------
সামগ্রিক স্বাস্থ্য ৮৫ ১৪৬ ৬১
ক্ষুধার তালিকায় ৫৫ ১০৭ ৫২
লিঙ্গ সমতা ১১৪ ১৩৫ ২১
বিশ্ব স্বস্তি সূচক ১১১ ১৩৯ ২৮
স্বধীনভাবে বাঁচার সূচক ১০৬ ১৫০ ৪৪
পরবেশ রক্ষার সূচক ১৫৫ ১৮০ ২৫
——————————————————————————————————————————————
এই পরিসংখ্যান নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করছে কয়েক বছরের মধ্যে আমরা কত দিক থেকে নিচে নেমে গেছি।
বস্তুত: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের স্লোগান— মাই হেলথ; মাই রাইট আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে এক গভীর পর্যবেক্ষণের কথা। তা হলে পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। একদিকে পরিবেশ বিপর্যয়, বায়ু দূষণের কারণে আমরা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছি। অন্যদিকে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্রমসঙ্কোচন ঘটছে। প্রান্তিক গরিব মানুষের কাছে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা। বিশ্বের ১৪০টি দেশ তাদের সংবিধানে স্বাস্থ্যকে মানুষের মানুষের অধিকার বলে স্বীকৃতি দিলেও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, তার যথাযথ প্রয়োগ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ২০২১ সালেও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আসেনি।
একটি সরকারি হাসপাতালে বা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি কি পরিষেবা পেতে পারেন সাধারণ মানুষ, সেখানে সুচিকিৎসার জন্য কি কি সুবিধা বা পরিকাঠামো থাকতেই হবে— সেসব সাধারণ মানুষের জানার অধিকার আছে। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার। সেই অধিকারের দাবি নিয়ে গোটা রাজ্যে সোচ্চার হয়েছে পিপলস রিলিফ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন।
একটি বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো স্বাস্থ্যের জন্য ভারত সরকারের বরাদ্দ মাত্র ২.১ শতাংশ। সরকার তার স্বাস্থ্যনীতি সরকার লক্ষ্যমাত্রা যা নির্ধারণ করেছিল তা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। এই বরাদ্দের মাত্র ১১ শতাংশ রোগ প্রতিরোধে ব্যয় হয়। স্বাস্থ্যবিমার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের করের টাকার একটা বড় অংশ কর্পোরেট স্বাস্থ্য পরিষেবার হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুনাফার গ্যারান্টি দিচ্ছে সরকার। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ কমছে। আলমা আটার ঘোষণা রূপায়িত করার জন্য যে পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল আমরা তার বিপরীতে হাঁটছি। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা খাতে ২০২৩-২৪ -এ ৭২০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল যার ৭৫ শতাংশ অর্থ প্রদান করা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে। অথচ এই অর্থ সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যয় হলে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল অনেকটাই ফেরানো যেত।
পরিসংখ্যান বলছে, পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের ৬২.৫ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার, মহিলাদের রক্তাল্পতার হার ৫৭ শতাংশ। স্বাস্থ্যের জন্য মাথাপিছ যে খরচ হয় তার ৪৭.০৭ শতাংশ মানুষকে পকেট থেকেই দিতে হয়। আমাদের দেশের ৬ - ৭ কোটি মানুষ কিছু না কিছু মানসিক রোগে আক্রান্ত। ৫৫% মানসিক রোগে আক্রান্ত মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার অন্যতম কারণ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মোট অর্থের মাত্র ১ শতাংশ ব্যয় হয় মানসিক রোগের জন্য।
তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্যের অধিকার বেঁচে থাকার অধিকারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে, কিন্তু আলাদাভাবে স্বাস্থ্যের অধিকার কিন্তু এখনও আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং স্বাস্থ্যের অধিকারটিকে সংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে সমস্ত রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিটি মানুষকে দিতে হবে বিনা খরচে। সরকার দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য বীমাগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ করতে হবে। সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার।
চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর যথাযথ উন্নতি করতে হবে। আরও নতুন সরকারি হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। তা করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারকে জিডিপি’র ৩.৫% স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলিকেও তাদের রাজ্য জিডিপি’র ৫% খরচ করতে হবে স্বাস্থ্যের জন্য। আর এই সরকারি খরচের ৪০% প্রাইমারি কেয়ার বা রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য খরচ করতে হবে। না হলে প্রত্যেক মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে না। পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দ্রুত নিয়োগ না করতে পারলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বড় ঘাটতি থেকে যাবে।
সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে ওষুধের দাম কমানো সরকারের কাজ। কিন্তু ওষুধের ক্ষেত্রে জিএসটি ধার্য অত্যন্ত অমানবিক। অতএব জিএসটি শূন্য শতাংশ করা দরকার। অর্থাৎ জিএসটি তুলে দিলে উপকৃত হবেন গরিব মানুষ। একইসঙ্গে সরকারি ওষুধ এবং টিকা প্রস্তুতকারক কারখানাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে তা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে। এছাড়া সমাজের বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ, এলজিবিটিকিউআইএ প্লাস থেকে আদিবাসী প্রন্তিক মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে।
গত ১৯৭৮ সালের ঘোষণা করা হয়েছিল যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য অর্জন করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো প্রাথমিক বা রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। সরকার আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের জন্য কম খরচ করে। স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গিয়ে মানুষকে নিজস্ব খরচ করতে হয়। ভারতবর্ষে এর পরিমাণ ৫৪.৭৮%। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় এটা বেশ বেশি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এর নীতি এজন্যে দায়ী। ওষুধ কেনা, ডায়গনস্টিক পরীক্ষা, এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের সামগ্রিক চিকিৎসার জন্য ব্যয় অত্যধিক হয়ে পড়ছে। কারণ ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেশিরভাগটাই প্রাইভেট সেক্টর দ্বারা পরিচালিত। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান ভারত এবং স্বাস্থ্য সাথী আউটডোর / বহির্বিভাগ চিকিৎসা কভার করে না। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ইত্যাদির মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘায়িত আউটডোর চিকিৎসা এই দুটি বীমার আওতায় পড়ে না। ফলে চিকিৎখাতে মানুষের আর্থিক চাপ বাড়ছে।
এই স্বাস্থ্য বিমাগুলোর জন্য সরকার যা খরচ করে তা আসে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ করদাতাদের টাকা থেকে। এই সরকারি খরচের একটা বড় অংশ যায় বেসরকারি বা প্রাইভেট হাসপাতালকে টাকা দেওয়ার জন্য। ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি রিপোর্ট ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী আয়ুষ্মান ভারত বিমা প্রকল্পের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা খরচ করেছে, তার ৬৬% গেছে প্রাইভেট বা বেসরকারি হাসপাতাল বা সেক্টরের কাছে। এই অর্থ অবশ্যই সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা যেত। আসলে সরকার মানুষের টাকা বেসরকারি বা প্রাইভেট, করপোরেট হাসপাতাল বা সংস্থাকে পাইয়ে দেয়। অথচ সরকারি আদেশনামা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে সব চিকিৎসা একেবারে বিনামূল্যে হওয়ার কথা।
পানীয় জল, খাবার ও পুষ্টি, বসবাসের বাড়ি ও স্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, টিকা ইত্যাদি হলো গুরুত্বপূর্ণ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য। আমাদের দেশে এই বিষয়গুলোকে অবহেলা করা হয়। সাধারণ মানুষ এবং গোটা সমাজের লাভ বেশি রোগ প্রতিরোধ করতে পারলে। পুষ্টিযুক্ত খাবার, পরিষ্কার পানীয় জল, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এগুলো ভালো স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। এগুলো পেতে গেলে কাজের সুযোগ এবং রোজগারের সুযোগ মানুষের থাকতে হবে। এখানেও দায়িত্ব রয়েছে সরকারের এবং সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন হচ্ছে না। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২৩ –এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১২৫ টা দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থান ১১১। অর্থাৎ আমাদের দেশের বহু মানুষ যতটা দরকার ততটা খাবার খেতে পায় না। এই মানুষগুলির স্বাভাবিকভাবেই নানান রকম রোগ বেশি করে হবে। অক্সফাম বলছে, বিলিয়নেয়ার- এর সংখ্যা আমাদের দেশে ২০২০ সালে ছিল ১০২। আর ২০২২ সালে সেটা বেড়ে হলো ১৬৬। যদি এই বিলিয়নেয়ারদের সম্পত্তির ওপর এককালীন ২% ওয়েলথ ট্যাক্স নেওয়া হতো তাহলে আমাদের দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের আগামী ৩ বছরের জন্য খাবারের সংস্থান করা যেত। কিন্তু আমার দেশের সরকার এই ধরনের কোনও কাজ করেনি।
এর ওপর এখন কোনও একটা ওষুধ কোম্পানি যদি নতুন ওষুধ আবিষ্কার করে পেটেন্ট নিয়ে নেয় তাহলে ২০ বছর সেই ওষুধ শুধুমাত্র সেই একটি কোম্পানি বানাতে পারবে এবং বিক্রি করতে পারবে। স্বাভাবিকভাবেই সে তার ইচ্ছামতো খুব বেশি দাম রাখতে পারবে এবং বেশি লাভ করতে পারবে। এটা খুব পরিষ্কার যে সরকারের নীতিগুলো এমন করে করা রয়েছে যে তাতে ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধের দাম বাড়িয়ে আরও বেশি বেশি লাভ করতে পারে।
জানা গেছে ৩৭টি ওষুধ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার বেশি দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। তাদের বেশ কিছু ওষুধের গুণমান বজায় ছিল না, ফলে সেসব চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে অর্থের বিনিময়ে। ওদিকে ওষুধের দামও তারা বাড়িয়ে দেয় ওই বিপুল পরিমাণ খরচ উসুল করতে। সরকার বা কর্পোরেট ওষুধ সংস্থা-কেউই কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা ভাবলো না। এছাড়াও তথ্য বলছে, ১৯৭৯ সাল, তারপর ১৯৮৭ সাল এবং তারপর ১৯৯৫ সাল- ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারগুলিকে ধীরে কার্যকারিতা কমানো হয়েছে যাতে ওষুধ সংস্থাগুলির পক্ষে ওষুধের দাম বাড়ানো সহজ হয়। এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে সাধারণ গরিব মানুষের ওপরে।
Post Editorial
হারিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ

×
![]()

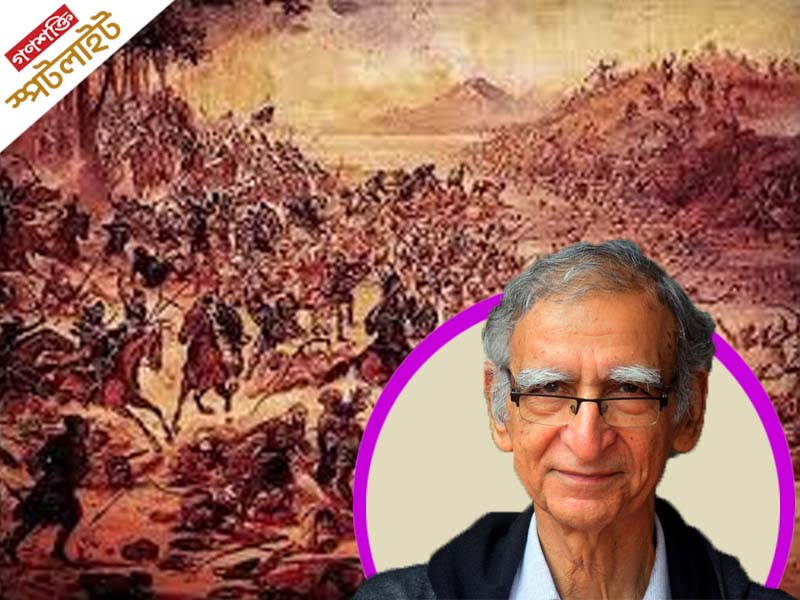





Comments :0