বাসব বসাক
ব্রাজিলের উত্তরাংশে আমাজন ও টোকান্টিক নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত আমাজন অববাহিকার প্রবেশদ্বার হিসাবে চিহ্নিত ঐতিহাসিক বেলেম শহরে চলতি সপ্তাহের শুরুতে, গত ১০ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ত্রিংশতিতম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, যার পোশাকি নাম কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ-৩০; সংক্ষেপে COP-30। এহেন সম্মেলনের অব্যবহিত আগে গত অক্টোবরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধীয় কাঠামোনির্মাণ কনভেনশনের(UNFCCC) পক্ষ থেকে তিনটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। সেই রিপোর্ট ত্রয়ীতেই স্পষ্ট দশ বছর আগের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি মোতাবেক চলতি শতাব্দীর শেষে শিল্পায়ন পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখা এখন কার্যত অসম্ভব। এটা ঠিকই যে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বেশ কিছু দেশকে তাদের জাতীয় স্তরে স্বনির্ধারিত পদক্ষেপ গ্রহণের জায়গায় ইদানীং সেই সব দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ভিত্তিক জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। এটাও ঠিক যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচির একটি হিসাব অনুযায়ী প্যারিস চুক্তির পর গত দশ বছরে কার্বন উদ্গীরণ অতি সামান্য হলেও কমেছে এবং এইভাবে চললে আগামী ২০৩৫-এর মধ্যে তা ১০ শতাংশ কমার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে, বলাই বাহুল্য এই হ্রাস প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। প্যারিস চুক্তি অন্তত কিছুটা হলেও কার্যকর করতে হলে এখন যা প্রয়োজন তা হল জলবায়ু সহনশীল অভিযোজনের পরিকল্পনা। এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রায় হয় নি বললেই চলে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক সাইমন স্টিয়েল জাতীয় স্তরে জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, ‘ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে আছে, দিশা নির্ধারিত হয়ে আছে, এখন আমাদের যা ভীষণরকম প্রয়োজন তা হলো এই কাজে গতি আনা। যে কারণে এবারের সম্মেলনের সভাপতি আঁন্দ্রে আরানহা কোরিয়া ডো লাগো অংশগ্রহণকারী দেশগুলির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন ৩০ তম জলবায়ু সম্মেলন ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে থাকুক জলবায়ু অভিযোজনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দিশারি হিসাবে।
চাই জলবায়ু অভিযোজন
জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ঙ্কর অভিঘাতে বিধ্বংসী ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, অসহনীয় তাপপ্রবাহ, সমুদ্রপৃষ্ঠের জলতলের বেলাগাম বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের জনগণকে রক্ষা করার প্রশ্নে সঙ্কটজনকভাবেই প্রস্তুতিহীন। এশিয়ান ফার্মার্স অ্যা সোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এস্থার পেনুনিয়া একটি সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল উদ্ধৃত ক’রে দেখিয়েছেন একজন পারিবারিক ক্ষুদ্র কৃষকের বর্তমান সময়ে জলবায়ু অভিঘাত থেকে কৃষিকে বাঁচাতে তার বছরে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ন্যূনতম ৯৫২ ডলার প্রয়োজন। অর্থাৎ কিনা প্রতিদিন দরকার ২.১৯ ডলার (মানে দৈনিক ১৯৫ টাকা)। এশিয়ার একজন ক্ষুদ্র কৃষক কোথা থেকে জোটাবে এই বিপুল অতিরিক্ত খরচ! চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রখ্যাত ল্যানসেট পত্রিকার বার্ষিক কাউন্টডাউন সংখ্যায় ২০১২ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে চরম তাপপ্রবাহের অভিঘাতে মৃত্যু ঘটেছে ৫৪৬০০০ জন মানুষের যেখানে দাবানল জনিত অগ্ন্যুৎপাত উদ্ভূত বিষাক্ত ধোঁয়া কেবল ২০২৪তেই কেড়ে নিয়েছে ১৫৪০০০ প্রাণ। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক হর্ষল সালভে জানাচ্ছেন ভারতে ক্রমশ তাপপ্রবাহ, জল সঙ্কট অথবা বায়ুদূষণের ফলে স্বাস্থ্য সঙ্কট দুর্বার গতিতে বাড়ছে। এ দেশে শুধু বায়ুদূষণের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় জলবায়ু অভিযোজনের জন্য স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ না বাড়লে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হতে বাধ্য। ফলে বিশ্বজুড়েই জলবায়ু অভিযোজনে উন্নত দেশগুলির বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি উঠেছে। কেননা উন্নত দেশগুলির যথেচ্ছাচারেরই আজ মাশুল গুনতে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। তাই বিশেষ ক’রে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বায়ুশক্তি বা মাইক্রোসোলার প্রকল্পের মতো পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি উৎপাদনে গুরুত্ব আরোপ, সমুদ্রবাঁধ নির্মাণ, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ, সমুদ্রোপকূলে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ রোপণ, লবণ সহনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার নির্ভরতা কমিয়ে জৈব কৃষিতে গুরুত্ব আরোপ, হত দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য তাপবিমা লাগু করা, অরণ্যভূমি রক্ষা ও অরণ্যচারী মানুষের কর্মসংস্থান ইত্যাদি নানা ধরনের প্রয়োজনীয় জলবায়ু সহনশীল অভিযোজনমূলক প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য যে বিপুল অর্থ ভাণ্ডার প্রয়োজন তার সংস্থান করতে হবে উন্নত বিশ্বকেই। রাষ্ট্রপতি লুলা দ্য সিলভার নেতৃত্বে সম্প্রতি বর্ষাবন সুরক্ষায় ১২৫ বিলিয়ন ডলারের একটি জলবায়ু অভিযোজন ভাণ্ডার নির্মাণের দাবি জানিয়েছে ব্রাজিল যে অর্থ ৭০ টি দেশে বিস্তৃত ১ বিলিয়ন হেক্টর অরণ্য ভূমির সুরক্ষার পুরস্কার হিসাবে ব্যয় হবে এবং যার অন্তত ২০ শতাংশ অর্থ যাবে অরণ্যবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের হাতে। গত মাসে রাষ্ট্রপতি লুলা ব্রাজিলের পক্ষ থেকে ওই ভাণ্ডারে ১ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেছেন।
লাও তো বটে কিন্তু আনে কে
রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচির সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের এহেন বিপুল অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলির আগামী ১০ বছরের মধ্যে প্রয়োজন বছরে অন্তত ৩১০ থেকে ৩৬৫ বিলিয়ন ডলার (মুদ্রাস্ফীতিকে হিসাবের মধ্যে ধরলে এই অঙ্ক বেড়ে ৪৪০ থেকে ৫২০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলেই আশঙ্কা ইউএনইপি-র); আর বর্তমানে গ্লাসগো সম্মেলনে বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষিত আন্তর্জাতিক জলবায়ু অভিযোজন পুঁজির বরাদ্দের পরিমাণ বছরে মাত্র ২৬ বিলিয়ন ডলার। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচি গত ২৯ অক্টোবর প্রকাশিত ‘দ্য অ্যা ডাপটেশন গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৫’এ তাদের হতাশা গোপন না ক’রে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে বাঁচতে ‘পু্ঁজির আকালে’র (‘Running on empty’)উল্লেখ ক’রে জানিয়েছে এই মুহূর্তে জলবায়ু অভিযোজনে যে অর্থ উন্নত দেশগুলি বরাদ্দ করেছে আদতে তা প্রয়োজনের তুলনায় ১২ থেকে ১৪ গুণ কম এবং যা কিনা গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তি নির্ধারিত লক্ষমাত্রার ধারে কাছেও নেই। অথচ গত বছর বাকুতে অনুষ্ঠিত ২৯তম জলবায়ু সম্মেলনে জলবায়ু অভিযোজন বাবদ ভুক্তভুগী উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্যের জন্য ২০৩৫-এর মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি অর্থ ভাণ্ডার গঠনের কথা রীতিমতো ঘটা ক’রে জানানো হয়েছিল। এমনকি ২০৩৫-এর মধ্যে বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলার এই খাতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য বরাদ্দ করা হবে এমন কথাও জানানো হয়েছিল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক আন্তোনিও গুত্তারেস ৩০ তম জলবায়ু সম্মেলনের প্রাক মুহূর্তে তাই বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত দ্রুত ক্রমবর্ধমান। অথচ অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি বরাদ্দের হার একেবারেই গতি পাচ্ছে না। যার অর্থ বিশ্বের সব থেকে দুর্বল অংশের মানুষ আরও বেশি বেশি ক’রে বাড়তে থাকা সমুদ্র জলতল, ভয়াবহ সাইক্লোন অথবা প্রাণশক্তি নিঙড়ে নেওয়া তাপপ্রবাহের বলি হতেই থাকবে। তাই জলবায়ু অভিযোজন আদতে খরচ নয়, এ আমাদের জীবনরেখা। জলবায়ু অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং বরাদ্দকৃত পুঁজির মধ্যে যে বিপুল ফরাক থেকে যাচ্ছে তা কমিয়ে আনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবন বাঁচানোর শর্ত। ও পথই জলবায়ু ন্যায়ের পথ। একমাত্র জলবায়ু অভিযোজন খাতে উন্নত দেশগুলি বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেই মিলতে পারে তুলনামূলক নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ পৃথিবী নির্মাণের দিশা। আমরা যেন আর একটি মুহূর্তও নষ্ট না করি”। কিন্তু কে শোনে কার কথা!
‘উন্মাদের পাঠক্রম’
আমরা জানি আজকের জলবায়ু সঙ্কটের সিংহভাগ দায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ শিল্পোন্নত দেশগুলিরই। অথচ বারবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা ছুতো নাতায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধী যে কোনও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে ব্যাগড়া দিয়ে এসেছে। মূলত আমেরিকার কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে ১৯৯৭ সালে গৃহীত কিয়োটো প্রোটোকল কার্যত ভেস্তে গেছে। ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নতুন ক’রে বিশ্বের সামনে যে আশার আলোটুকু জ্বেলেছিল গত অক্টোবরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন আসলে পৃথিবীর সব থেকে প্রতারণামূলক একটি বিষয় (‘greatest con job’) যা দেশগুলিকে তাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যকে বন্ধক রেখে জলবায়ু নীতি প্রণয়নে কার্যত বাধ্য করে। ট্রাম্প চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে ২০২৬-এর জানুয়ারি মাস থেকেই আমেরিকা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে আসবে। তার সদর্প ঘোষণা কার্বন উদ্গীরণ কমানোর থেকেও আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেই তিনি ঢের বেশি আগ্রহী। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর দেশে ‘জাতীয় শক্তি উৎপাদনের আপৎকাল’ (‘National Energy Emergency) ঘোষণা ক’রে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন আরও বাড়াতে বিশেষ নির্দেশিকায় সাক্ষর করেছেন। তৈল উৎপাদন ক্ষেত্রে মিথেন নির্গমনের নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার মতো জো বাইডেনের সময়কালে যে সামান্য কয়েকটি পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ ছিল সে সবও ইতিমধ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পের মতে এসবই নাকি জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের ‘অনৈতিক বোঝা’ (‘undue burden’)। শুধু তাই নয়; এ বছরের গোড়ায় প্লাস্টিক দূষণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্লাস্টিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে যেন কোনোরকমের সর্বসম্মত চুক্তিতে দেশগুলি স্বাক্ষর না করে সে জন্য আমেরিকা অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে ভয়ঙ্কর চাপে রেখেছিল। স্বভাবতই চুক্তিটি শেষপর্যন্ত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখিয়ে কার্যত ঠান্ডা ঘরে ঢুকে গেছে। ট্রাম্পের পছন্দের শিল্পপতিরাও এখন আর রাখঢাক না ক’রে একই সুরে গান ধরেছেন। সম্প্রতি বিল গেটস জানিয়েছেন, ‘বিশ্বের গড় তাপমান বাড়তে না দেওয়ার লক্ষ্য থেকে নজর সরিয়ে আনার এটাই সময়। এমন নয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হতে চলেছে’। ট্রাম্প সরকারের পক্ষে তাই দিন কয়েক আগে হোয়াইট হাউস থেকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ট্রাম্প তো নয়ই, এমনকি বেলেমে এ বছর আমেরিকা খুব উচ্চ পর্যায়ের কোনও প্রতিনিধিকেই পাঠাচ্ছে না। আমাদের দেশেও মোদীজি যতই মুখে পরিবেশ রক্ষায় পঞ্চশীল নীতির কথা শোনান, আসলে তাঁর কাছেও খুব গুরুত্ব যে আর নেই এই সম্মেলনের তা স্পষ্ট হয় যখন তিনি এবার আর নিজে বেলেম না গিয়ে তাঁর পরিবেশ ও বন মন্ত্রীকে পাঠাচ্ছেন সেখানে।
‘আশা শুধু মিছে ছলনা’
১৯৭৫ সালে প্যারিস শহরে প্রতিষ্ঠিত বহুজাতিক বাজার গবেষণা সংস্থা ইপসোস গত ২০ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার মোট ৩০ টি দেশের ১৮ থেকে ৭৪ বছর বয়স পর্যন্ত ২৩৭০০ জনের ওপর আসন্ন তিরিশতম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনকে সামনে রেখে একটি নিবিড় সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য যে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণে আন্তর্জাতিক মতৈক্য খোঁজা সে সম্পর্কে যেমন অবহিত আছেন ৪৪ শতাংশ মানুষ; তেমনি আবার ২৯ টা সম্মেলন হয়ে যাওয়ার পরেও ৪৪ শতাংশ মানুষ এমন কোনও জলবায়ু সম্মেলনের কথা জানেনই না। ৫ শতাংশ আবার জানিয়েছেন এ নাকি খেলাধুলো সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের মঞ্চ। যারা জানেন তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মানুষই (৪৯%) মনে করেন এই সম্মেলন আদতে প্রতীকী ব্যাপার, কাজের কাজ কিছুই এতে হবে না। তবে এই সমীক্ষার সব থেকে চিন্তার দিক যেটা তা হলো বিশ্বের ৬৯ শতাংশ মানুষ মনে করছেন বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সব সময়েই পরিবেশের থেকে অনেক বেশি অগ্রাধিকার দেয় তাদের মুনাফায়; ২৪ শতাংশ মনে করেন জীবাশ্ব জ্বালানি শিল্পের প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে সব দেশকে, ১৭ শতাংশ মনে করেন কর্পোরেট কৃষিই জলবায়ু অভিযোজন উদ্যোগের পথে সব থেকে বড় অন্তরায়, আর ৪২ শতাংশ মানুষের বিচারে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পথে সব থেকে বড় বাধা হলো বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রধানদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ভয়ঙ্কর অভাব। সোজা কথাটা হলো বিশ্ববাসীর সামনে ফি বছর জলবায়ু সম্মেলনের নামে অলীক কুনাট্য রঙ্গের ফক্কিকাড়ি ধরা পড়ে গেছে। বলাই বাহুল্য ত্রিশতম জলবায়ু সম্মেলনও শেষ পর্যন্ত আরও একটি মৃত শিশু প্রসব করতে চলেছে।
মনে রাখতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনের অসহনীয় অভিঘাতে বিপন্ন মূলত তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিই। আবার সেই সব দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রান্তিক গরিব মানুষ। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের তেমন কোনও ভূমিকা কস্মিনকালেও ছিল না। তাই সময় এসেছে জলবায়ু ন্যায়ের দাবিতে পথে নামার। বিশ্বজুড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত জর্জর সেই সব দেশের মানুষগুলোর জোট গড়ে তোলাই আজ সময়ের দাবি। বিশ্বজুড়ে আওয়াজ উঠুক জলবায়ু অভিযোজন কেবল কথার কথা হয়ে থাকলে চলবে না। তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে উন্নত দেশগুলিকেই।



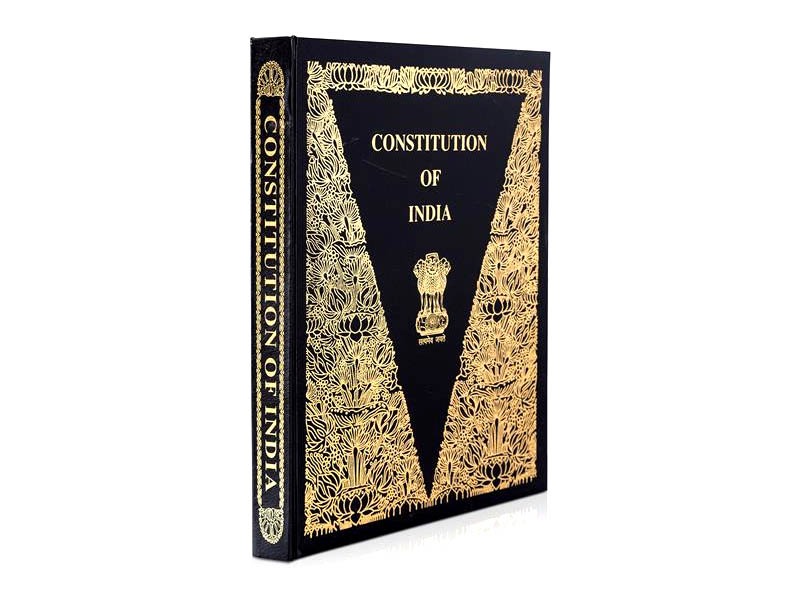




Comments :0