জয়রাজ
নীরজ ঘেওয়ান পরিচালিত হোমবাউন্ড সিনেমাটা, মিথ্যে, সুখী ভারতের তলায় চাপাপড়া, ধুঁকতে থাকা, মুমূর্ষু ভারতকে দেখিয়ে দেয়। দক্ষিণপন্থীদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ মানুষের সমর্থন আদায় করে নেয়, কখনো জোর খাটিয়ে, কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে। জোর খাটানোটাকে যতো সহজে দেখা যায়, যতো সহজে বোঝা যায় যে- ওটা ফ্যাসিবাদই, আদর করে মাথায় হাত বুলোনোকে ফ্যাসিবাদ বলে চিনতে পারা ততো সহজ নয়। ‘রেঁধে বেড়ে পিঁড়ে পেতে তোমায় খাওয়াবো/ নরম বিছানাতে ঘুম পাড়াবো/ আমার কাছে থাক না হয়, ভাঁড়ারেরই চাবি/ তোর কি ব্যাটা হেসে খেলে দিন তো কাটাবি’ - অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মারীচ সংবাদ' নাটকের মেরি বাবার গান।
এই যে মাথায় হাত বুলিয়ে পাবলিককে টুপি পরানো, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে বুঝতে না দেওয়া, এটাকেই কালচারাল হেজেমনি বলে। কালচারাল হেজেমনির বাংলা করলে মোটামুটি দাঁড়ায়- সাংস্কৃতিক আধিপত্য। এই প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক আধিপত্য, যা দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গণসমর্থন আদায় করে নেয়, তাকে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আধিপত্য দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে। ‘মিথ্যা’, এখন যার নতুন নাম হয়েছে 'উত্তরসত্য বা পোস্ট ট্রুথ' তাকে মোকাবিলা করতে হয় দ্বিধাহীন সত্য দিয়ে, আর তা করতে পারে নিজের বর্গ থেকে উঠে আসা অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল।
নিজের দলিত আত্মপরিচিতি নিয়ে সিনেমার কারিগর হয়ে ওঠা চুয়াল্লিশ বছর বয়সের নীরজ ঘেওয়ান, তাঁর প্রথম ছবি মাসান-এর মতো দ্বিতীয় ছবি হোমবাউন্ড-এও নিজের বর্গের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি স্থিত থাকেন।
আরো সদর্থক, নীরজ এটা করেন মেনস্ট্রিম ছবির শর্তকে মান্যতা দিয়েই। ছবিটার প্রিমিয়ার হয়েছে কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। সেখানে ছবি প্রদর্শনের পর ১০ মিনিট স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছেন নীরজ। হোম বাউন্ডই এই বছরের অ্যাকাডেমি আওয়ার্ড’এর জন্য ভারত থেকে অফিসিয়ালি নির্বাচিত হয়েছে।
ভারতীয় মেনস্ট্রিম ছবির ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি শোলের মতো, হোমবাউন্ডেও আমরা দেখি দুই বন্ধুর গল্প। এখানেও অন্তিমে এক বন্ধু মারা যায়। কিন্তু শোলের দুই বন্ধু জেল ফেরত আসামি হলেও, আমাদের চোখে তারা ততটা আসামি নয়, যতটা হোমবাউন্ড সিনেমার দুই মুখ্য চরিত্র- মহম্মদ শোয়েব আর চন্দন কুমার, তাঁদের আত্মপরিচয়ের কারণে। একজন মুসলমান আর অন্যজন দলিত, এই পরিচয়টুকুই আজকের হ্যাপেনিং ভারতবর্ষে যথেষ্ট কারণ, কাউকে ‘ক্রিমিনাল’ অভিধায় দাগিয়ে দেওয়ার জন্য।
প্রান্তিক গ্রাম ভারতের দুই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ বন্ধু, দু’জনেই পুলিশের চাকরি করতে চায়, বাড়ির হাল একটু ফেরাতে চেয়ে। একজন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, অন্যজন পারে না। এর ফলে তাদের বন্ধুত্বেও আসে সাময়িক বিচ্ছেদ। কিন্তু যে উত্তীর্ণ হয় পরীক্ষায়, তার চাকরিতে যোগ দেওয়ার খবর এসে আর পৌঁছায় না। অপেক্ষা করতে করতে, করতে করতে, চন্দন কুমার ঠিক করে আরও কিছুদূর পড়াশোনা করা যেতে পারে, কিন্তু অভাবের সংসারে সেটাও সম্ভব হয় না। যোগ দিতে হয়, বাড়ির থেকে বহুদূরে সুরাটে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাপড়ের কলে মজদুরি করতে। অন্য বন্ধু মহম্মদ শোয়েব, যোগ দেয় একটা অফিসে চাপরাশির কাজে। নিজের সেলসের কাজে দক্ষতা প্রমাণ করে কিছুটা উন্নতিও করে। একদিন সেই অফিসের পার্টিতে অন্যদের সাথে ডাক পায় শোয়েবও, পার্টির প্রধান উপলক্ষ-ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ। বিগস্ক্রিনে ভারত পাকিস্তানের খেলা চলছে, আর বারবার মহম্মদ শোয়েব আলির ভারতীয়ত্ব যথেষ্ট খাঁটি কিনা, এই মর্মে নেহাতই মামুলি মশকরা করা হতে থাকে। যেমন মশকরা আজকের ভারতে আমরা, হিন্দু পরিচয়ের নিরাপত্তা বলয়ে থাকা মানুষেরা, স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। যেমন মশকরায় পাশের মুসলমান মানুষটি রিঅ্যা ক্ট করলেই বরং, আমাদের গুড হিউমার আর উইটের ভাবাবেগ আহত হয়। কিন্তু মহম্মদ শোয়েব আলি সেদিন আর পারে না মেনে নিতে। চাকরি ছেড়ে দেয়। বাবার হাঁটুর রিপ্লেসমেন্ট, পরিবারের অপরিসীম দারিদ্র কিছুই তার চাকরি ছাড়ার মতো ইমম্যাচিওর সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করতে পারে না।
অতঃপর সেও পৌঁছায় সুরাট। বন্ধুর কাছে। বন্ধু নিয়ে যায় মিলে। মিলে, মিলে যায় আরও বন্ধু। ভাগাভাগি করে থাকা, ভাগাভাগি করে খাওয়া, সহনীয় লাগে। তারপর করোনা। তারপর লকডাউন। তারপর মিল বন্ধ। তারপর রসদ ফুরিয়ে যাওয়া। তারপর একটু খাবারের জন্য অপমানিত হওয়া। তারপর পুলিশের লাঠি। তারপর লাখ লাখ পরিযায়ী মজুরের হাঁটতে থাকা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এক বন্ধুর মৃত্যু। গল্প এইরকম। এতোটা বাস্তব কী আর ততটা ভালো গল্প হতে পারে? কিন্তু এই সিনেমা এরকমই। নীরজের অন্য কাজে আমরা দেখেছি, বাস্তবের পাশাপাশি, সে একটা সিনেমাটিক বাস্তবতা তৈরি করতে দক্ষ। অনেকে সেই সিনেমাটিক উপস্থাপনাকে পোয়েটিক বলেও চিনতে চান। কিন্তু এই সিনেমায় নীরজ এই কাব্যিক ব্যাপার স্যাপার উইথড্র করেছেন। যেমন জীবন থেকে সমস্ত আলগোছে ছুঁয়ে যাওয়া ফুলের স্পর্শ উইথড্র হয়ে গেছে। যেমন মৃত্যুর পরে শববহনের কালে, ভাসিলের গালে চুম্বন করে যায় গাছ থেকে নুইয়ে পড়া আপেল, আর জানলায় আছাড়িপাছাড়ি ক্রন্দনরত প্রেমিকার নগ্ন নিতম্বে সাপের মতো দুলতে থাকে বেণি, দেভজেঙ্কোর আর্থ ছবিতে। তেমন এক্সেস আর তেমন কবিতার নির্মাণ এই ছবিতে হয় না, কারণ মৃত্যুরও এখানে ডিগনিটি নেই। এক্সেস আর এসেনশিয়ালের দ্বন্দ্বে সিনেমা পরিচালকেরা কিছু এক্সেস রাখেন, সেই এক্সেসই হয়ে ওঠে অমোঘ। যেমন সোনার কেল্লা সিনেমায় লালমোহন গাঙ্গুলির ইন্ট্রোডাকটরি সিকোয়েন্সে, এক মাড়োয়ারি মানুষ ট্রেনের বাঙ্কে বসে টিফিন বাক্স থেকে খাবার খেতে থাকেন। এসেনশিয়াল নয়, এক্সেস, কিন্তু মনে থেকে যায় আমাদের। সেরকম এই সিনেমায় ঘটে না, কারণ ছবিটাই এক্সেসদের নিয়ে, যাদেরকে বাতিল করতে পারলেই নাকি ভারতের উন্নয়ন মনে করে উন্নতিকামী ভারত। এখানে তাই বেশিরভাগ শট কম্পোজিট শট। প্রেফারেন্স শট কম, প্রায় নেই। ক্যামেরা একটা প্যারালাল এঙ্গেলে থাকে। দু’- একটা চুড়ান্ত শটে পার্পেণ্ডিকুলার অবস্থান নেয়। ছবির সত্তর ভাগ শট হ্যান্ড হেল্ড, অর্থাৎ ক্যামেরা থাকে সিনেম্যাটোগ্রাফারের হাতে। এই ছবির কালার গ্রেডিংও রঙের বাহুল্য ও বৈভবকে পরিহার করেছে।
চন্দন কুমারের মা, যিনি ইস্কুলে মিড ডে মিলের রান্না করলে, উঁচু জাতের অভিভাবকরা হুমকি দেন বাচ্চাদের ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, কারণ দলিতের হাতের রান্না খেলে তাদের জাত যাবে। ফুটিফাটা মাটিতে তারচেয়েও ফাটা গোড়ালি নিয়ে যখন চন্দনের মা, যাঁর নাম ফুল, হাঁটেন তখনও ক্যামেরা একেবারে মাটিতে নেমে এসে থাকে প্যারালাল এঙ্গেলে। দেখতে পাই আমরা শাশ্বত গ্রামীণ ভারতে ফুলের পদচারণা। চন্দন কুমার মারা যায়। একটা চটি সে মায়ের জন্য কিনেছিল। ফুলের পা নয়, হাতে সেই চটি তুলে দেয় চন্দনের বন্ধু শোয়েব। ক্যামেরা তখনও প্যারালাল এঙ্গেলে। ফুল কাঁদছে, আমাদের মনে পড়ে সর্বজয়ার কান্না। ক্যামেরা প্যারালাল এঙ্গেলে। আমরা অপেক্ষা করি ফুলের হাতে ধরে থাকা চটি আরও ওপরে উঠে আছড়ে পড়বে একদিন তথাকথিত শুদ্ধ ভারতের গালে। আর সেদিন নীরজের ক্যামেরা থাকবে প্যারালাল এঙ্গেলে।
ছবিতে প্রণয় এসেছে এবং পরিণতি পায়নি। চন্দনের প্রেমিকা পড়তে চেয়েছিল, পিএইচডি করতে চেয়েছিল, আম্বেদকর তাকে নিয়ত অনুপ্রেরণা দেয় দেওয়ালের ফোটোগ্রাফ থেকে। সে এই লড়াই চালিয়ে যাবে আমরা বুঝতে পারি। চন্দনের দিদি পড়ার সুযোগ পায়নি, একজনই পড়তে পারতো অভাবের সংসারে, বেছে নেওয়া হয় ছেলেকে। নীরজ প্রান্তিকের মধ্যে প্রান্তিকতমকে বুঝতে চেয়েছেন সহমর্মিতায়। শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি মৃত চন্দন কুমারের নামে চাকরি পাওয়ার চিঠিটা আসে। শোয়েব রিসিভ করে চিঠি। শোয়েবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বন্ধুর সাফল্যে। একদিন বন্ধুর সাফল্যে সে যন্ত্রণা পেয়েছিল। আজ বন্ধুর সেই একই সাফল্যে সে খুশিতে হেসে ওঠে। বন্ধুকে সে পিঠে করে মাইলের পর মাইল বয়ে এনেও বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু বন্ধুত্ব বেঁচেছে। শোয়েব ঠিক করে পড়াশোনা করবে, বন্ধু পড়াশোনা করতে চেয়েছিল।
হোমবাউন্ড একটা উত্তরণের ছবি। শোয়েব হাতে বই তুলে নেয়। শুধু আম্বেদকর না, ব্রেখট বলেছেন ‘ভুখা মানুষ হাতে বই তোলো, ওটা হাতিয়ার।’
দক্ষিণপন্থীদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি ফ্যাসিবাদ। তার বিরুদ্ধে যা কিছু প্রতিরোধ সবকিছু স্বাভাবিক ভাবেই বামপন্থীদের পক্ষে, এমনকি তা যদি বামপন্থী নির্মাতা না বানায়, তাহলেও। হোমবাউন্ড এই মূহূর্তে বামপন্থীদের একটা হাতিয়ার। সিনেমার প্রথমেই একটা ডিসক্লেইমার দেওয়া হয়, সরকার বাহাদুরকে আস্বস্ত করতে, যা গোটা ছবিটা দেখার পর মনেই থাকে না। মনে থাকে সরকারের উদাসীনতা, তাচ্ছিল্য, উপহাস, আর অপরাধের খতিয়ান। মেইন স্ট্রিমে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলে দিতে এই কৌশল নিতে হয় যা সর্বোচ্চ সফল হয়েছে। হোমবাউন্ড প্রথম দফায় কলকাতায় চলার পর, হল থেকে সরে গিয়েছিল, কিন্তু দর্শকদের আগ্রহে আবার ফিরে এসেছে। দ্বিতীয় দফায় একটা মাত্র শো দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন হল এবং শোয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। অর্থাৎ দর্শক বাড়ছে। দর্শক ভালো সিনেমার পাশে আছে। সেকুলার সিনেমায় পাশে আছে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে, আক্রান্তের পাশে থাকা সহমর্মি সিনেমার পাশে আছে।
লালসেলাম, জয়ভীম কমরেড নীরজ।
Homebound Movie
প্রান্তিক ভারতের লড়াই দেখিয়েছেন নীরজ

×
![]()


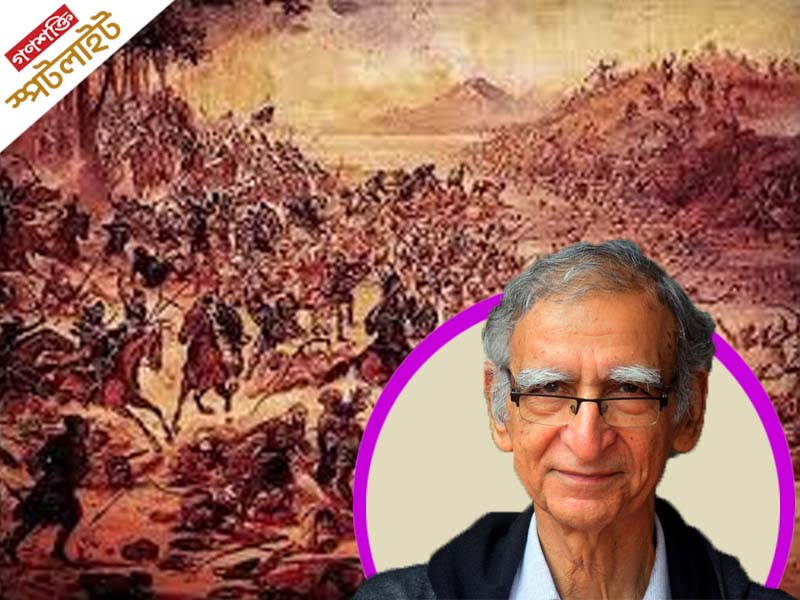



Comments :0